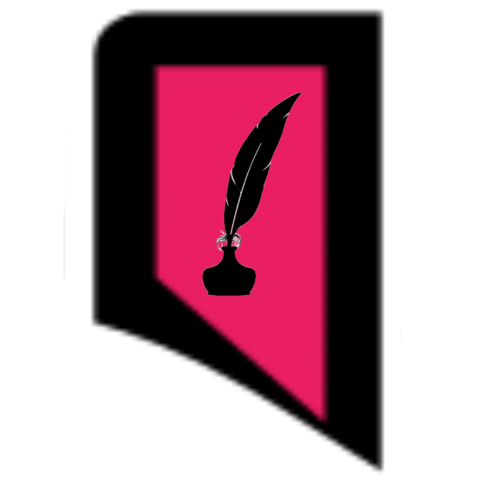বিষাণগড়ের সোনা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭
ভিরিন্ডি থেকে লাইট রেলওয়ের ট্রেন ঠিক দেড়টাতেই ছেড়েছিল। ছোট-মেসোমশাই বলেছিলেন, ওখান থেকে বিষাণগড় খুব দূরে নয়, তবে কিনা লাইট রেলওয়ের ট্রেন তো, ঢিকুস-ঢিকুস করে চলে, পৌঁছতে পৌঁছতে তা প্রায় পাঁচ-ছ ঘণ্টা লেগে যাবে। তা তিনি কিছু বাড়িয়ে বলেননি। এ লাইনের গাড়ি দেখলুম নামেই রেলগাড়ি, আসলে গোরুর গাড়িরও অধম। কোথাও একবার থামে তো নড়তে চায় না, আর যদি-বা নড়ে তো এগোতে চায় না একেবারেই।
দু’দিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। তারই মধ্যে একটু-আধটু ফাঁকা জায়গা কি দু-চারটে কুঁড়েঘর মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে। আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট বাদে বাদে স্টেশনও আসে এক-একটা। দু’চারজন লোক সেখান থেকে ট্রেনে ওঠে, দু’চারজন যাত্রী সেখানে নেমেও যায়।
যাত্রীদের মধ্যে চোদ্দো-আনাই আদিবাসী। অধিকাংশেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারে অনাবৃত, আর নিম্নাঙ্গেও অনেকেরই নিতান্ত একটি লেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। পুরোপ্রস্ত জামা-কাপড় পরা যাত্রীর সংখ্যা নামমাত্র। তাদের মধ্যে মাকড়ি-পরা, কপালে চন্দনের তিলক আঁকা, পাগড়িওয়ালা জনাকয় মানুষও চোখে পড়ল। দেখেই বোঝা যায় যে, এরা কারবারি লোক। সম্ভবত মারোয়াড়ি। টাকা কামাবার ধান্দায় এই জঙ্গলে এসে ব্যাবসা ফেঁদেছে।
ভিরিন্ডি থেকেই এই রকমের একজন মানুষকে আমার সঙ্গী হিসেবে পাই। যে-কামরায় উঠেছিলুম, আমার খানিক আগেই তিনি তার একটা বেঞ্চির একধারে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে নিজের জায়গা ছেড়ে আমার পাশে এসে বসলেন। ভদ্রলোকের নাম সুরজপ্রসাদ আগরওয়াল। বয়েস বছর পঞ্চাশেক বিষাণগড়ের মার্কেট রোডে এঁর গয়নার দোকান আছে। তা ছাড়া কাঠের কারবারেও টাকা লাগিয়েছেন, তার সূত্রে মাঝে-মাঝে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়তে হয়। একা দু’দিক সামলাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে গয়নার দোকানের দায়িত্ব পুরোপুরি ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। নিজে শুধুই কাঠের কারবার দেখেন। শাল-সেগুনের জঙ্গল ইজারা নেন, লোক লাগিয়ে গাছ কাটান, মস্ত-মস্ত গাছের গুঁড়ি ওয়াগন আর ট্রাকে বোঝাই হয়ে হরেক শহরে পৌঁছে যায়। তবে লোকাল ডিমান্ডও কিছু আছে তো, সেটা মেটাবার জন্যে বছর কয়েক হল বিষাণগড়ে একটা স-মিল্ বসিয়েছেন। কিছু গুঁড়ি সেই মিল-এ যায়। রোদ খেয়ে আর জলে ভিজে গাছের কাঁচা গুঁড়ি সেখানে সিজন্ড হয়। তারপরে সেই গুঁড়ি চেরাই করে বসানো হয় তক্তা আর দরজা-জানলার ফ্রেম।
আগরওয়ালজির কাছেই জানা গেল যে, যেমন ফার্নিচার তেমন জানলা-দরজার পাল্লা বানাতে হলেও নাকি শালকাঠে বিশেষ সুবিধে হয় না, তার জন্যে সেগুন চাই।
“শালকাঠ দিয়ে তবে কী হয়?”
“কেন, দরজা-জানলার পাল্লা না হোক, তার ফ্রেম হয়। বড়লোকের পালঙ্ক না হোক, গরিব লোকের তক্তাপোষ হয়। বয়েল-গাড়ির চাকা হয়। শাল কাঠ আরও অনেক কাজে লাগে।”
“যেমন?”
আগরওয়ালজি বুঝে গিয়েছিলেন যে, কাঠের ব্যাপারে আমি বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানি না। তাই কৃপার হাসি হেসে বললেন, “বাবুজি, আপনারা আংরেজি পড়েছেন, দো-চারঠো পাশ ভি করেছেন, কিন্তু কিতাবের বাইরে কুছু আপনারা দেখেননি। বাবুজি, ক’টা লোক আর দালান-কোঠা থাকে? বেশির ভাগ লোকই তো থাকে কাঁচা মাটির বাড়িতে। তো তার জন্যেও খুঁটি চাই। আপনাদের বংগাল-মুল্লুকে তো আমি ছিলুম, তখন সেখানে বাঁশের খুঁটির চল্ দেখেছি। তা এদিকে বাঁশঝাড় কোথায়? ঘরের চালটাকে ধরে রাখবার জন্যে এখানে শালের খুঁটির দরকার হয়। সে-সব অবশ্য ভাল জাতের শাল নয়, ওই যাকে এদিকে শলাই বলে, সেই জিনিস আর কি। সেও শালগাছই, তবে খুব ইনিফিরিয়র কোয়ালিটির।”
নিজের অজ্ঞতাকে খানিকটা অন্তত চাপা দেবার জন্যে বললুম, “এককালে খুব বার্মা-টিকের নাম শুনেছি।”
আগরওয়ালজি এতক্ষণ মৃদু-মৃদু হাসছিলেন, আমার কথা শুনে এ বারে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন, “ভুলে যান, বাবুজি, ভুলে যান। যুদ্ধের আগে বার্মা থেকে ও-জিনিস কুছু-কুছু আসত বটে, কিন্তু আমদানি এখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গেছে। আর বন্ধ না হলেই বা কী হত? ও-জিনিস কিনত কে? বার্মা-টিক হল সেগুনের রাজা, কিন্তু যা দাম, রাজা-উজির ছাড়া ও- কাঠ ছোঁবার মতন পয়সা কারও নেই। তো বাবুজি, ইন্ডিয়া নাকি এবার স্বাধীন হবে?”
বললুম, “মনে তো হয়।”
এ হল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। বাতাসে তখন স্বাধীনতার দু’চার ঝলক অগ্রিম সৌরভ মাঝে-মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীন। তো দেড়-বছর পরের ব্যাপার, ইন্টেরিম ক্যাবিনেটও তখনও পর্যন্ত গড়া হয়নি। আর দেশীয় রাজ্যগুলির মার্জার তো আরও অনেক পরের ঘটনা।
সত্যি বলতে কী, পিছনে তাকিয়ে আজ যখন আমি বিষাণগড়ের কথা ভাবি, তখন এই কারণেই সেখানকার কাঠের কারবারি সুরজপ্রসাদ আগরওয়ালকে এজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মানুষ বলে আমার মনে হয়। দেশ এবারে স্বাধীন হবে, অন্তত তার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, আমার মুখে শুধু এইটুকু শুনেই আগরওয়ালজি সেদিন বলেছিলেন, “তা হলে তো ব বুজি হয়েই গেল, রাজারাও তখন আর বার্মা-টিক ছুঁতে পারবে না। সিপি-টিকও ছুঁতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে।”
শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, “একথা বলছেন কেন? স্বাধীন তো হবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, তাতে নেটিভ স্টেটগুলোর গায়ে তো আঁচড় লাগবার কথা নয়। তা হলে?”
আগরওয়ালজি আবার এক দফা হেসে বললেন, “ছোড়িয়ে, বাবুজি, ছোড়িয়ে। তামাম দেশ আজাদ হয়ে গেল আর এই নেটিভ স্টেটগুলার রাজা অওর নবাবদা তবু সিংহাসনে আরামসে বসিয়ে রইলেন, তাও কি হয় নাকি? না বাবুজি, তা হয় না। আজাদির লড়াই তখন ইখানেও খুব জোর চলবে। কংগ্রেস তো ইখানেও আছে, তারা ছোড়বে না।”
বললুম, “আপনার কথা শুনে আমার রণজিৎ সিংয়ের কথা মনে পড়ছে, অবশ্য উলটো দিক দিয়ে।”
“রণজিৎ সিং কে বাবুজি?”
“জবরদস্ত এক শিখ রাজা। ম্যাপে তো ইংরেজদের দখল-করা জায়গাগুলো লাল-রঙে দাগিয়ে দেখানো হয়। তা ইংরেজরা যখন এ-দেশে তাদের রাজ্যবিস্তার করছিল, তখন ভারতবর্ষের ম্যাপে একদিন লাল-রঙ-করা জায়গাগুলো দেখে তিনি বলেছিলেন, সং লাল হো জায়েগা। আপনি অবশ্য উলটো দিক থেকে একই কথা বলছেন। আপনার কথা হল, ‘সব নাল একইসঙ্গে খতম হো জায়েগা।’ তাই না?
আগরওয়ালজি আবার হাসলেন। বললেন, “ঠিক বাত। বিলকুল ঠিক বাত। এই যে সব রাজা দেখছেন, এরা তো সব কাঠের পুলি। ইংরেজ যদি চলে যয় তো পুলিগুলানকে কে বাঁচিয়ে রাখবে? কোই বাঁচাবে না, বাবুজি, কোই বাঁচাবে না।”
গাড়ির গতি এমনিতেই কম। সেটা আরও কমে যাওয়ায়ঝতে পারছিলুম যে, একটা-কোনও স্টেশন আসছে। আগরওয়ালজি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, “সামনেই ঝিংড়া টিশান। ইখানে নেমে যাব। আজ আর বিষাণগড়ে ফিরছি না, ইখানে একটা জঙ্গলের ইজারা নিয়ে কথা বলবার আছে। কথাবার্তা মিটিয়ে রাতটা ইখানেই কাটাতে হবে, তারপর কাল আবার এই ট্রেনে আমি ফিরব। তো বাবুজি, আপনার কথা তো কিছুই জানা হল না।”
“কী কথা?”
“আপনি বিষাণগড়ে যাচ্ছেন কেন? সির্ফ বেড়াতে?” বললুম, “না, না, আমি চাকরি করতে যাচ্ছি।”
“কিসের চাকরি? এই রেল-কোম্পানির?”
“না, আমি বিষাণগড়ের রাজ-এস্টেটে কাজ করব। প্যালেসের কেয়ারটেকার।”
শুনে চোখ গোল হয়ে গেল আগরওয়ালজির। দুই হাতে দুই কানের লতি ছুঁয়ে জিভ কেটে,হাত জোড় করে বললেন, “সিয়ারাম, সিয়ারাম, তবে তো ভারী গলতি হয়ে গেল!”
“কিসের গলতি?”
“ওই যে রাজাদের সব পুলি বললাম। আরে ছি ছি, খুব খারাপ কাজ করেছি। আমি কাজ-কারবার করি, ই-সব কথা যদি রানি-মা জানতে পারে তো আমার কারবার লাটে উঠবে।”
“আরে জানতে পারবে কেন?” আগরওয়ালজিকে অভয় দিয়ে বল।ম, “কথা যা হয়েছে, সে তো আপনার আর আমার মধ্যে হয়েছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্য কেউ এ-সব কথা জানতে পারবে না।”
শুনে আগরওয়ালজির মুখে আবার হাসি ফুটল। ট্রেন থেমেছে। তিনি নেমে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দরজা থেকে আবার ফিরে এসে বললেন, “আপনার সঙ্গে টর্চ আছে বাবুজি?”
বললুম, “না।”
আগরওয়ালজি তাঁর ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে বললেন, “এটা রাখুন। এই লাইনের গাড়িতে আলোর ব্যবস্থা নেই। একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে যাবে তো, তখন টর্চ না থাকলে অসুবিধায় পড়বেন। না না, ডাকু-উকুর ভয় নেই, ইখানকার লোকজন খুব ভাল। …আচ্ছা, তা হলে চলি বাবুজি। রাম রাম।”
আগরওয়ালজি নেমে গেলেন।
ফেব্রুয়ারি মাস। দিন এখনও বিশেষ বড় হয়ে ওঠেনি। সারা দুপুর রোদ্দুরে সব ঝলমল করছিল, কিন্তু বিকেল না হতেই সূর্য ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল, আর তার খানিক বাদেই সন্ধেটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল অন্ধকার। জঙ্গলের উঁচু-উঁচু গাছপালার আড়ালে অস্তাভ সূর্য যে কখন কীভাবে গা-ঢাকা দিয়ে হারিয়ে গেল, তার টেরও পাওয়া গেল না। শীত করছিল। তাই টর্চ জ্বেলে সুটকেস থেকে আলোয়ানটা বের করে গায়ে জড়িয়ে নিলুম। ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢেলে নিলুম খানিকটা। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝলুম যে, ফ্লাস্কটা সুবিধের নয়, চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছু করবারও নেই। অগত্যা চুপচাপ বসে-বসে দেখতে লাগলুম যে, কামরার মধ্যে গোটাকয়েক জোনাকি ওড়াউড়ি করছে। তা ছাড়া, যেমন ভিতরে, তেমন বাইরেও একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।
ছোট-মেসোমশাই বলেছিলেন, ভিরিন্ডি থেকে বিষাণগড়ে পৌঁছতে পাঁচ-ছ ঘণ্টা লাগবে। আসলে আরও একঘণ্টা বেশি লাগল। ভিরিণ্ডি থেকে দেড়টায় ট্রেন ছেড়েছিল। সেই ট্রেন যখন বিষাণগড়ে পৌঁছল, রাত তখন সাড়ে আটটা বাজে।
নতুন জায়গামাত্রেরই কিছু না কিছু রহস্য থাকে। তার ওপরে যদি রাত্তিরে সেখানে পৌঁছই, তা হলে তার রহস্য যেন আরও হাজারগুণ বেড়ে যায়। ছোট্ট স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম মাত্র একটাই, তাও খুব নিচু, রেলের লাইন থেকে তার উচ্চতা বোধহয় এক ফুটের বেশি হবে না। আলো অবশ্য এখানে কিঞ্চিৎ বেশি। তার কারণ, একে তো এটাই এই লাইনের টার্মিনাস স্টেশন, তার উপরে আবার বিষাণগড় স্টেটের এটাই রাজধানী। রাজ্য আর রাজধানীর একই নাম।
অনেকক্ষণ তো অন্ধকারে ছিলুম, তাই আলোর রাজ্যে পৌঁছে প্রথমে চোখ একটু ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের উপরে পরপর কয়েকটা ব্যতিস্তম্ভ। তার কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। জিনিসপত্র বলতে আমার নেহাতই একটা সুটকেস, একটা শতরঞ্জি, একটা হাওয়া-বালিশ আর সদ্য পাওয়া সেই টর্চ। সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছিলুম, তারপর ধীরেসুস্থে বাইরে বেরোবার গেটের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় একটা বাতিস্তম্ভর তলা থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, “আপনি নিশ্চয় চ্যাটার্জি-বাবু!”
“হ্যাঁ। আপনি?”
“আমার নাম নারায়ণ ভার্মা, আমি রাজবাড়ির মুনিম, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।” বলে পাশের লোকটিকে মুনিমজি একটা ধমক লাগিয়ে বললেন, “হা রে বুধন, উজবুকের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাবুজির হাত থেকে সামানগুলো নিম্ন গাড়িতে তুলে দিয়ে আয়।” তারপর আমার দিকে তাকিয়ে গলার স্বর তিন পর্দা নামিয়ে বললেন, “গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন… বাইরে গিয়ে উঠে পড়া যাক।”
গাড়ি মানে মোটরকার নয়, টাঙ্গা। স্টেশনের চত্বর থেকে বেরিয়ে মিনিট দশ-বারো এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে তারপর টাঙ্গা একটা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। মুনিমজি বললেন, “নদীর ধার বরাবর এই যে রাস্তাটা দেখছেন, এটাই প্যালেস রোড। এই রাস্তা ধরে সিধে যদি উত্তর দিকে হেঁটে যান, তা হলেই রাজবাড়িতে পৌঁছে যাবেন।”
এতক্ষণ যে-সব রাস্তা দিয়ে এসেছি, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, জায়গাটা পাহাড়িয়া। সে-রকম চড়াই-উতরাই নেই ঠিকই, তবে কিনা একেবারে সমতলও নয়; জমি যে ঢেউ-খেলানো, গাড়ির মধ্যে বসেই তা আমি আন্দাজ করতে পারছিলুম। রাস্তায় কিছু-কিছু বাড়িঘরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। অধিকাংশই খাপড়ার চালের বাড়ি। তার মধ্যে বেশির ভাগই অন্ধকার। রাস্তায় অনেক দূরে-দূরে ল্যাম্পপোস্ট, তাতে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে বটে, কিন্তু এত কম পাওয়ারের বাল্ব যে, পথের অন্ধকার তাতে বিশেষ কাটছে না।
প্যালেস রোডে এসে কিন্তু দেখলুম যে, ছবিটা একেবারে পালটে গেছে। এতক্ষণ আমরা নদীর পশ্চিম পারে ছিলুম, এখন ব্রিজ পেরিয়ে পুব পারে চলে এসেছি। আলোর জেল্লা এখানে অনেক বেশি। রাস্তাটাও এখানে এবড়ো-খেবড়ো নয়, একেবারে মসৃণ। রাস্তার একদিকে নদী, সে-দিকে কোনও বাড়িঘর দেখলুম না, অন্যদিকে কম্পাউন্ডওয়ালা চমৎকার সব বাড়ি। এটাই মনে হল শহরের শৌখিন এলাকা। মুনিমজিকে সে-কথা বলতে তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, “রাস্তার ডানদিকে এই যে সব বাড়ি দেখছেন, এর বেশির ভাগই সরকারি বাংলো। রাজ-এস্টেটের নোকরির তো অনেক ধাপ আছে, তো কার ধাপ কত উঁচু, আর দরবারে কার কীরকম পজিশন, সেইটে বুঝে এ-সব বাংলো অ্যালট করা হয়।”
“কে অ্যালট করেন?”
“অ্যাদ্দিন তো ত্রিপাঠীজি অ্যালট করতেন, তিনি রিটায়ার করেছেন, এখন থেকে তাই আপনাকেই অ্যালট করতে হবে। এটা কেয়ারটেকারের বাড়তি কাজ। তা কাজটা তো আপনি খাতায়-কলমে করবেন, ডিসিশন তো আর আপনাকে নিতে হচ্ছে না। উপরে কলকাঠি নড়বে, নীচে হুকুম আসবে, আপনি সেই হুকুম তামিল করবেন, বাস্, মিটে গেল!”
“অর্থাৎ উপরতলায় যে যত ধরাধরি করতে পারবে, তার তত ভাল বাংলো, কেমন?”
মুনিমজি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন, তাই কথাটার কোনও জবাব দিলেন না। তা ছাড়া, রাজবাড়ির ফটকে ইতিমধ্যে পৌঁছেও গিয়েছিলুম আমরা। ফটকের সামনে টাঙ্গা থামাতে পাহারাদার এগিয়ে এসে আমাদের নজর করে দেখল। মুনিমজিকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে। মুনিমজি বললেন, “প্যালেসের কেয়ারটেকার, আজই এসেছেন, আউটহাউসের দোতলায় এঁরই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।”
ফটক খুলে দেওয়া হল। টাঙ্গা গিয়ে ভিতরে ঢুকল। বেশ রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, তাই রাজবাড়ির চৌহদ্দি যে ঠিক কতটা, সেই সঙ্গে প্যালেসটাই বা কেমন ধাঁচের আর কতখানি ছড়ানো, সেটার কোনও স্পষ্ট ধারণা হল না।
আউটহাউসের দোতলায় উঠে আমার কোয়ার্টার্স দেখে যে দারুণ খুশি হয়েছিলুম, এইটে এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চমৎকার ফ্ল্যাট। পুরোপুরি ফার্নিশড। দুটো ঘর। একটা শোবার, একটা বসবার। শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুম। কিন্তু কিচেন নেই। মুনিমজিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, “কিচেনের কোনও দরকার তো আপনার হচ্ছে না। সকালবেলার বেড-টি থেকে শুরু করে রাতের খাবার, সবই তো রাজবাড়ির কিচেন থেকে আপনাকে পৌঁছে দেওয়া হবে।”
রানি-মা’র সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে কি না, তাও জিজ্ঞেস করেছিলুম। মুনিমজি বললেন, “কী করে দেখা করবেন? রানি-মা তো এখন পঞ্জাবে। হপ্তাখানেক বাদে ফিরবেন। তখন যদি আপনাকে ডেকে পাঠান, তো দেখা হবে। নিজের থেকে আপনি দেখা করতে যাবেন না, তার নিয়ম নেই।”
“আমার কাজটা তা হলে কার কাছে বুঝে নেব?”
“ত্রিপাঠীজি এসে কাল আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। আপনার আগে তিনিই ছিলেন এখানকার কেয়ারটেকার। জানুয়ারি মাসের শেষে তাঁর ছুট্টি হয়ে গেল। ইউ. পি.’র লোক, সেখানে ফিরে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু কাউকে দায়িত্বটা বুঝিয়ে না দিয়ে ফিরবেন কী করে? তাই দিন কয়েকের জন্যে রয়ে গেলেন।”
“তার মানে তো তিনিই এই কোয়ার্টার্সে থাকতেন। এখন তা হলে আছেন কোথায়?”
মুনিমজি হেসে বললেন, “এখানে তিনি কোনও দিনই থাকেননি। সির্ফ ওই কিচেনের জন্যেই থাকেননি। গোঁড়া বামুন তো, রাজবাড়ির কিচেনের খাবার তাই মরে গেলেও খানে না। বলতেন, ওখানে পঞ্চাশ জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি, ওখানকার জল খেলেও তাঁর জাত যাবে। এদিকে এই কোয়ার্টার্সে তো কিচেন নেই, তা হলে রান্না করবেন কোথায়। বাধ্য হয়ে তাঁর জন্যে তাই আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।”
“সে-বাড়ি কোথায়?”
“প্যালেসের বাইরে। সেখান থেকে সকাল-সকাল দৃটি খেয়ে এখানে চলে আসতেন। তারপর সারা দিন এখানে কাজকর্ম করে আবার রাত্তিরে সেখানে ফিরে যেতেন। কিন্তু ওই যে বললুম, যতক্ষণ এখানে থাকতেন, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খেতেন না।”
“এই কোয়ার্টার্সে অ্যাদ্দিন তা হলে কে থাকত?”
“কেউ থাকত না। আপনি না আসা পর্যন্ত এটা খালি পড়ে ছিল।” মুনিমজি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “আর নয়, অনেক রাত হল, এবারে চলি। যাবার আগে রাজবাড়ির কিচেনে বলে দিয়ে যাচ্ছি, আপনার রাতের খাবারটা ওরা এখানে পৌঁছে দেবে।”
বললুম, “বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি, রাতে আর কিছু খাব না। কাল থেকেই জার্নির ধকল চলছে তো, শরীর আর টানছে না, এবারে শুয়ে পড়ব।”
“একেবারে লঙ্ঘন দেবেন? সেটা কি ঠিক হবে? বলেন তো হাল্কা কিছু খাবার, এই ধরুন ফল আর মিষ্টি পাঠিয়ে দিতে বলি।”
“কিচ্ছু দরকার নেই,” হেসে বললুম, “আপনি অত উতলা হবেন না তো। ঘুম দিলেই শরীরটা একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে।”
“কিন্তু বেড-টি খান তো? সেটা কাল সকালে কখন দিয়ে যেতে বলব?”
“ছ’টা থেকে সাড়ে ছ’টার মধ্যে দিলেই চলবে।”
“ঠিক আছে, সকাল ছ’টাতেই দিয়ে যাবে।”
মুনিমজি চলে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর জুতোর শব্দ ক্রমে মিলিয়ে এল। বাথরুমের ভিতরটা তখনও দেখা হয়নি। জল আছে কি না জিজ্ঞেস করায় মুনিমজি বলেছিলেন, কিছু অসুবিধে নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই জল পাওয়া যাবে। ভাবলুম, এত রাতে স্নান করাটা ঠিক হবে না, ভাল করে মুখহাত ধুয়ে এবারে টান হওয়াই ভাল।
বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়েও কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। প্রথমে মনে হয়েছিল চোখের ভুল, কিন্তু তারপরেই বুঝলুম যে, তা নয়, ভিতরের দিক থেকে বাথরুমের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।
জীবনে কখনও বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করিনি, কিন্তু দরজার আড়াল থেকে প্রথমেই যেটা বেরিয়ে এল, সেটা যে একটা বন্দুকের নল ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।
যার বন্দুক, সেও পরক্ষণে বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। সতেরো আঠারো বছর বয়সের একটি ছেলে। নতুন তামার-পয়সার মতো গায়ে। রঙ, থুতনির একটু উপরে বাঁ-গালে একটা কাটা দাগ, চোখ দুটি বড়-বড়, কিন্তু একটু রাগী ও অস্থির। মুখের গড়ন লম্বাটে, ধারালো। পরনে যোধপুরী ব্রিচেস আর বুক-খোলা শার্ট। গলায় লাল বুটিদার একটা রেশমি স্কার্ফ।
ডান কাঁধে বন্দুকের কুঁদো, বাঁ হাতের তালুর উপরে নল, ট্রিগারে ডান হাতের তর্জনী, বাথরুম থেকে বেরিয়ে ছেলেটি শোবার ঘরের মধ্যে এশে দাঁড়াল, তারপর মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে বন্দুকের নলটাকে সরাসরি আমার বুকের দিকে উঠিয়ে শুকনো গলায় বলল, “ডোন্ট মুভ! ফর, ইফ ইউ ডু, ইউ উইল গেট্ হার্ট!”
সম্ভবত নিজের অজান্তেই এক-পা এগিয়ে গিয়েছিলুম। তৎক্ষণাৎ এক-পা পিছিয়ে এসে একেবারে নিশ্চল একটা পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি। ছেলেটি একই রকমের শুকনো গলায় বলল, “দ্যাট্স বেটার। নাউ টেল মি, আর ইউ আ ফ্রেন্ড অর অ্যান এনিমি?”
কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিলেই রেহাই মিলবে কি না, তাও না। তবু স্রেফ আত্মারক্ষার তাগিদে বললুম, “হোয়াই, আ ফ্রেন্ড অফকোর্স!”
বন্দুক নামিয়ে নিল ছেলেটি। বলল, “ববি পানিশেস হিজ এনিমিজ, বাট দ্যাট্স নট দ্য ওলি থিং হি লাইক্স টু ডু। হি অলসো রিওয়ার্ডস হিজ ফ্রেন্ডস্। সিন্স ইউ আর আ ফ্রেন্ড, ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড।”
ব্রিচেসের পকেট থেকে চকোলেটের মস্ত একটা স্ল্যাব বার করে আমার দিকে ছুড়ে দিল ছেলেটি। তারণর, যেন কোনও ষড়যন্ত্র করছে, এইভাবে, আমার কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিস করে বলল, “দ্যাট্স ফর দ্য প্রেজেন্ট। বাট থিংস আর লুকিং আপ। সিংহাসনটা এবারে ঠিক উদ্ধার করতে পারব, আর সিংহাসনে বসেই আমি কী করব জানো,… আই শ্যাল মেক ইউ মাই দিওয়ান। …কী, চুপ করে রইলে কেন? বলছি তো, ইংরেজের কুত্তা ওই কপুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাকেই আমার দেওয়ান করব। তাতেও খুশি নও?”
একে তো আমার বোধবুদ্ধি একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, তার উপরে আবার এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম যে, মুখ দিয়ে কোনও কথাই সরছিল না। তবু, যার হাতে বন্দুক, তার তাবৎ কথায় সায় দেওয়াই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এই সহজ কথাটা তখনও নিশ্চয় ভুলে যাইনি; তাই, শুকনো ঠোঁটের উপরে বার কয়েক জিভ বুলিয়ে অস্ফুট গলায় বললুম, “ও ইয়েস, আই অ্যাম হ্যাপি…এক্সট্রিমলি হ্যাপি!”
“ভেরি গুড। কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো, একটু যদি অন্যমনস্ক হয়েছ, তো ডিকি তোমাকে শেষ করে দেবে। দ্যাটস হোয়াই আই অ্যাম নেভার অফ মাই গার্ড। ভাবতে পারো, দ্যাট বাস্টার্ড হ্যাজ বিন ট্রাইং টু সেন্ড মি টু অ্যান অ্যাসাইলাম? সেজ আই অ্যাম ম্যাড…অফ্ মাই রকার! বাট দেন হি ইজ অ্যান এনিমি, অ্যান্ড হি উইল বি পানিশ্ড্।”
বলেই হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল ছেলেটি। তারপর বন্দুক ঘাড়ে তুলে, মার্চ করবার ভঙ্গিতে ‘লেফট্ রাইট…লেফট্ রাইট’ বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।