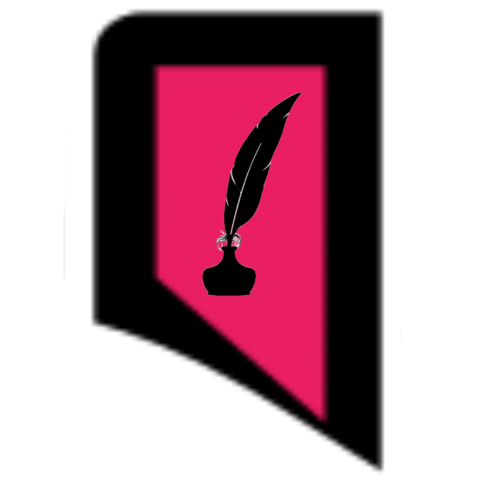বিষাণগড়ের সোনা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১
গেস্ট হাউসের দোতলার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। নীচে ড্রাইভওয়ে, তার দু’পাশে লন। যে গেট দিয়ে এই বাড়িতে ঢুকতে হয়, সেটা খোলা। গেটের ওদিকে এই ছোট্ট শহরের সবচেয়ে চওড়া রাস্তা, প্যালেস রোড। রাস্তার এদিকে, এই গেস্ট হাউসেরই মতো, পরপর কয়েকটা বাগানওয়ালা বাড়ি। বাঁ দিকে ডক্টর সিদ্দিকির বাড়ির দোতলায় একটা ঘরে এতক্ষণ আলো জ্বলছিল, একটু আগে নিবেছে। ডাইনে যমুনাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের বাংলো। বাড়িটা। সেই সন্ধে থেকেই অন্ধকার।
প্যালেস রোডের ওদিকে একটাও বাড়ি নেই। গোটাকয়েক ঝুপড়ি দোকানঘর ছিল, সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাস্তার একটা দিক একদম ফাঁকা। শুধু সারি-সারি কিছু গাছ আর দূরে-দূরে কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট প্যালেস রোডের দুই দিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এখন শুক্লপক্ষ, তাই ল্যাম্পপোস্টের মাথায় আলো জ্বলছে না। চাঁদ উঠেছে, কিন্তু আকাশটা মেঘলা, তাই জ্যোৎস্নার তেমন জোর নেই।
মেঘটা অবশ্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না, ঝোড়ো হাওয়ায় যেমন মুখের আঁচল সরে যায়, ঠিক তেমনই চাঁদের মুখের উপর থেকে মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। যখন সরে যায়, ত্রয়োদশীর চাঁদটা তখন হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নার জোর বেড়ে যায় খানিকটা। তাতে রাস্তার ওদিকটা খানিক স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। বোঝা যায়, রাস্তার ওদিককার খানিকটা জমি সমতল। তারপরেই জমি হঠাৎ ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে। জমির শেষে একটা নদীর চিকচিকে জল আর নদীর পাড়ের ঝুপসি একটা গাছও তখন স্পষ্ট দেখা যায়। একটু নজর করে দেখলে এটাও তখন বোঝা যায় যে, গাছের নীচে, নদীর দিকে মুখ করে একটি মানুষ একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
মানুষটি যে ভাদুড়িমশাই, তা আমি জানি। ঘণ্টাখানেক আগে এই গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে তিনি সর্সোতিয়া নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলুম। তিনি নেননি। এমনকি, বারান্দায় এসে দাঁড়াতেও তিনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, ঘর থেকে আমার বার না-হওয়াই ভাল। যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসছেন, ততক্ষণ যেন আমি ঘরের মধ্যেই থাকি। তা আধঘণ্টার মতো তা আমি ছিলুমও। কিন্তু তারপরে আর বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারিনি। উদ্বেগ আর কৌতূহল এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, বুঝবার জন্যে বিছানা ছেড়ে পা টিপে-টিপে বারান্দায় এসে দাঁড়াই।
তা এখানেও প্রায় আধঘণ্টা আমি দাঁড়িয়ে আছি। হাতঘড়ির রেডিয়াম-ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত এখন একটা বাজতে পাঁচ। চারদিক একেবারে স্তব্ধ। শুধু গাছপালার ভিতর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ কোথাও নেই। চাঁদটা আবার মেঘের আঁচলে মুখ ঢেকেছে। তাই ভাল করে এখ.. আর কিছু ঠাহরও করা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই একসময় মনে হল যে, ভাদুড়িমশাই যা-ই ভেবে থাকুন, আজ আর কিছু ঘটবে না। তা হলে আর এইভাবে রাত জেগে লাভ কী? এমনও একবার ভাবলুম যে, ঢের হয়েছে, আর নয়, এবারে নীচে নেমে যাই, রাস্তাটা পার হয়ে ভাদুড়িমশাই ক গিয়ে বলি, চলুন, এবারে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক।
ঠিক সেই মুহূর্তেই মেঘটা আবার সরে গেল। আর চোখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকানো মাত্ৰ চমকে উঠলুম আমি। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ঢালু জমি বেয়ে আর-একটা লোক দীর দিকে নেমে যাচ্ছে। ভাদুড়িমশাইকেও চোখে পড়ল। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখনও ঠিক সেইভাবেই তিনি—একেবারে নিষ্প্রাণ একটা মূর্তির মতো—নদীর দিকে চোখ রেখে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনের লোকটিকে তিনি দেখতে পাননি।
কালো আংরাখায় শরীর ঢাকা, লোকটি নিঃশব্দে নামছে। ভাদুড়িমশাই আর তার মধ্যে ব্যবধান যখন বড়জোর হাত দুয়েকের, তখন আর সে এগোল না। দাঁড়িয়ে গিয়ে আংরাখার ভিতর থেকে বার করল তার হাত। জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে উঠল একটা ছোরার ফলা।
একবার ভাবলুম, চেঁচিয়ে উঠি, ভাদুড়িমশাইকে সাবধান করে দিই। কিন্তু তার আর সময় পাওয়া গেল না। চেঁচিয়ে উঠবার আগেই বেজে উঠল কলিং বেল। ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতেই বুঝতে পারলুম যে, গায়ের গেঞ্জিটা ভিজে একেবারে জবজব করছে।
দরজা খুলতেই হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার আর থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে সদানন্দবাবু ভিতরে ঢুকলেন। বসবার ঘরের সেন্টার টেবিলের উপরে সে-দুটোকে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, “ধন্যি মানুষ বটে আপনি, কতক্ষণ ধরে কলিং বেল বাজাচ্ছি। অথচ আপনার ঘুমই ভাঙতে চায় না!” তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, “ওরেব্বাবা, ঘেমে যে একেবারে নেয়ে উঠেছেন দেখছি।”
বললুম, “বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখছিলুম। ভাগ্যিস এসে পড়লেন, নইলে ভাদুড়িমশাইকে নির্ঘাত মারা পড়তে হত।”
“তার মানে?”
“মানে আর কী, স্বপ্ন দেখছিলুম যে, পিছন থেকে একটা লোক ভাদুড়িমশাইকে ছোরা মারতে যাচ্ছে।”
ব্যাপারটা যে বাস্তব নয়, একেবারেই অলীক, এতক্ষণে সেটা সদানন্দবাবু বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, “ও, স্বপ্ন? তা-ই বলুন। আমি তো মশাই ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। …যান, আর দেরি করবেন না, মুখচোখ ধুয়ে এসে চা-জলখাবার খেয়ে নিন। আমি বরং ততক্ষণ আজকের কাগজটার উপরে চোখ বুলোই।”
শ্যামনিবাসের সদানন্দবাবুকে আপনাদের না-চিনবার কথা নয়। ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী। বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। কিন্তু চেহারা দেখে তা কারও বুঝবার জো নেই। সদানন্দবাবুর বয়স এখন তা প্রায় বাহাত্তর-তিয়াত্তর। কিন্তু এই বয়সেও শরীর-স্বাস্থ্য বেশ মজবুত রেখেছেন। থাকেন আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে। নিত্য আমার খোঁজখবর নেন। পরোপকারী, হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল মানুষ।
সারাক্ষণ যাঁরা পরোপকার করবার জন্য ছটফট করেন, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের অনেকেই একটু গায়ে পড়ে উপদেশ দেন। তা যাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি সেটা পছন্দ করুন আর না-ই করুন। সদানন্দবাবুও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তিনিও দেখেছি গায়ে-পড়ে উপদেশ দিতে ভালবাসেন। অনেকে তাতে বিরক্ত হয়। আমি হই না।
কেন বিরক্ত হব? তাঁর তাবৎ উপদেশ মান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্তত একটা উপদেশ মান্য করে যে আমার উপকারই হয়েছে, সেটা তো আর অস্বীকার করতে পারি না। একে তো আমি গেঁটে-বাতের রুগি, মাঝে-মাঝেই আমার আঙুলের গাঁট ফুলে গিয়ে ব্যথায় যেন শরীর একেবারে ঝঝন্ করতে থাকে, তার উপরে আবার হাইপার অ্যাসিডিটিও আমাকে দারুণ ভোগাত। সদানন্দবাবু সে-কথা জানবামাত্র নিত্য আমাকে বলতে শুরু করেন, ‘সিগারেটটা ছাড়ুন মশাই; আর হ্যাঁ, ওই দুধ-চিনি দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাসটাও আপনাকে ছাড়তে হবে। নইলে মশাই ভগবানও আপনাকে বাঁচাতে পারবেন না।’
সিগারেটটা ছাড়তে পারিনি ঠিকই, তবে কমিয়েছি। দিনে আগে পঞ্চাশ-ষাটটা সিগারেট খেতুম, এখন চার-পাঁচটার বেশি খাই না। দুধ-চিনি মিশিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাসটা অবশ্য পুরোপুরি ছেড়েছি, এখন শুধুই হাল্কা লিকার খাই। তাতে যে উপকার পাচ্ছি, সেটা অস্বীকার করব কেন? বুক জ্বালা করে না, চোঁয়া ঢেকুর ওঠে না, অ্যাসিডিটি একেবারে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে।
সদানন্দবাবু বলেন, “গেঁটে-বাতও বিদায় নেবে। অম্বলকে যেমন বিদায় করেছেন, তেমন ওটাকেও এবার তাড়ান। কিন্তু হ্যাঁ, তার জন্যে আপনাকে মর্নিং ওয়াক ধরতে হবে। আমাকে দেখছেন তো, ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তা ধরুন মাইল তিনেক হেঁটে আসি। তবে হ্যাঁ, রোদ্দুর উঠে গেলেই সর্বনাশ। আপনাকেও ঠিক আমারই মতো ভোর-পাঁচটায় বেরোতে হবে, তারপর অন্তত এক ঘণ্টা হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। দেখবেন, গেঁটে-বাতও তা হলে আর আপনাকে কাবু করতে পারবে না। কী মশাই, রাজি?”
রাজি তো অবশ্যই। কিন্তু বহুকাল যে-লোকটা সূর্যোদয় দেখেনি, ভোর পাঁচটায় সে ঘুম থেকে উঠবে কীভাবে? খবরের কাগজে কাজ করি, সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে-ফিরতেই তো রাত ন’টা-দশটা। তারপরে থাকে নিজের লেখাপড়ার কাজ, যে-বইটা প্রেসে রয়েছে তার প্রুফ দেখার কাজ, শুতে-শুতে তাই রাত তা প্রায় একটা বেজে যায়। তা হলে আর ভোর পাঁচটায় কী করে বিছানা ছাড়ি? পরপর ক’দিন চেষ্টা করেও যখন পারা গেল না, তখন একদিন সদানন্দবাবুকে বলেও ফেললুম যে, জীবনে তো অনেক ভাল কাজই করা হয়নি, তা এটাও আমার দ্বারা হবার নয়।
সদানন্দবাবু তবু হাল ছাড়েননি। ভদ্রলোকের এক কথা, গেঁটেবাতের যন্ত্রণা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করবেনই। তা এই যে আমার উপকার করবার আগ্রহ, শ্যাম-নিবাসের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর থেকেই এটা আরও বেড়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা হয়তো আপনাদের মনে নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। সেলামি নয়, আগাম তিনমাসের ভাড়া পর্যন্ত নয়, স্রেফ মুখের কথায় বিশ্বাস করে সদানন্দবাবু তাঁর বাড়ির একতলাটা সেবার একজন উটকো লোককে ভাড়া দিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস্, তার কিছুদিন বাদেই সেই ভাড়াটে খুন হল, আর ভদ্রলোক জড়িয়ে গেলেন একটা বিচ্ছিরি মামলায়। তবে তাঁর ভাগ্য ভাল, ভাদুড়িমশাই সেইসময় কলকাতায় ছিলেন। কেটা যদি তিনি না নিতেন, সদানন্দবাবুকে তা হলে সম্ভবত সেই মামলা থেকে ছাড়িয়ে আনা যেত না। ফাঁসি না হোক, যাবজ্জীবন হতই। তা ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগটা যেহেতু আমিই করিয়ে দিয়েছিলুম, সদানন্দবাবু তাই আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় একেবারে আপ্লুত হয়ে আছেন। মুখে যদিও সেই ঘটনার কোনও উল্লেখ তিনি করেন না, তবু বুঝতে পারি, আমার জন্যে কিছু-একটা করবার সুযোগ পেলে তিনি বর্তে যান।
সুযোগ এ-যাত্রায় বাসন্তীই করে দিয়েছে। বড়-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে থাকে এলাহাবাদে, কলকাতায় থাকি আমি, বাসন্তী আর আমাদের ছোট-মেয়ে পারুল। তা দিন দশেক আগে খাওয়ার টেবিলে বাসন্তী হঠাৎ বলে বসল, “জগন্নাথ এক্সপ্রেসে তিনটে বার্থ চাই। দুটো লোয়ার, একটা আপার। তরশু পুরী রওনা হবার কথা।”
ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললুম, “কারা রওনা হচ্ছে?”
“পরে বলছি। আগে বলো, রিজার্ভেশানটা করিয়ে দিতে পারবে?”
ভাতের গ্রাসটা মুখের কাছে এসে গিয়েছিল। হাতটা নামিয়ে নিয়ে বললুম, “তা হয়তো পারা যাবে। আজকাল অবশ্য সবই কম্পিউটারাইজড়, তবে কিনা আমাদের ট্রাভল এজেন্ট মলয় অতি তুখোড় ছেলে, কিছু-না-কিছু বার্থ তো ওর ঝুলির মধ্যে থাকেই, জগন্নাথ এক্সপ্রেসের তিনটে বার্থ কি আর দিতে পারবে না? কিন্তু তা না হয় হল, যাচ্ছে কারা?”
“আমি যাচ্ছি, পারুল যাচ্ছে, তুমিও যাচ্ছ।”
ভাতের গ্রাসটা আবার নামিয়ে রাখতে হল। বললুম, “তার মানে? আমি এখন কী করে যাব? না না, হাতে এখন বিস্তর কাজ, আমার এখন যাওয়া হবে না। যেতে হয় তো তোমরা যাও, দিন কয়েক একটু ঘুরে এসো।” তারপর একটু থেমে বললুম, “কিন্তু আমি না-গেলে তোমরাই বা যাবে কী করে? থাকবে কোথায়?”
বাসন্তী গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলল, “তা নিযে তোম।কে ভাবতে হবে না। মেজদিরা পুরী যাচ্ছে। চক্রতীর্থে একটা মস্ত বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ঘর কি পাঁচ-ছ’খানা। তাই বলছিল যে, আমরাও যদি যাই তো বেশ হয়।”
বললুম, “তা হলে আর ভাবনা কী? ‘
বাসন্তী বলল, “ভাবনা তোমাকে নিয়ে। নিজে তো কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে শেখোনি, সকালবেলার চা থেকে রাত্তিরের খাওয়ার পরের মশলাটা পর্যন্ত তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হয়। সে-সব কে এগিয়ে দেবে? কে কেচে দেবে তোমার গেঞ্জি আর রুমাল? নিজে তো দেখি ফাউন্টেন পেনের কালিটা পর্যন্ত ভরতে পারো না। তা হলে?”
ভাবলুম বলি যে, এইজন্যেই আমাদের পূর্বপুরুষরা একাধিক বিয়ে করতেন। কিন্তু বাসন্তীর মুখচোখ দেখে আর হাল্কা গলাতেও কথাটা বলবার সাহস হল না। তার বদলে কালুম, “আরে দূর, ও-সব কি একটা সমস্যা নাকি? আসল সমস্যা তো পাওয়ার। তা আমাদের অফিসে চমৎকার ক্যান্টিন রয়েছে। তোমরা তো আর সাতদিনের বেশি বাইরে থাকছ না, ও আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারব।”
“সকালবেলার জলখাবারটা কে করে দেবে?”
“সেটাও কোনও সমস্যা নয়। ফ্রিজের মধ্যে এক প্যাকেট মাখন আর কিছু ডিম রেখে যেয়ো। রোজকার রুটিটা আমি কিনে নেব। বাস্।”
“কিছু বিস্কুটও থাকবে। কিন্তু চা? ওটা তুমি করে নিতে পারবে তো?”
হেসে বললুম, “আমার চা মানে তো ফোটানো-জলের মধ্যে এক-চিমটি চায়ের পাতা। উনুন তো আর ধরাতে হচ্ছে না, স্রেফ গ্যাসটা জ্বেলে জলটা ফুটিয়ে নেব। তার আগে একটা ডিমও সেদ্ধ করে নেওয়া যাবে।”
পারুল এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল সে। বলল, “দেখো বাবা, যে-জলে ডিম সেদ্ধ করবে, তাতেই যেন আবার চা করতে যেয়ো না। তা হলে কিন্তু ভীষণ আঁশটে গন্ধ হবে।”
বললুম, “তুই আর তোর মা আমাকে কী ভাবিস বল্ তো? যা যা, তোরা ঘুরে আয়, আমাকে নিয়ে অত ভাবতে হবে না।”
রিজার্ভেশানের ব্যাপারে কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি। মলয় ঠিকই দুটো লোয়ার বার্থ জোগাড় করে দিয়েছিল। ট্রেন ছাড়বার মিনিট পাঁচেক আগে হঠাৎ বাসন্তী একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবে পুরীতে আমাদের কাগজের এজেন্টকে তো ওদের যাবার কথা জানিয়ে রেখেছিলুম, পরশুদিন তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে বুঝতে পারি যে, মা আর মেয়ে বাইরে গিয়ে বেশ ফূর্তিতেই আছে। পুরী এক্সপ্রেসে কাল সকালে তাদের ফিরবার কথা।
কিন্তু যে-কথা বলছিলুম। বাসন্তী আর পারুলকে যে-দিন হাওড়া ইস্টিশনে গিয়ে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে তুলে দিই, তার পরদিন সকালে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় আটটার সময় সদানন্দবাবু আমার বাসায় এসে হাজির। কথায়-কথায় বাসন্তী হয়তো কখনও ওঁর স্ত্রী কুসুমবালাকে বলে থাকবে যে, সকাল ঠিক আটটায় আমাকে ব্রেকফাস্ট দিতে হয়, ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর কাছে সেটা শুনেছেন নিশ্চয়ই, ফলে একেবারে ঘড়ি দেখে তিনি আমার জলখাবার এনে হাজির করেছেন। শুধু তা-ই নয়, টিফিন ক্যারিয়ার খুলে টেবিলের উপরে জলখাবার সাজিয়ে দিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় চা ঢেলে, ভদ্রলোক বলেছিলেন, “আপনার মিসেস তো এখন কয়েকটা দিন বাইরে তাকবেন। তা এই ক’টা দিন যদি দুপুর আর রাত্তিরের খাওয়াটা আমাদের বাড়িতে সেরে নেন তো হোটেলে খেয়ে আপনাকে আর শরীর নষ্ট করতে হয় না। …না না, আপনার সংকোচের কিছু নেই, বলেন তো দু’বেলার খাবার আমি পৌঁছেও দিয়ে যেতে পারি।
রাজি হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সদানন্দবাবুর স্ত্রীকে জানি তো, বাতের ব্যথায় ভদ্রমহিলা প্রায় পঙ্গু বললেই হয়, হঠাৎ একজন অতিথির বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপলে তিনি ঘোর অসুবিধেয় পড়বেন, তাই প্রস্তাবটা একেবারে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বললুম, “পাগলামি করবেন না তো, আপিসে একটা ক্যান্টিন রয়েছে, তারা খাওয়ায়ও চমৎকার, দু’বেলা সেখানেই খেয়ে নেব।”
ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা অবশ্য অত সহজে নাকচ করা গেল না। ওটাতে যদি আপত্তি করি, সদানন্দবাবুর ‘বেটার হাফ’ তা হলে নাকি দারুণ দুঃখ পাবেন। ব্যাস্, ভদ্রলাক একেবারে সেই থেকেই রোজ টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক-ভর্তি চা নিয়ে আমাদের ‘ফ্ল্যাটে এসে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন। আসেন একেবারে কাঁটায-কাঁটার সকাল আটটায়। একদিনও তার ব্যতিক্রম হতে দেখলুম না।