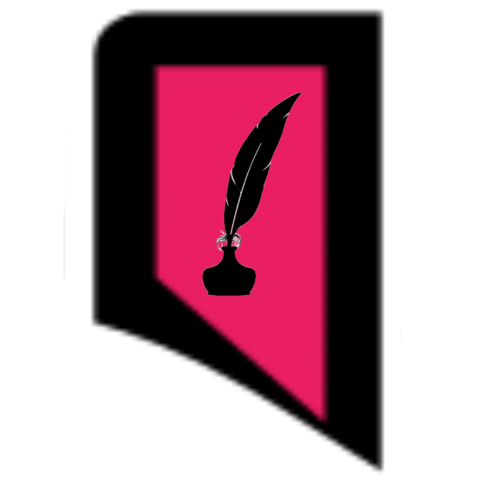বিষাণগড়ের সোনা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬
সরস্বতীর বয়স মনে হল তিরিশের নীচেই। লছমির গায়ের রং ছিল দুধে-আলতায়, সরস্বতী সেটা পায়নি। শ্যামলা রং, গড়ন ছিপছিপে, চোখ দুটি টানা-টানা। শুধু ওই চোখের মধ্যেই লছমিকে যেন খানিকটা খুঁজে পাওয়া যায়। তাও মায়ের চোখের নীলচে রংটা পায়নি। বাদবাকি কোথাও কিছু মিল নেই। এমনকি চুলেও না। লছমির চুল ছিল কোঁকড়া। সরস্বতীর চুল একেবারে সিধে, সেখানে একটা ভাঁজ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। মুখখানা অসম্ভব ধারালো; দেখলেই বোঝা যায় যে, এ মেয়ে খুব সাধারণ নয়, আর-পাঁচটা মেয়ের থেকে একটু অন্য রকমের।
যতীন বাগচি রোডে যাব। গড়িয়াহাট-রাসবিহারীর মোড় থেকে ডাইনে বেঁকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে গেলে সুবিধে হত, কিন্তু তাতে জ্যামে আটকে যাবার সম্ভাবনা। গুরুসদয় দত্ত রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে তাই বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরলুম। এ-রাস্তায় এখনও গাড়ির তত ভিড় হয়নি, সরাসরি দক্ষিণে গিয়ে হাজরা রোড পেরিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে রাসবিহারীতে পড়তে কোনও সমস্যা নেই। তারপর ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে খানিক এগোলেই যতীন বাগচি রোড।
গাড়ি আমি আস্তে চালাই। সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলতে তাই কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কথায়-কথায় জানা গেল যে, সরস্বতীর স্বামী সুমঙ্গনও অধ্যাপক। সেও দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। তবে তার বিষয় আলাদা। জিওলজি নয়, জিওগ্রাফি।
“তোমার মা এখন কোথায় সরস্বতী?”
“কোথায় আবার, আমার কাছেই।” সরস্বতী ম্লান হাসল। “আপনি বোধহয় জানেন যে, আমার মায়ের বয়েস যখন মাত্র পাঁচ, তখনই তাঁর বাবাকে তিনি হারিয়েছিলেন।”
“জানব না কেন, আমি যেদিন বিষাণগড়ে পৌঁছই, তার মাসখানেক আগে তিনি মারা যান। নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। তোমার মায়ের দাদুর কাছে অন্তত সেই কথাই শুনেছি।”
“মায়ের দাদু কেমন মানুষ ছিলেন?”
গঙ্গাধর মিশ্রের চেহারা যেন চকিতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ পুরুষ। কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরনে রেশমি থান, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, বুকের উপরে পৈতে ঝুলছে, হাতে কমন্ডলু, পায়ে খড়ম, –নদীর ঘাটে স্নান সেরে সূর্যবন্দনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি ফিরে আসছেন। দোতলার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন তিনি, আর দেখবামাত্র চমকে উঠলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে তিনি একতলায় তাঁর কোয়ার্টার্সের মধ্যে ঢুকে গেলেন।
তার ঠিক আগের রাত্রে আমি বিষাণগড়ে পৌঁছেছি। একই বাড়িতে থাকতুম বটে, কিন্তু সে রাত্রে আর তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। পরদিন সকালে সেই তাঁকে আমি প্রথম দেখলুম। পরে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ হয়। আমি চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান, অথচ পৈতে ধারণ করি না, এইটে দেখে গঙ্গাধর মিশ্র বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, “বেটা, তোমাকে আর কী বলব, দোষ তো তোমার একার নয়, দোষ এই জমানার, এই কল্যুগের।” তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, “পুরন্দর আমার একমাত্র ছেলে, সেও যজ্ঞোপবীত পরত না। তা হলে আর অন্যকে কী করে দোষ দেব?”
পুরন্দরের কথা সেই আমি প্রথম শুনি। এও শুনি যে, তিনি সর্সোতিয়ার জলে ডুবে মারা যান। আরও মর্মান্তিক ব্যাপার, মৃতদেহটা গঙ্গাধর মিশ্রের চোখেই প্রথম পড়ে। যেমন রোজ করেন, তেমন সেদিনও ভোরবেলায় স্নান করতে গিয়ে গঙ্গাধর মিশ্রই নাকি দেখতে পান যে, রাজবাড়ির ঘাটের কাছে আধডোবা একটা পাথরের চাঙড়ে তার ছেলের মৃতদেহ আটকে রয়েছে। মাথাটা একেবারে থ্যাঁতলানো।
ডাক্তার এলেন। লাশ পরীক্ষা করলেন। তারপর রায় দিলেন, “মনে হচ্ছে এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। সম্ভবত জলে নামবার সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে পথরে চোট লেগে মাথা ফেটেছে।”
রাজবাড়ির ডাক্তার। তাঁর কথার উপরে কে কথা বলবে। আর তাই শেষ-রাত্তিরে পুরুন্দরের হঠাৎ জলে নামবার দরকার হল কেন, এই প্রশ্নটা কাউকে কাউকে একটু বিচলিত করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কেউ মুখ খোলেনি।
এ হল জানুয়ারি মাসের ঘটন’। অর্থাৎ আমি গিয়ে বিষাণগড়ে পৌঁছবার এক মাস আগের ব্যাপার। পুরন্দর বিয়ে করেছিলেন। তাঁর বউ আর একটি মেয়ে রয়েছে। প্রথম পরিচয়ের দিনই গঙ্গাধর মিশ্র তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা আমাকে জানান; সব জানিয়ে তারপর বলেন যে, সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে তাঁর পাঁচ বছরের নাতনি লছমিকে নিয়ে। “বউমা তাঁর শোক কিছুটা সামলে নিয়েছেন বটে, কিন্তু বাপ মরবার পর থেকেই লছগি একেবারে গুম মেবে গেছে।” হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে, সেদিন থেকে সে আর নাকি একটা কথাও কারও সঙ্গে বলছে না।
“এ পেনি ফর ইয়ার থট্স!”
গাড়ি চালাতে-চালাতেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। সরস্বতীর কথায় চমক ভাঙল। লজ্জিত গলায় বললুম, “ও হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?”
“আমার মায়ের দাদু গঙ্গাধর মিশ্রের কথা বলছিলুম। মানুষটি তিনি কেমন ছিলেন?”
“শুনেছি তো এককালে খুবই তেজি মানুষ ছিলেন। রানি-মা, দেওয়ান, রাজবাড়ির ম্যানেজার, কাউকেই নাকি ছেড়ে কথা বলতেন না। তবে কিনা আমি যখন দেখি, তখন তো তিনি সদ্য তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন, তাঁর অবস্থা তখন ঝড়ে-ভাঙা শালগাছের মতো।”
সরস্বতী বিষণ্ণ হাসল। বলল, “বড্ড বেশি প্রাচীনপন্থী ছিলেন, না?”
বললুম, “সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে কিনা খুব একটা অসহিষ্ণু ছিলেন বলে অন্তত আমার কখনও মনে হয়নি। আমি তো বলতে গেলে ব্রাহ্মণ বংশের কুলাঙ্গার, আচার-বিচার জাতপাত কিছু মানি না, না করি সন্ধ্যা: আহ্নিক, না পরি পৈতে, তাও আমাকে ভালবাসতেন।”
“আপনার কথা আলাদা। আপনাকে যে ভালবাসতেন, তার একটা কারণ ছিল। আমার মায়ের কাছে অন্তত সেইরকমই শুনেছি।”
গুরুসদয় দত্ত রোড থেকে বাঁয়ে টার্ন নিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোৎ ধরে দক্ষিণে চলেছি। পিছন থেকে একটা মিনিবাস ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছিল। স্পিড কমিয়ে, যতটা সম্ভব রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেটাকে এগিয়ে যেতে বললুম। তারপর আবার স্পিড খানিকটা বাড়িয়ে, গিয়ার পালটে সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করলুম, “মায়ের কাছে কী শুনেছ?”
“আপনি জানেন না?”
“মনে তো হয় জানি। তবু তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।”
“আপনাকে দেখতে অনেকটা….”
“গঙ্গাধর মিশ্রের সেই ছেলের মতন, এই তো?” সরস্বতীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, “এটা তার জানব না কেন? অনেককেই তো ও-কথা বলতে শুনেছি। আর তা-ছাড়া পুরন্দর মিশ্র অর্থাৎ লছমির বাবার ফোটোগ্রাফ যে আমি দেখিনি, তাও তো নয়।”
“দেখে কী মনে হয়েছিল আপনার?”
“মনে হয়েছিল যেন ওটা আমারই ফোটোগ্রাফ। যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে দেখছি।”
“তা-ই?”
“তা-ই। তফাত যে একেবারেই ছিল না, তা কিন্তু নয়। ছিল। বেশ বড় দুটো তফাত ছিল। তাঁর রং ছিল ফর্সা, আর আমার রং যে কালো, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তা ছাড়া তাঁর কপালে একটা জড়ুল ছিল, আমার সেটা নেই। দু’জনের হাইটেরও কিছু ফারাক থাকতে পারে। তবে সব-মিলিয়ে মিলটাই ছিল চোখে পড়বার মতো।”
অস্ফুট গলায় সরস্বতী বলল, “মিলটা আমার মায়ের চোখেও পড়েছিল।”
বললুম, “চোখে পড়েছিল বললে খুব কমই বলা হয়, সরস্বতী। পাঁচ বছরের মেয়ে, বোধবুদ্ধি হয়নি, লছমি বোধহয় ভেবেছিল যে, তার বাবাই আবার ফিরে এসেছে। নয়তো তার বাবার মৃত্যুর পরে যে-মেয়ে পুরো একটা মাস কারও সঙ্গে কোনও কথাই বলেনি, আমি গিয়ে গঙ্গাধর মিশ্রের কোয়ার্টার্সে ঢুকবামাত্র সে ঘরের এক কোণ থেকে ছুটে এসে ‘বাবুজি’ বলে আমাকে আঁকড়ে ধরবে কেন?”
“মা যে ভুল করে আপনাকে বাবুজি ভেবেছিলেন, এটা কেউ তাঁকে বলে দেয়নি?”
“তা কেন বলে দেবে না, আমি বলে দিয়েছিলুম। তক্ষুনি-তক্ষুনি অবশ্য বলিনি, সেটা সম্ভবও ছিল না, তবে প্রথম সুযোগেই তাকে বুঝিয়ে বলেছিলুম যে, আমি বাবুজি নই, বাবুজির ছোট ভাই, তার চাচা। তবে হ্যাঁ, বাবুজি তো বাইরে গেছেন, এখন অনেকদিন আসতে পারবেন না, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাতে লছমিকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতে পারি, তার সঙ্গে ‘ইক্কড় মিক্কড়’ খেলতে পারি, ‘এক খেলাড়ি আয়া থা, উ এক বান্দর লায়া থা’র ছড়াটা তাকে শোনাতে পারি, আর হ্যাঁ, যাতে কিনা অনেক-অনেক গল্প তাকে বলতে পারি।”
হাজরা রোড ধরে একটা মিছিল যাচ্ছে। মাডক্স স্কোয়ারের পুব দিক দিয়ে মোড়ের কাছে এসে পড়েছিলুম, সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে আটকে যেতে হল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সরস্বতীকে বললুম, “কিছু বলছ না যে?”
‘আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গে কিন্তু আরও একটা ফারাক ছিল আপনার। বয়সেও তিনি আপনার চেয়ে বছর-সাতেকের বড় ছিলেন।”
হেসে বললুম, “জানি। সাত বছরের নয়, ন’বছরের। কিন্তু পুরন্দর মিশ্রের মুখে এক ধরনের সারল্য ছিল। এমন সারল্য, যা শুধু শিশুদের মুখেই দেখা যায়। ফলে বয়েসের তুলনায় তাঁকে ছোট দেখাত। কথাটা অন্যদের মুখে শুনেছিলুম। ফোটো দেখে আমার নিজেরও মনে হয়েছিল যে, কথাটা মিথ্যে নয়।”
“মানুষটা তিনি কেমন ছিলেন?”
“পুরন্দর মিশ্রের কথা জিজ্ঞেস করছ?”
“হ্যাঁ।”
“তা আমি কী করে বলব? আমি তো তাঁকে দেখিইনি। তবে হ্যাঁ, অন্যদের কাছে তাঁর কথা কিছু-কিছু শুনেছি বটে। যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, যেমন চেহারায় তেমন স্বভাবেও তিনি ছিলেন শিশুদেরই মতো। কোনও ঘোরপ্যাচের ধার ধারতেন না। সরল স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ। কারও কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনও খারাপ কথা শুনিনি।”
সরস্বতী বলল, “কিন্তু মায়ের দাদু যে তাঁর ছেলের উপরে খুব প্রসন্ন ছিলেন না, সেটা জানেন তো?”
“তাও জানি। গঙ্গাধর মিশ্র নিজেই সে-কথা আমাকে বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলে টোলে পড়বে, সংস্কৃত শিখবে, তারপর পুজো-আচ্চার তাবৎ বিধি-ব্যবস্থা বুঝে নিয়ে তাঁরই মতন বিষাণগড়ের রাজ-পুরোহিত হবে। তা ছেলে গেল ম্লেচ্ছ ভাষা ইংরেজি শিখতে। গঙ্গাধর মিশ্র তাই অপ্রসন্ন তো হতেই পারেন।”
“ছেলে কিন্তু ইংরেজির পাঠও শেষ করলেন না। ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে রায়পুর থেকে বিষাণগড়ে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে তো কিছু একটা করবেন, তা-ই বা করলেন কই। দেওয়ানজি তাঁকে কাঠের ব্যাবসা করতে বলেছিলেন। করেননি। রানি-মা তাঁকে রাজ-এস্টেটে চাকরির অফার দিয়েছিলেন। নেননি।”
বললুম, “শুনেছি। মনে হয়, মানুষটি খুব সংসারী প্রকৃতির ছিলেন না।
সরস্বতী হাসল। বলল, “দাদামশাই যখন মারা যান, মা তো তখন নেহাতই শিশু। বয়েস মাত্ৰ পাঁচ বছর। মা তাঁর বিষয়ে খুব-একটা কিছু বলতে পারেননি, পারা সম্ভবও নয়। তবে দিদিমার কাছে অনেক গল্প শুনেছি।”
“তোমার দিদিমাকে প্রথম-প্রথম আমি ‘ভাবি’ বলতুম। আর তিনি আমাকে ‘ভাইয়া’। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিলেন। একদিন বললেন, তাঁর নিজের কোনও ভাই নেই, তাই আমি যদি তাঁকে ‘দিদি’ বলে ডাকি, তো তিনি খুব খুশি হবেন। সেইদিন থেকেই তাঁকে “দিদি” বলতে শুরু করি। বড় ভালমানুষ ছিলেন। তা তিনি এখন কোথায়?”
“যেমন মা, তেমন দিদিমাও এখন আমার কাছেই থাকেন?”
“তোমার বাবা?”
সরস্বতী আবার হাসল। ম্লান হাসি। বলল, “মায়ের সঙ্গে আর তো কোনও মিল নেই আমার, কিন্তু এইখানেই একটা মস্ত মিল। আমিও একেবারে ছেলেবেলাতেই আমার বাবাকে হারিয়েছি। ঠিক ওই পাঁচ বছর বয়সেই।”
মিছিল শেষ হয়েছে, সামনের গাড়িগুলি নড়তে শুরু করেছে। আমিও গাড়িতে স্টার্ট দিলুম। হাজরা ক্রস করে দেশপ্রিয় পার্কের পুব দিক দিয়ে রাসবিহারীতে পড়ে টার্ন নিলুম বাঁ দিকে। তারপর ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছে ট্রাম-লাইন পেরিয়ে বললুম, “পুরন্দর মিশ্র সম্পর্কে তোমার দিদিমার কাছে কী শুনেছ?”
“শুনেছি যে, দাদামশাই বড় খেয়ালি মানুষ ছিলেন। তাঁর স্বভাবটাই ছিল বাউন্ডুলে। অথচ কোনও বদ-খেয়াল যে ছিল, তা নয়। শুনেছি বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে বেরিয়ে যেতেন, আর একবার যেতেন তো পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে ফিরতেন না।”
“কোথায় যেতেন?”
“বিশেষ-কোথাও না। স্রেফ পাহাড়ে আর জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। এই নিয়ে দিদিমা কোনও অনুযোগ করলে কী বলতেন জানেন?”
“কী বলতেন?”
“বলতেন যে, মানুষের কথা শুনতে-শুনতে এক-এক সময় তাঁর হাঁফ ধরে যায়। তখন জঙ্গল তাঁকে টানতে থাকে, নদী তাঁকে টানতে থাকে, পাহাড় তাঁকে টানতে থাকে। তাই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। জঙ্গলে গিয়ে গাছপালার কথা শোনেন। নদীর ধারে বসে জলের কথা শোনেন। পাহাড়ে গিয়ে পাথরের কথা শোনেন।”
“বলো কী! এ তো সংসারী মানুষের কথা নয়, সরস্বতী, এ তো কবিতার মতো শোনাচ্ছে।”
“অথচ দাদামশাই কখনও এক-লাইনও কবিতা লেখেননি। তাঁর ওই বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানো নিয়ে দিদিমা যখন খুব বেশি রেগে যেতেন, তখন নাকি হেসে বলতেন যে, ঘুরে না বেরিয়ে তার উপায় কী, তাঁর প্রেমিকা নাকি ওই পাহাড়ে কোথাও বন্দী হয়ে আছে, যতক্ষণ না তাকে খুঁজে বার করতে পারছেন, তাকে মুক্তি দিতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই।”
“এসব-কথা তুমি কোথায় শুনলে?”
সরস্বতী হাসল। বলল, “আমার দিদিমা’র কাছে। দাদামশাই তো খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন, তা মজা করবার জন্যে ওই প্রেমিকার কথা বলে মাঝে-মাঝেই তিনি দিদিমাকে খুব রাগিয়ে দিতেন। বলতেন, তাঁর প্রেমিকার মতন সুন্দরী নাকি দেখাই যায় না। একেবারে কাঁচা হলুদের মতন তাঁর গায়ের রং।”
যতীন বাগচি রোড এসে গিয়েছিল। ডাইনে ঘুরে বিবেকানন্দ পার্কের কাছাকাছি পৌঁছে একটু ফাঁকামতো একটা জায়গা দেখে গাড়ি পার্ক করলুম। তারপর সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললুম, “আমরা পৌঁছে গেছি।”
“নামব?”
“নামবে তো বটেই, এত অস্বস্তি বোধ করছ কেন? ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে তোমার এখনও আলাপ হয়নি, কিন্তু দেখো, তোমার পরিচয় পেলে তিনি খুব খুশি হবেন। লছমিকে তো তিনিও কিছু কম স্নেহ করতেন না।”
সরস্বতী গাড়ি থেকে নোে এল। বলল, “চলুন।”
জানলার কাচ তুলে, গাড়ি লক করে সরস্বতীকে নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় উঠতে-উঠতে বললুম, “একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমরা তো আসলে ইউ. পি.র লোক, তা হলে এত ভাল বাংলা তুমি শিখলে কোথায়?”
সরস্বতী এবারে ঝরঝর করে হেসে বলল, “বা রে, আমি বাঙালি-বাড়ির বউ না? আমার দাদামশাইরা ইউ. পি.’র লোক ঠিকই, ওদিকে আমার বাবাও দিল্লির লোক, চাকরিও করতেন দিল্লিতে, ফলে আমিও দিল্লিতেই পড়ালেখা করেছি, কিন্তু আমার বিয়ে যে হয়েছে এক বাঙালি ভট্চাজের সঙ্গে, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? বিয়ের পরে সুমঙ্গলই আমাকে বাংলা শিখিয়েছে। বলুন, আমি যে অবাঙালি, আমার কথা শুনে সেটা বোঝা যায়?”
বললুম, “খুব খেয়াল করে শুনলে তবেই বোঝা যয়। ‘পড়ালেখা’ না-বলে যদি ‘লেখাপড়া’ বলতে, তা হলে কিন্তু তাও যেত না।”
দোতলায় উঠে এসে কলিং বেল টিপলুম।
কৌশিক এসে দরজা খুলে দিল। দেখলুম, ভাদুড়িমশাই আর অরুণ সান্যাল তার একটু পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। মালতীও তার রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।
ভিতরে ঢুকে বললুম, “সরস্বতী, পরিচয়ের পালাটা আগে চুকিয়ে নেওয়া যাক।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিচ্ছু দরকার নেই। সরস্বতীকে আমরা সবাই চিনি। ও এর আগে দু’বার এই ফ্ল্যাটে এসেছে।”