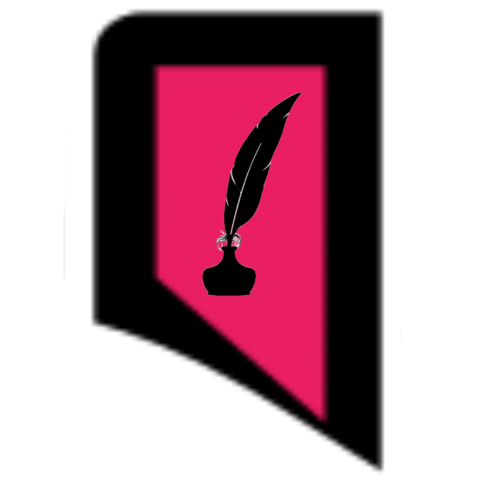বিষাণগড়ের সোনা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪
ইন্টারভিউ হয়েছিল ছেচল্লিশের জানুয়ারির মাঝামাঝি। তারপর এক সপ্তাহ কাটল, দু’সপ্তাহ কাটল, ওঁদের দিক থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। তাতে যে খুব অবাক হয়েছিলুম, তা নয়, কেননা, ওই যে আগেই বলেছি, গোড়ার থেকেই ধরে রেখেছিলুম যে, এ-চাকরি আমার হবার নয়, হবেও না
বরং ফেব্রুয়ারির গোড়ায় একদিন বাড়িতে পিওন এসে, আমাকে দিয়ে সই করিয়ে, যে রেজিস্টার্ড চিঠিখানা দিয়ে গেল, খাম খুলে সেই চিঠি পড়েই আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। মোটা ব্রোমাইড পেপারে টাইপ করা চিঠি। “ডিয়ার স্যার, উই আর গ্ল্যাড টু ইনফর্ম ইউ….”
অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আরও একটা খুশির খবর ছিল। বিজ্ঞাপনে যদিও বলা হয়েছিল যে, মাস-মাইনে তিনশো টাকা, এঁরা আমাকে সাড়ে তিনশো দেবেন। প্রথম তিন বছর সেটা পঞ্চাশ টাকা করে বাড়বে, তারপর থেকে বাড়বে বছরে পঁচাত্তর টাকা করে। বিজ্ঞাপনে যা বলে দেওয়া হয়েছিল, নিয়োগপত্রেও তার উল্লেখ দেখলুম। ফুড আর লজ-এর ব্যবস্থা করা হবে প্যালেস থেকেই, তার জন্য আমার মাইনে থেকে কিছু ‘ডিডাক্ট’ করা হবে না।
কিন্তু আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই। যদি রাজি থাকি, তা হলে যেন কবে আমি বিষাণগড়ে পৌঁছচ্ছি, পত্রপাঠ তা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই; সেই অনুযায়ী স্টেশনে আমার জন্য লোক রাখা হবে।
একে অজানা জায়গা, তায় একা যাচ্ছি, তায় আবার সেখানে না আছে আত্মীয়স্বজন, না বন্ধুবান্ধব কী খেতে দেবে, তা আমার সহ্য হবে কি না, কে জানে। তার উপরে আবার মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বললেন, “কেন, এত-এত লোক এই কলকাতায় চাকরি-বাকরি করছে, আর তোর একটা চাকরি হবে না?”
বললুম, “চাকরি তো করছিই, বেকার। তা আর নই, কিন্তু মাইনেটাই যে পাচ্ছি না।”
“তাই বলে কলকাতা ছেড়ে এই বয়সে একা-একা বিদেশ-বিভুঁইয়ে গিয়ে থাকবি?”
বাবা হেসে বললেন, “ওই তো তোমার মুশকিল, হাওড়া ইস্টিশন থেকে গাড়ি ছাড়লেই চতুর্দিকে তোমার বিদেশ-বিভুঁই শুরু হয়ে যায়। না না, ওকে বাধা দিও না। চাকরি বলে কথা কী, দেশটাকে চেনাও তো চাই। সব দেখুক, সব চিনুক, তাতে ওর ভালই হবে।”
দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। আমার নীচে এক ভাই আর এক বোন। তারা এখনও ইস্কুলের গণ্ডি ছাড়ায়নি। রাজবাড়িতে চাকরি করতে যাচ্ছি শুনে তারা বলল, “ভালই তো, রাজবাড়ির কাজ যখন, তখন দু’বেলা নিশ্চয় রাজভোগ খাওয়াবে। তবে ও-সব খেয়ে আবার আমাদের কথা ভুলে যেয়ো না কিন্তু।”
মা প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাবার কথায় রাজি হলেন।
কিন্তু বিষাণগড়ে যাব কী করে? জায়গাটা যে মধ্যপ্রদেশে, শুধু এইটুকুই তো জানি। কোন্ ট্রেন ধরে কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হয়, মাঝপথে কোথাও ট্রেন পালটাতে হয় কি না, কিছুই তো জানা নেই।
মা বললেন, “তুই বরং সুরেশের সঙ্গে দেখা কর। সে রেলের চাকরি ক…। আমার ধারণা, সে-ই তোকে সব বলে দিতে পারবে।”
সুরেশ মুখুজ্যে আমার মেসোমশাই। হাওড়া ইস্টিশানের দোতলায় বসেন। সেখান গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। সব শুনে তিনি বললেন, “বেশ, বেশ, বাইরে যাচ্ছ, এর চেয়ে ভাল কথা আর কী হতে পারে! বাঙালির ‘ঘরকুনো’ বদনামটা যদি তোমরা ইয়াং ম্যানরা না ঘোচাও, তা হলে তো এ-জাতটার ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার।”
বদনামটা ঘোচাবার জন্য বিষাণগড়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু যাব কী করে?
মেসোমশাই বললেন, “তা তো জানি না বাবাজীবন। আমি তো ই. আই. আর.-এ চাকরি করি, আর তোমাকে যেতে হবে বি. এন. আর. লাইনে। ও-লাইনের খবর তো আমার জানা নেই।”
“তা হলে?”
মেসোমশাই একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, “দাঁড়াও, একটা উপায় কি আর হবে না? হবে। তবে কিনা এক্ষুনি হবে না। তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। উপেনকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিয়ে আমি নাহয় রাত্তিরে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে সব জানিয়ে আসব।”
কে উপেন, কিছু বুঝতে পারলুম না। বেজার হয়ে বাড়ি ফিরলুম। মাকে সব বলতে তিনি বললেন, “উপেনকে চিনিস না? সুরেশের পিসতুতো ভাই। বি. এন. আর.-এ চাকরি করে। অনেকদিন রায়পুরে ছিল, বছর দেড়েক হল কলকাতার আপিসে বদলি হয়েছে। বয়েসে সুরেশের চেয়ে ছোট হলে কী হয়, অনেক বেশি তুখোড়।”
মেসোমশাই এলেন রাত ন’টায়। এসে বললেন, “উপেনের কাছে শুনে যা বুঝলুম, তোমার পথটা তো মোটেই সুবিধের নয় হে।”
বললুম, “ট্রেনে যাব, এতে আবার অসুবিধের কী আছে?”
“নেই?” মেসোমশাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “তা হলে শোনো। রেলগাড়িতে উঠলুম আর ঘুমিয়ে রাত কাবার করে বিষাণগড়ে গিয়ে নামলুম, এ অত সহজ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে মুশকিল কী জানো, বিষাণগড় আসলে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের আওতার মধ্যেই পড়ছে না।”
“তা হলে?” মা জিজ্ঞেস করলেন, “ও সেখানে যাবে কী করে?”
মেসোমশাই বললেন, “যাওয়া কি আর যাবে না, যাবে। তবে কিনা একটু কষ্ট করে যেতে হবে। খানিকটা পথ অবশ্য যেতে হবে ওই বিন. এন. আর. লাইনের বোম্বে মেলেই।”
“কোন্ পর্যন্ত?”
“রায়পুর পর্যন্ত। বোম্বে মেল সেখানে রাত্তিরে পৌঁছবে। সেখানে …”
“গাড়ি পালটে বিষাণগড়-লাইনের ট্রেন ধরতে হবে, এই তো?” মেসোমশাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললুম, “এ আর এমন শক্ত কী। আমার সঙ্গে তো আর রাজ্যের লটবহরও থাকছে না। একটা সুটকেশ, একটা শুজনি আর একটা বালিশ, বাস্। যত রাত্তিরই হোক, লাইন পালটে করেসপন্ডিং ট্রেনে ঠিকই উঠে পড়তে পারব।”
হাঁ করে আমার কথাগুলি শুনে গেলেন মেসোমশাই। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বুঝলেন সেজদি, আজকালকার ছেলেছোকরাদের নিয়ে এই হয়েছে ফ্যাসাদ, এরা ভাল করে অন্যের কথাটা পর্যন্ত শুনতে চায় না।” তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝাঁঝালো গলায়, “আরে, করেসপন্ডিং ট্রেনে যে উঠবে, বিষাণগড়ের সেই ট্রেনটা তুমি ওখানে পাচ্ছ কোথায়?”
“তার মানে?”
“মানে আর কী, রাতটা তোমাকে রায়পুর ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমেই কাটাতে হবে। তা কোন্ ক্লাসে যাচ্ছ? থার্ড ক্লাসেই তো?”
“অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে বলেছে যে, ইন্টার ক্লাসের ভাড়া দেবে। তা হলে আর থার্ড ক্লাসে যাব কেন?”
“ঠিক আছে, টাকা যখন বাঁচাতে চাও না, তখন ইন্টারেই যাও। সেটাই অনেস্ট কাজ। কিন্তু ইন্টারের ওয়েটিং রুমও তো বিশেষ সুবিধের হবে না, বাবাজীবন। তাই একটা মতলব ঠাউরেছি। উপেন একটা চিঠি লিখে দেবে অখন, সেটা সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। সে তো ওই রায়পুর ইস্টিশানেই পুরো পাঁচটা বছর কাটিয়ে এসেছে, সেখানকার রেলের লোকেরা সবাই তাকে চেনে। রায়পুরের মাস্টারমশাইকে যদি চিঠিখানা দেখাও, তা হলে তিনি ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে দেবেন। সাহেব-সুবো প্যাসেঞ্জার থাকলে অবিশ্যি ঝঞ্ঝাট বাধে, তবে থাকবে বলে মনে হয় না। নিশ্চিন্তে ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিতে পারবে।”
“তারপর?”
“তারপর সকালবেলায় মুখহাত ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে বাসে উঠতে হবে। বাস ছাড়বে ইস্টিশনের বাইরে থেকেই। যাবে ভিরিন্ডি পর্যন্ত। মাইল পঞ্চাশেক পথ। পৌঁছতে পৌঁছতে বারোটা। দুপুরের খাওয়াটা চটপট সেখানেই খেয়ে নিয়ো।
“তা না হয় নিলুম, কিন্তু ভিরিন্ডি পর্যন্ত যাব কেন?”
মেসোমশাই বললেন, “না গিয়ে উপায় কী, বিষাণগড় লাইট রেলওয়ের ট্রেন তো ওই ভিরিন্ডি থেকেই ছাড়ে। ওখান থেকে বিষাণগড় যে খুব দূরপাল্লার পথ, তা নয়। তবে লাইট রেলওয়ের ব্যাপার তো, আমাদের এই হাওড়া-আমতা লাইনের গাড়ির মতোই নাকি ঢিকুস-টিকুস করে চলে। উপেন অন্তত সেই কথাই বলল। বিষাণগড়ে পৌঁছতে পৌঁছতে তোমার তা প্রায় পাঁচ-ছ ঘণ্টা লেগে যাবে। পথে কোনও খাবার তো দূরের কথা এক কাপ চা পর্যন্ত পাবে না।”
অবাক হয়ে মা বললেন, “সে কী, চা পর্যন্ত পাওয়া যাবে না, সে আবার কেমন কথা?”
“কী করে পাওয়া যাবে,” মেসোমশাই বললেন, “ভিরিন্ডি থেকে বিষাণগড়, গোটা পথটাই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। উপেনের কাছে শুনলুম, এটা একেবারে ষোলো-আনা ট্রাইবালদের এলাকা। আদিবাসীরা থাকে, আর থাকে বাঘ-ভাল্লুক।”
“ওরে বাবা, সেখানে গিয়ে চাকরি করতে হবে?”
বললুম, “উপায় কী, চাকরির বাজার যেভাবে গুটিয়ে আসছে, তাতে না-যাওয়াটা খুব বোকামির ব্যাপার হবে।”
“তাই বলে ওই জঙ্গুলে জায়গায় যাবি? বলি চাকরি বড়, না মানুষের প্রাণটা বড়?”
মেসোমশাই বললেন, “যেতে দেবেন না সেজদি, যেতে দেবেন না। আরে, গত বছর আমাকে মোগলসরাইয়ে বদলি বরেছিল, তাও পর্যন্ত গেলুম না, পাড়ার এর ছোকরা ডাক্তারকে দিয়ে একটা ফল্স সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে তারপর বড়সাহেবকে সেইটে দেখিয়ে বদলিটা রদ করিয়ে ছাড়লুম, আর এ কিনা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ায় যাবার জন্যে নাচছে!”
আমি তো হতভম্ব। এই মানুষটিই আজ দুপুরবেলায় কিনা বাঙালির ঘরকুনো বদনামটা ঘোচাতে বলছিলেন!
বাবা অসুস্থ মানুষ। এতক্ষণ তিনি একটা কথাও বলেননি। চুপচাপ মা আর মেসোমশাইয়ের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এবারে বললেন, “তোমরা এত বাধা দিচ্ছ কেন? যেতে যখন চাইছে, যাক না। যদি ভাল না লাগে, ফিরে আসবে।”
এর পরে আর কথা বিশেষ এগোল না। চা-জলখাবার খেয়ে মেসোমশাই উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, “দাদা এক হিসেবে ঠিক কথাই বলেছেন। জায়গাটা যদি পছন্দ না হয় তো ফিরে এলেই হল। কেউ তো আর ওকে শেকল দিয়ে সেখানে বেঁধে রাখছে না।”
তাও যে রাখতে পারে, অন্তত তার চেষ্টা যে একটা হতে পারে, তখন কি আর তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলুম? পারলে আমি বিষাণগড়ের পথে পা বাড়াতুম না।
বাবার অনুমতি মিলেছে, এই আনন্দেই তখন আমি মশগুল। নিয়োগপত্রে বলা হয়েছে, আমাকে বিষাণগড়ে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হবে ‘বাই দ্য ফিফ্টিথ অভ ফেব্রুয়ারি’। যেখানে কাজ করছি, সেখানে এক-মাসের নোটিস দিলে ভাল হত। কিন্তু যারা মাইনেই দিতে পারছে না, তারা কি আর নোটিসের জন্যে ঝুলোঝুলি করবে। কে জানে, এই যে আমি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিচ্ছি, তাতেই হয়তো তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাববে যে, যাক, ঘাড় থেকে অন্তত একটা বোঝা নামল। কিছু কেনাকাটা অবশ্য করা দরকার। কিন্তু তার জন্যে একটা দিনই যথেষ্ট। জামাকাপড় কাচিয়ে নিতে বড়জোর আর তিনটে দিন। ভেবে দেখলুম, ইচ্ছে করলে দশ তারিখেই আমি নতুন কাজে জয়েন করতে পারি। কিন্তু তাতে আবার না আমার তরফে বড্ড-বেশি গরজ প্রকাশ পায়। ঠিক আছে, যে ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে, তার একদিন আগে, চোদ্দ তারিখে, আমি বিষাণগড়ে পৌঁছব।
জি.পি.ও. থেকে পরদিনই সেই মর্মে একটা টেলিগ্রাম ছেড়ে দিলুম।
.
রায়পুরে গাড়ি থামল রাত আটটায়। গাড়ি এখানে অনেকক্ষণ থেমে থাকে। কেননা, এই স্টেশন থেকেই কামরায়-কামরায় রাতের খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। ইন্টার ক্লাস কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখলুম, উর্দি-পরা তকমা-আঁটা খানসামারা বম্বে মেলের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।
মেসোমশাইয়ের সেই ভাই ঠিকই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। চিঠিখানা যে সঙ্গে করে আনিনি, তাও নয়। কিন্তু আমি ইন্টার ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, ফার্স্ট ক্লাসের সুবিধে নিতে সংকোচ হচ্ছিল। তা ছাড়া ইন্টার ক্লাসের ওয়েটিং রুমে উঁকি মেরে দেখলুম যে, সেখানেও বিশেষ ভিড়ভাট্টা নেই, অন্তত এক কোণে একটা বেতের আর্মচেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। তার উপরে শুজনি বিছিয়ে শুয়ে পড়া গেল। চামড়ার সুটকেসটা রেখেছিলুম পায়ের কাছে। যাতে তার উপরে পা রেখে শোয়া যায়। তাতে একদিকে যেমন আরাম করে শোয়া গেল, অন্যদিকে তেমন নিশ্চিন্ত রইলুম যে, সুটকেসটা চুরি যাবে না।
সারাটা দিন টুকটাক খাবার নেহাত কম খাইনি। স্টেশনে-স্টেশনে চাও সম্ভবত একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেই কারণেই খিদে বিশেষ ছিল না। সঙ্গে একটা ম্যাগাজিন ছিল, সেটার উপর চোখ বুলোতে বুলোতেই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।
ঘুম ভাঙল ভোর ছ’টায়। আগের রাত্তিরেই খবর নিয়ে জেনেছিলুম যে, আটটা নাগাদ স্টেশন চত্বরের বাইরে থেকে ভিরিন্ডির বাস ছাড়বে। ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা-শহরে শীত বিশেষ থাকে না, সকালে সন্ধ্যায় আর রাত্তিরে তেমন গরম বোধ না হলেও দুপুরের দিকে বাতাস মোটামুটি তেতে উঠতে আরম্ভ করে। এখানে কিন্তু ফেব্রুয়ারিতেও দেখলুম বেজায় শীত। তারই মধ্যে জমাদার ডেকে, তাকে আস্ত একটা সিকি বখশিস করে ওয়েটিং রুমের বাথরুমটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে, শুধু মুখেচোখে জল দেওয়া আর দাড়ি কামানো নয়, স্নানটাও চুকিয়ে ফেলা গেল।
স্টেশন-চত্বরের বাইরেই চায়ের দোকান। পরপর কয়েকটা চালাঘর। তারই একটার সামনের বেঞ্চিতে বসে এক প্লেট পুরি-তরকারি আর দু’ খুরি চা খেয়ে যখন ভিরিন্ডির বাসে উঠলুম, ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা।
বাস ঠিক আটটাতেই ছাড়ল। রায়পুর খুব বড় শহর নয়, শহরের চৌহদ্দি ছাড়াতেও তাই খুব সময় লাগল না। তারপরেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু মিলিটারি ট্রাকের আনাগোনা তখনও খুব কমেনি। দু’চারটে তাঁবু আর কাঁটাতারের বেড়াও মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছিল। সৈন্যদের একটা মস্ত ছাউনি যে এখানে ছিল, সেটা জানতুম। মনে হল, ধীরে-ধীরে সেটা গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিস্তর শালগাছও যে পথের দু’দিকে দেখতে পাচ্ছিলুম না, তা নয়, তবে যাকে জঙ্গল বলে, ভিরিন্ডি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সেটা বিশেষ দেখিনি।
বারোটায় পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু বাসও চলছিল ঢিকুস-টিকুস করে। তাই ভিরিন্ডিতে পৌঁছতে-পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। এখান থেকে লাইট রেলওয়ের ট্রেন ছাড়বে দেড়টায়। হাতে পুরো এক ঘণ্টা সময়। টিকিট কেটে স্টেশনের বাইরের একটা খাপড়ার চালের ঘরের সামনে তাই বসে পড়া গেল। সেটাই এখানকার একমাত্র হোটেল। দুপুরের খাওয়া সেখানেই সেরে নিলুম। খাওয়া মানে মোটা চালের ভাত, সেইসঙ্গে দুখানা বাজরার রুটি, দু’হাতা ডাল আর কুঁদরির একটা ছেঁচকি-জাতীয় জিনিস। পাশের চায়ের দোকান থেকে চা’ও নিয়ে নিলুম ফ্লাস্ক ভর্তি করে। শুনেছিলুম, এখান থেকে বিষাণগড় পর্যন্ত পথে আর কিছু পাওয়া পাবে না। তা ফ্লাস্ক-ভর্তি চা যখন রইল, তখন আর অন্য-কিছুর দরকারই বা কী। মোটামুটি ফাঁকা একটা কামরায় উঠে জানলার ধারে বসে পড়লুম।
ঘণ্টা পড়ল। গার্ডসাহেব সবুজ পতাকা দেখাতে লাগলেন। হুইসল দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে, খেলনা-রেলগাড়ি তার যাত্রা শুরু করল। আর তার খানিক বাদেই শুরু হয়ে গেল জঙ্গলের রাজত্ব।