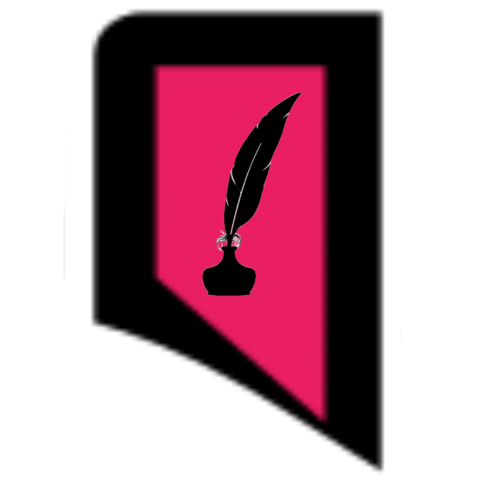মউলির রাত (ঋজুদা) – বুদ্ধদেব গুহ
তিনকড়ি
পর পর পাঁচ ভাই মারা যাওয়ার পর যখন কড়িদা জন্মাল, তখন কড়িদার মা তাঁর নাম রাখলেন তিনকড়ি। ঠিক যে নাম রাখলেন তা নয়, তিন কড়ি দিয়ে কড়িদার কাকিমা কিনে নিলেন তাকে তার মার কাছ থেকে।
সকলের ভয় ছিল যে, কড়িদাও বুঝি বাঁচবে না। কিন্তু কড়িদা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।
কড়িদাকে আমি প্রথম দেখি যখন আমি কলেজে ঢুকেছি তখন। আমার পিসীমার বাড়ি ছিল আসামের ধুবড়ি শহর থেকে কচুগাঁওয়ের দিকে যাবার রাস্তায় তামাহাট বলে ছোট একটা গঞ্জে। কড়িদারা থাকত তামাহাটের আগে কুমারগঞ্জ বলে আরেকটা গ্রামে।
কড়িদা যখন ছোট তখনই কড়িদার বাবা মারা যান। বিধবা মা তাঁর অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সিন্দুকের যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে কড়িদাকে মানুষ করেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের ছেলেকে নিজের ছেলে মনে করার মতো সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর অন্য পাঁচ ছেলের মতোই কড়িদাও পালিয়ে যায়।
পিসীমা ও পিসেমশাই কড়িদাকে নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে একইরকম করে বড় করতে থাকেন। এখানে ওখানে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত কড়িদা আমার অন্য দুই প্রায়-সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাই কলকাতায় থাকতাম বলে তাদের কারও সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হত না।
কলেজের গরমের ছুটিতে ধুবড়ি গেলাম। রাত কাটালাম কড়িদার কাকা পূর্ণকাকার বাড়িতে। আজকে আমার পিসেমশাই বা পূর্ণকাকা কেউ আর বেঁচে নেই।
বাড়িতে বিজলীর আলো ছিল না। পাখাও ছিল না। সে রাতে বড় ভ্যাপসা গুমোট গরম ছিল। ব্রহ্মপুত্রর দিক থেকে হাওয়াও আসছিল না একটুও। এদিকে প্রচণ্ড মশা। বাধ্য হয়ে মশারি টানিয়ে শুতে হয়েছিল। কড়িদার খুড়তুতো দিদি ভারতীদি যত্ন করে মশারি টানিয়ে দিয়ে গেছিলেন। কড়িদা আর আমি পাশাপাশি খাটে শুয়েছিলাম। আমাকে জানলার পাশের খাটে যেখানে হাওয়া লাগার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে শুতে দিয়েছিল কড়িদা।
আমি আজন্ম কলকাতায় মানুষ, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় অভ্যস্ত; সাহেবী কলেজে পড়ি, সমস্ত মিলিয়ে সেই পাখাহীন ঘরে, মশারির দুর্গের মধ্যে বন্দী হয়ে একজন গ্রাম্য ছেলের পাশে শুয়ে, যাকে আমি সেদিনই প্রথম দেখলাম বলতে গেলে, আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। কড়িদার সঙ্গে গল্প যে কী করব তার বিষয়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কলকাতার সেই-আমির সঙ্গে ছোট-ছোট অনগ্রসর জায়গায় স্কুলের হস্টেলে-মানুষ গেঁয়ো ছেলেটির সঙ্গে ভাব হচ্ছিল না।
কড়িদা তখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে দু-একটা কথা বলেছিল মাত্র। তবে সেই মুখের দিকে প্রথমবার চেয়েই আমার মনে হয়েছিল যে, এমন নিষ্পাপ, স্বর্গীয় মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।
রাত গম্ভীর হচ্ছিল। মশারির মধ্য গরম এবং বাইরে মশার পিপিনানি বেড়েই চলছিল। ঘরের পাশে একটা কী-যেন ফুলের ঝোঁপ ছিল। সেই ঝোঁপ থেকে ঝিম-ধরা গরমের মতো একটা ঝিম-ধরা গন্ধের ঝাঁজ উঠছিল।
আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিন্তু কড়িদার যে কেন ঘুম আসছিল না, তা বুঝতে পারছিলাম না। এটাই তার ঘর, এই ঘরেই সে রোজ শোয়, বৈদ্যুতিক পাখাতে সে অভ্যস্তও নয়। তাহলে?
ছটফট করতে করতে বোধহয় চোখ জুড়ে এসেছিল এক সময়। চোখ জুড়ে আসার পরই বেশ একটা হালকা হাওয়া আসতে লাগল মাথার দিক থেকে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভাবলাম, বোধহয় নদীর দিক থেকে হাওয়া দিল।
পাশের বাড়ির কতগুলো রাজহাঁসের প্যাকপ্যাঁক আওয়াজে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখি কড়িদা খাটের মাথার দিকে একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায় ভঙ্গিমায় তার শরীরটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে হাত-পাখাটা মাটিতে পড়ে আছে।
কড়িদা কখন ঘুমিয়েছে জানি না; হয়তো বা সারারাত আমাকে হাওয়া করে এই একটু আগেই। মশার কামড়ে হাত দুটো লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে গেছে। কিন্তু মুখে সেই অম্লান অনুযোগহীন অভিযোগহীন হাসি।
এই কড়িদা!
যাকে সে জানে না ভাল করে, চেনে না, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই, বন্ধুত্ব নেই, যার সঙ্গে নেই কোনও দেনা-পাওনার সম্পর্ক, সেই কলকাতার ছেলেটাকে নিজে সারারাত মশার কামড় খেয়ে হাতপাখা চালিয়ে ঘুম পাড়ানোর অযাচিত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ভার একমাত্র কড়িদাই নিতে পারত।
সকলের প্রতিই ঠিক একই রকম ব্যবহার ছিল তার। তামাহাটে পৌঁছে খুব মজা করতাম আমরা। পূর্ণকাকার দোনলা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতাম।
সাত-বোশেখীর মেলা বসেছিল রাঙামাটি পাহাড়ে। টুঙ-বাগানের ছায়া-শীতল ভয়-ভয় সাপ-সাপ বাঘ-বাঘ গন্ধভরা বুনো পথ মাড়িয়ে রাঙামাটি-পর্বতজুয়ারের জঙ্গল। ম্যাচ-সর্দারদের বাসা সেখানে। সারা দুপুর নিকোনো দাওয়ায় বসে তেল-চুকচুক সটান চুলে কাঠের কাঁকই খুঁজে, তাঁত বোনে সেখানে ম্যাচ-মেয়েরা। আর হলুদ-লাল কাঁঠাল পাতা ঝরে পাহাড়ী হাওয়ায় টুপ-টাপ, খুস্স্-খাস্ করে। সেখানে নিয়ে গেল কড়িদা আমায়। ম্যাচ-সর্দার লম্বা বিড়ি মুখে দিয়ে বাইরে এসে দা দিয়ে একটা কাঠ কেটে কেটে কী যেন বানাচ্ছিল।
কড়িদা বলল, আছে কেমন?
বুড়ো সর্দার ঘোলাটে চোখ তুলে বলল, ভাল আছি।
কড়িদা হাসল; বলল, তুমি তো ভাল থাকবেই। সে আছে কেমন?
সর্দার এবার অবাক হল।
বড় বড় বিস্মিত চোখ তুলে, নিজের বাতে-ধরা শরীরটাকে কোনওক্রমে ওঠাল, হাড়ে হাড়ে কটাকট শব্দ তুলে, তারপর দাওয়ার এক কোনায় একটা বাঁশের চালায় নিয়ে গেল আমাদের।
দেখি, একটা বাদামী রঙা ভুটিয়া কুকুর খড়ের উপর শুয়ে আছে। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি দগদগে ঘা। কী-সব পাতা-টাতা বেটে লাগানো আছে। তাতে। ঘরময় ঘিনঘিন করে মাছি উড়ছে।
কড়িদা বিড়বিড় করে বলল, নাঃ, অবস্থা ভাল নয়। ধুবড়ি গিয়ে ওষুধ আনতে হবে।
আমি শুধোলাম, কী হয়েছিল?
কড়িদা বলল, সাতদিন আগে ওকে একটা ছোট চিতা কামড়ে দিয়েছিল।
তুমি জানলে কী করে?
এই সর্দার হাটে এসেছিল পরশুদিন, ওর মুখে শুনেছিলাম।
কুকুরটা বুঝি তোমার খুব প্রিয়?
কড়িদা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী যেন ভাবল অল্পক্ষণ।
তারপর হেসে বলল, হ্যাঁ! খুব প্রিয়।
কী নাম কুকুরটার?
কড়িদা বলল, জানি না তো।
সর্দার বলল, ডালু।
তারপর সর্দারই বলল, দিন দশ হল আমার বেয়াই কচুগাঁও থেকে আমার জন্যে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।
আমি আরও অবাক হলাম সে-কথা শুনে।
কড়িদা বলল, কুকুরটাকে আগে দেখিনি। তবে বেচারীকে চিতাবাঘে কামড়েছে শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া বুড়োর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, কুকুরটাকে বুড়ো বড় ভালবেসে ফেলেছে। আর বুড়োর খুব ভাল লাগবে যদি আমি আসি, তাই তোমাকে নিয়ে চলে এলাম।
আমি বললাম, এই জন্যে সাইকেলে ও হেঁটে বারো মাইল এলে তুমি? মিছিমিছি? বুড়ো কি তোমাকে পাটের ব্যবসায় সাহায্য করে?
কড়িদা আবার অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আমার দিকে। বলল, না তো! বুড়োর সঙ্গে হাটে দেখা হয় মাঝে মাঝে।
কড়িদা পকেট থেকে পটাশ-পারমাঙানেটের লাল লাল কুচি বের করল, কাগজে মোড়া। বুড়োকে বলল, গরম জলে এই ওষুধ একটু গুলে ঘা-টাকে ভাল করে ধোবে বারবার। কাল আমি আবার আসব ওষুধ নিয়ে।
পর্বতজুয়ার থেকে অনেকখানি হেঁটে এসে তারপর সাইকেলে ফিরছিলাম আমরা। মাইল তিনেক রাস্তা চষা-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হয়। পেছনের হাড়গোড় প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।
রেগেমেগে কড়িদাকে বললাম, কোনও মানে হয়? একজন প্রায় অচেনা-অজানা লোকের জন্যে আর তার একটা সাধারণ কুকুরের জন্যে এই হয়রানির?
কড়িদা হাসল। সাইকেল চালাতে চালাতে বলল, একটু জিরিয়ে নাও। এসো, ওই বড় গাছটার নীচে বসি একটুক্ষণ।
সাইকেল দুটো গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা মুখোমুখি বসলাম। পশ্চিমের আকাশে সবে সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ভারী একটা শান্তির পরিবেশ চারিদিকে। সন্ধে হবার ঠিক আগে নিরিবিলি জায়গায় থাকলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে ওঠে।
কড়িদা বলল, তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি ম্যাচ-সর্দার যখন হাসল, তখন তার মুখটা কেমন দেখাচ্ছিল। তুমি কি কুকুরটার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে? তাকাওনি তো? তোমার দোষ নেই। কেউই তাকায় না। কিন্তু তাকালে বুঝতে পারতে, কুকুরটাও কত খুশি হয়েছিল আমাদের দেখে।
তারপর আবার ও হাসতে হাসতে হঠাৎ বলল, জানি, তোমার খুব কষ্ট হল। ঠিক আছে। কাল আমি একাই আসব। ওষুধ আনতে হবে সকালে গিয়ে। ঘায়ের অবস্থা ভাল না কুকুরটার।
আমি বিরক্ত গলায় বললাম, কলকাতার পথে-ঘাটে এমন কত কুকুর তো রোজ মরে। বড়লোকদের শৌখিন কুকুর ছাড়া কুকুরের চিকিৎসার কথা তো কখনও শুনিনি। কুকুরটা মরে গেলে তোমার কী যাবে-আসবে?
কড়িদার মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল। তার পরেই আবার সেই আশ্চর্য, উদার অনাবিল হাসিতে ভরে গেল। ডান হাতে এক মুঠো দুর্বাঘাস ছিঁড়ে বলল, দ্যাখো, কেউ মরে গেলে কারও কিছু এসে যায় না। আমাদের মতো সাধারণ লোক, কুকুর-মুকুর এইসব। কিন্তু…
কিন্তু…বলেই কড়িদা থেমে গেল।
আর কিছুই বলল না।
পরে বলল, তোমার মতো ভাষা আমার নেই, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু অন্য কাউকে খুশি দেখলে, সুখী দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। কী যে ভাল লাগে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে যেই-ই হোক না কেন। আর, কাউকে দুঃখী দেখলে আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়।
আমি গেঁয়ো মানুষ; আমি অমনিই। আমাকে কেউ বোঝে না।
এরপর কড়িদা কর্মজীবনে কলকাতায় এসেছিল। আমার চেয়ে বয়সে দু বছরের মাত্র বড় ছিল। সেই গেঁয়ো নোকটা শহরে এসেও একটুও বদলাল না। কলকাতার কেজো জগতের সমস্ত স্বার্থপর লোকই তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল। যার যা অসুবিধা, ডাকো কড়িকে। ডাক না-পাঠালেই বা কী, অসুবিধার কথা জানতে পারলেই হল, কড়িদা ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছত। নিজের কাজকর্ম করে এবং রীতিমত ক্লান্ত থাকার পরেও যে কড়িদা কী করে এত লোকের জন্যে এত কিছু করত তা ভাবতেও অবাক লাগে।
কেউ যদি কখনও কড়িদার ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত, তাহলে তার যে কী আনন্দ হত তা তার মুখের হাসি যে না দেখেছে, সে বুঝবে না।
কড়িদা বলত, বুঝলে, আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক, আমাদের উপর কোনও দায়-টায় নেই, কোনও বড় কাজ আমাদের দ্বারা হবে না, আমরা মরে গেলে কারও কিছু যাবে-আসবে না, ময়দানে স্ট্যাচু বানাবে না কেউ, এই রকম হেসে-খেলে বেঁচে থাকলেই খুশি।
হেসে-খেলেই থাকত কড়িদা। নিজের যে কোনওরকম অসুবিধে ছিল, দুঃখ ছিল মানসিক, কষ্ট ছিল শারীরিক, তা কেউ কখনও জানতে পারেনি। সমস্তক্ষণ সে অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্যেই এমন ব্যস্ত থাকত যে, নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি কখনও। অন্যের জন্যে, অন্যের কারণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ সে পেয়েছিল, আর সেই সুখেই ঝুঁদ হয়ে থাকত।
শুনলাম, কড়িদার পেটে নাকি ব্যথা হয়। শরীরে কী সব গোলমাল। চেহারা ও হাসি দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না কারও।
হঠাৎ শুনলাম, কড়িদা হাসপাতালে ভর্তি হবে। কী সব পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে–সিস্টোগ্রাফ-বায়োপসি ইত্যাদি বায়োপসি করে ধরা পড়ল ক্যান্সার।
যেদিন অপারেশন, তার আগের দিন নার্সিং হোমে তাকে দেখতে গেলাম।
আমি যেতেই কড়িদা উঠে বসল, জমিয়ে গল্প জুড়ে দিল, যেন ওটাও তার বাড়ির বৈঠকখানা। চমৎকার দেখাচ্ছিল কড়িদাকে। ধুতি আর পাতলা লংক্লথের পাঞ্জাবিতে।
আমি যখন উঠলাম, বলল, শরীরের যত্ন নিও, তুমি বড় বেশি খাটো, অত্যাচার করো বড়।
পরদিন অপারেশন হল। আর জ্ঞান ফিরল না। কড়িদা হাসতে হাসতেই বলতে গেলে, অত বড় দুরারোগ্য রোগটাকে হারিয়ে দিয়ে, আমাদের মতো যাটো মাপের সব মানুষদের মাথা ছাড়িয়ে তার যেখানে জায়গা সেখানে চলে গেল!
প্রায়ই মনে পড়ে, এবং চিরদিন পড়বে যে, কড়িদা একদিন সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রেখে বলেছিল, কেউ মরে গেলে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু…
আজ আমি জানি, তুমি সেদিন ঠিক বলোনি কড়িদা। কেউ কেউ মরে গেলে কারও কারও যায়-আসে নিশ্চয়ই, বড় বেশি যায়-আসে।
কড়িদার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমার পিসীমা বড় সস্ত দামে কড়িদাকে কিনেছিলেন। মাত্র তিনটি কড়ি দিয়ে!
কিন্তু পৃথিবীর সব কড়ি দিয়েও কি তোমার দাম দেওয়া যেত কড়িদা?