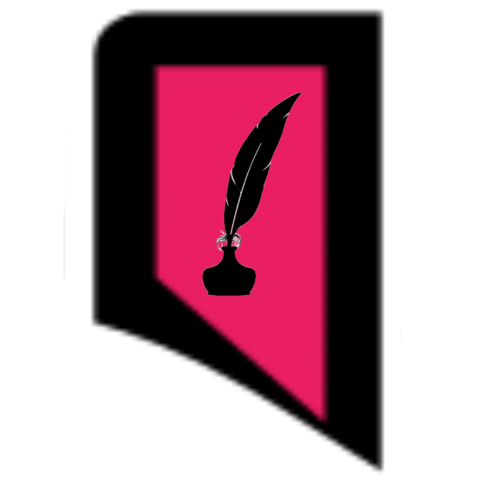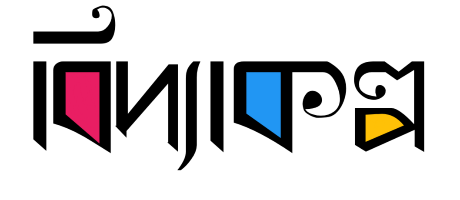ঋজুদা এবং ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে – বুদ্ধদেব গুহ
এক
ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধনের মালিকানা নিয়ে যে খুনের পর খুন হয়েছিল তারই কিনারা করে আমরা ফিরে আসার পরই এই জমায়েত, আমাদের সাকসেস সেলিব্রেট করার জন্যে। তিতির যদিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেনি স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে, কারণ সে তখন দিল্লিতে ছিল, ও এসেছিল সেই সন্ধ্যাতে ঋজুদার বাড়িতে বিশেষ অতিথি হিসেবে।
আজ রাতের মেনুতে গদাধরদার করণীয় কিছুই নেই। হাজারিবাগের আঙ্গু মহম্মদ তার বাবুর্চিসমেত হাজির। আজ মোগলাই খানা। মাটন বিরিয়ানি, মধ্যে বটি কাবাবের গোল গোল বটিকা। গুলহার কাবাব, চিকেন চাঁব, পাঁঠার তেলের চৌরি, লাব্বা, পায়া আর কবুরার চচ্চড়ি। মাটন রেজালা, সিনা ভাজা। এক এক পদ খাবার শেষ হতে না হতে হামদর্দ দাবাইয়া কোম্পানির এক এক বটি পাঁচনল। সমস্ত গুরুপাক খাদ্য নিমেষে হজম করানোর জন্যে।
বিরিয়ানির হাণ্ডি বসেছে রান্নাঘরে। উমদা বিরিয়ানি রান্না করাটাই শুধু আর্ট নয়, সেই বিরিয়ানি হাঁড়ি থেকে পরতে পরতে বের করাও, যাকে বলে হাণ্ডি নিকালনা একটি বিশেষ আর্ট।
গদাধরদার ওসব অ-হিন্দু রান্নাবান্নাতে ঘোর আপত্তি। সে রান্নাঘরের বাইরের দিকে বারান্দাতে হাওড়া স্টেশনের কুলিরা ট্রেন না-থাকলে যেমন করে কোমর, আর মাটি থেকে তোলা দু’পায়ে গামছা কষে বেঁধে বসে আরাম করে, যেমন করে বসাকে শ্রীমান ভটকাই নাম দিয়েছেন ‘পোর্টার আসন’ (যোগাসনের তালিকায় তার বতম অবদান) তেমন আসনে বসে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে দু’ঠ্যাং দোলাচ্ছে। আর গুনগুন করে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুরে গাইছে এবং তারই মাঝে মাঝে গুণ্ডি পানের লাল তরলিমা পাশের পিকদানিতে পিচকিরির রঙের মতনই ছুড়ছে।
আমরা সব ঋজুদাকে ঘিরে বসে গল্প করছি। তিতির আফসোস করছে স্যেশেলস-এর সুন্দর দ্বীপপুঞ্জে আমাদের সফল অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য উদঘাটনের সঙ্গী হতে পারেনি বলে।
ভটকাই যেন তিতিরের জ্যাঠামশাই, এমনি করে বলল, শুধু কেতাবি বিদ্যেই সব নয় জীবনে, বুঝেছ তিতির দেবী, স্কোয়ার হতে হয়, স্কোয়ার। এ স্কোয়ার পেগ ইন এ রাউন্ড হোল।
আমরা সকলেই ভটকাই-এর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম।
ভটকাই বোকার মতন বলল, কী হল? তারপর তার দু’কান লাল হয়ে গেল। সে বলল, ভুল বললাম?
আমি বললাম, নিশ্চয়ই। কোনও স্কোয়ার খোঁটা কি গোল গর্তে পোঁতা যায়? আর স্কোয়ার হওয়ার সঙ্গে স্কোয়ার পেগ-এরই বা সম্পর্ক কী?
ভটকাই বলল, সরি সরি ভুল হয়ে গেছে।
ওর ক্ষমা চাওয়ার কায়দাতে আমরা আবারও হেসে উঠলাম।
তিতির বলল, তা ছাড়া ভটকাই, ইংরেজিতে ‘এ’ বললে যাঁরা ইংরেজ, অথবা যাঁরা ইংরেজি জানেন, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। ‘এ’ হচ্ছে বাঙালি ইংরেজি, A’র উচ্চারণ সবসময়েই ‘আ’। এটা মনে রাখবে।
ভটকাই নিজের অপ্রতিভতা কাটিয়ে উঠে বলল, ও ঋজুদা! মোগলাই খানা খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এনে স্পোকেন ইংরেজির ক্লাসে ঢুকিয়ে দেবে জানলে আমি আসতামই না।
আমি বললাম, শেখার আবার স্থল-অকুস্থল কী রে! যার শেখার ইচ্ছে আছে সে চিতাতে উঠতে উঠতেও শেখে।
ঋজুদা আজ্জু মহম্মদকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সীমারিয়ার সেই ডাকাতরবিনহুড পিপ্পাল পাঁড়ের বাবা-মা কেমন আছে? তার দলের লোকেরা কি তাদের দেখাশোনা করে?
তা করে বইকি। বহত পড়ে-লিখে মানুষদের চেয়ে ওই ডাকাত-টাকাতদের মধ্যে ইনসানিয়াৎ অনেকই বেশি।
তিতির এতক্ষণে মুখ খুলল, বলল, ঋজুকাকা, এই পিপ্পাল পাঁড়ে লোকটি কে? এর কথা তো আগে শুনিনি।
এসব অনেকদিন আগের ঘটনা। যখন আমি আর আমার জঙ্গলের বন্ধু গোপাল নিয়মিত হাজারিবাগে যেতাম, তোরা হয়তো তখন জন্মাসইনি, সেই সময়কার ঘটনা।
ইসস। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কী ভালই না হত।
তিতির বলল।
আজ্জু মহম্মদ, হাজারিবাগের মহম্মদ নাজিমের বড় ছেলে, বলল, ক্যা বোল রহি হ্যাঁ বহিন? জানসে বাঁচ গ্যয়ি তুম যো পিপ্পল পাঁড়েসে নেহি ভেটিন। ইকফে হামকো মিলাথা পুরানা চাতরাকি রাস্তেমে। ইয়া আল্লা! চার পায়েরসে সাইকিল চালাকর বহুত মুশকিলসে জান বাঁচাকর পিচ রোডমে আকর পৌঁছা। আভভি ভি ইয়াদ আনেসে জি ঘাবড়াতা হ্যায়।
তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কখনও ঋজুকাকা?
তিতির শুধোল।
নেহি ভেটনেসে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকো…
তাহলে আমাদের বলো না ঋজুকাকা, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে তোমার প্রথম। দেখা হওয়ার কথা।
এমন করে বলছ তিতির যেন ঋজুদার সঙ্গে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বিয়েই হয়েছে। যেন শুভদৃষ্টি!
ভটকাই-এর ইয়ার্কিতে আমরা সকলে তো হেসে উঠলামই, আজ্জু মহম্মদও হেসে উঠল জোরে। তার মুখে জরদাপান ছিল। সুগন্ধি পানের রস ছিটকে গিয়ে লাগল ভটকাই-এর কপালে। আমরা ওর হেনস্থা দেখে আরেকবার হেসে উঠলাম।
আজ্জু মহম্মদ লজ্জা পেয়ে বলল, আমি একটু বাওয়ার্চিখানাতে যাচ্ছি। আজমল বাবুর্চি বলেছিলাম আগে ফিরনিটা বানিয়ে রাখবে, দেখি, গিয়ে কী করল!
তিনি হিন্না আতরের গন্ধ ঘরে রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেপে ধরলাম ঋজুদাকে।
পাইপটা ধরিয়ে, ঋজুদা বলল, কী যে বলব! এতে বাহাদুরির কী আছে জানি না।
আহা! বলোই না।
আমরা সমস্বরে বললাম।
ঋজুদা মিনিট দুতিন ফিল করা পাইপটাতে টান লাগিয়ে বলল, তখন তো আমরা ছাত্র। হাজারিবাগের বরহি রোডে গোপালদের ছবির মতন বাড়িতে আছি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝির কথা। হাজারিবাগ শহর থেকে যে লালমাটির পথটা চলে গেছিল গোরস্থান, বনাদাগ, গোন্দা বাঁধ, টুটিলাওয়া, সীমারিয়া হয়ে বাঘড়া মোড়, সেই পথে তখন ঝুণ্ডকে ঝুণ্ড ময়ূর দেখা যেত। তিতির বটেরের তো গোন-গুনতি ছিল না। তা ছাড়া ভাল্লুকেরও আজ্ঞা ছিল সে অঞ্চলে। কেন? তা বলতে পারব না।
ময়ূর না ন্যাশনাল বার্ড! মারা তো বারণ।
ন্যাশনাল বার্ড ডিক্লেয়ার্ড হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়াতে অথবা পঞ্চাশের দশকের শেষে। তখন মারাটা বে-আইনি ছিল না। ওই পথটা ছিল করোগেটেড টিনের মতো। প্রতি দু ইঞ্চি বাদে বাদে ঢেউ উঠেছিল পথে। সাইকেলে বা গাড়িতে সে পথে যাওয়া বিস্তর অসুবিধার ছিল। তাই আমরা আগের দিন বিকেলের বাসে বন্দুক কাঁধে করে চড়ে পড়ে, টুটিলাওয়াতে নেমে পড়ে, গোপালের বন্ধু ইজহারুল হক-এর ডেরাতে গিয়ে পৌঁছলাম। ইজহারুল নিজেও খুব শৌখিন মানুষ ছিল এবং ভাল শিকারিও। থাকত অবশ্য হাজারিবাগে কিন্তু টুটিলাওয়াতে অনেক জমিজমা ছিল। জোতদার যাকে বলে।
বাস থেকে নামতে নামতে সন্ধে। নাজিম সাহেব খিচুড়ির ইন্তেজাম করে ফেললেন। ফার্স্ট ক্লাস খিচুড়ি, সঙ্গে ইজাহারের খিদমদগারের জোগাড় করা খাঁটি ঘি, বেগুনের ভাত্তা, কাঁচালঙ্কার আর পেঁয়াজের কুচি দেওয়া, আলুরও ভাত্তা। উপাদেয়। এই সব আজমল-ফাজমল নাজিম সাহেবের ধারেকাছে আসত না বাওয়ার্চি হিসেবে, আজ নাজিম সাহেব বেঁচে থাকলে।
ভটকাই নাকটা উপরে তুলে ল্যাব্রাডর গান-ডগ-এর মতন গন্ধ শুকল বার তিনেক। তারপর স্বগতোক্তি করল, আমাদের আজমল মিঞাতেই চলবে ঋজুদা। বিরিয়ানির যা খুশবু ছেড়েছেনা! আহা। এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।
আমরা সকলেই হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে।
তিতির বলল, ভটকাই বড় ইন্টারাপট করে। বলল তো ঋজুদা।
হ্যাঁ। পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা আমাদের বন্দুক আর গুলির বেল্ট নিয়ে, মাথায় টুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিনজনে তিনদিকে। কথা হল যে, সকাল আটটাতে যেখানে টুটিলাওলা থেকে চাতরাতে যাওয়ার পুরনো পথটা বেরিয়ে গেছে, সেই মোড়ে এসে জমায়েত হব। সেখানে নিজামুদ্দিনও উপস্থিত থাকবে তার দলবল নিয়ে। শিকার করা পশু ও পাখি, যদি পাওয়া যায়, কুড়িয়ে নিয়ে আসবে বনে গিয়ে।
নাজিম সাহেব বললেন আমাকে চাতরার পুরনো পথে যেতে, কারণ সেখানে ভালুক বাবাজির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজোড়া অতিকায় ভাল্লুক নাকি সেই পথে মৌরসি-পাট্টা গেড়ে আছে। তবে বহতই খতরনাক তারা। যদিও সে পথ এখন পরিত্যক্ত কিন্তু যদি কেউ কখনও যায় কোনও কাজে, ছোটখাটো ঠিকাদার, ফরেস্ট গার্ড, জঙ্গলের কৃপকাটনেওয়ালা, তবে তাদের কারও নাক, কারও কান, কারও চোখ খুবলে নেয়, কখনও কখনও বিনা নোটিসে ‘রে রে’ করে তেড়ে এসে কুস্তিও লড়ে। যতই ‘খেলব না’ ‘খেলব না করে কেউ চেঁচাক, আদৌ শোনে না। যার সঙ্গে কুস্তি লড়ে তাদের সর্বাঙ্গ ফালা ফালা হয়ে যায়। প্রাণ থাকে না।
নাজিম সাহেব বললেন, বহত সামহালকে যাইয়েগা উঁওড়া-পুত্তানলোগ।
আরে তখন আমার যা বয়স আর যা শরীর তাতে স্বয়ং যম কুস্তি লড়তে এলেও তাকে কাবু করে দেবার হিম্মত রাখি। ভয় ব্যাপারটা শিশুকাল থেকেই আমার চরিত্রানুগ নয়। তাই বললাম, বে-ফিক্কর রহিয়ে।
নাজিম সাহেব তখন বললেন, আপকি বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলকা গ্রিনার বন্দুক হ্যায় ঔর আপকি নিশানা ভি বঁড়িয়া। ভাল্ কি লিয়ে কুছ ভি ফিক্কর নেহি। মগর ইস রাস্তাহিকি আসপাস ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আভভি ছিপা হুয়া হ্যায়।
সে আবার কে? পিপ্পাল পাঁড়ে?
ইয়া আল্লা! দশদিন হল হাজারিবাগে এসেছেন অথচ ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের নাম শোনেননি?
না তো!
আমি আকাশ থেকে পড়লাম।
আজিব বাত।
তারপরই বললেন, যোভি হো। সামহালকে রহিয়ে গা। বহতই খতরনাক হ্যায় উ ডাকু। পুলিশ কুছ নেহি কর পায়া হ্যায়। বহতই আদমিকো জান সে মার ডালা।
নাজিম মিঞার মুখে সে কথা শোনার পর আমার ভাল্লুক শিকারের শখ টিমে হয়ে গিয়ে পিপ্পাল পাঁড়ে শিকারের সাধটা চেগে উঠল।
তারপর? তিতির বলল। ছওড়া-পুত্তান মানে কী?
মানে যে ঠিক কী, তা আজও আমি জানি না। তবে নাজিম সাহেব আমাকে আর গোপালকে ওই বলে ডাকতেন আদর করে।
তখনও অন্ধকার ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। তখন হাজারিবাগ জেলার ঠাণ্ডা যে কেমন ছিল তা আজ তোরা বুঝবি না। আজ থেকে কত বছর যে আগের কথা। বনজঙ্গল ছিল নিবিড়। ভারতে তখন গিনিপিগ-এর মতন মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়নি।
ভটকাই বলল, তোমরা তখন কত বড়?
কত আর বড়। তোরা এখন যত বড় তার চেয়ে সামান্যই বড় হয়তো।
কী দুঃসাহস!
তিতির স্বগতোক্তি করল।
ভটকাই বলল, কী ওয়ান্ডারফুল বাবা-মা পেয়েছিলে ভাবো একবার। দুধের ছেলেদের একে ভাল্লুক তায় ডাকাতের মুখে ছেড়ে দিয়েও তাঁরা নির্বিকার। আমাদের আর কী হবে! রবীন্দ্রনাথ সেই বলেছিলেন না? রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী।
উলটো বললি।
আমি বললাম।
ওই হল। সোজা করে নে তাহলেই তো হল, না কি!
তারপর? বলল ঋজুদা।
এই ভটকাই, শাট-আপ।
তিতির ধমক দিল।
ইয়েস। বলল, ভটকাই, শাটিং-আপ।
আলো ফুটছে আস্তে আস্তে পুবের আকাশে। তবে তখনও কুয়াশা আছে ভারী। দিনের পাখিরা জাগছে একে একে। থ্রাশার, ব্যাবলার, কপারস্মিথ, টিয়া, টুই, মুনিয়া, মিনিটে।
বনমোরগের ডাকে চারদিক তো সরগরমই। তিতিরের টিটর-টিটর, ময়ুরের কেঁয়া-কেঁয়া, কালি তিতিরের টিউ-টিউ। তারও আগে জেগেছে, বনমোরগেরও আগে, র্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গোরা, কাঁচের বাসন ভাঙার মতন স্বর নিয়ে। সারারাত বন-পাহারা সেরে রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ টিটিটি-হুঁট-টিটিটি-হুঁট-হুঁট-হুঁট করে ডাকতে ডাকতে চলে যাচ্ছে মানুয়ানা টাঁড়ের দিকে।
যদিও খুব শীত, তবু কিছুটা চলতেই শরীর গরম হয়ে উঠল। আমার গায়ে একটি ছাই-রঙা ফ্লানেলের জার্কিন। আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু’দিকে নজর রাখতে রাখতে চলেছি কারণ এই সময়েই মাংসাশী প্রাণীরা, যেমন বাঘ, চিতা রাতের টহল সেরে নিজের নিজের ডেরায় ফেরে।
এমন সময়ে আমার থেকে বেশ কিছুটা সামনে মানুষের গলার স্বর পেলাম। তবে দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। একে আধো অন্ধকার, তায় পথটা কিছুটা সামনে গিয়েই বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। এখন বসন্তও নয়, গ্রীষ্মও নয় যে, মেয়ে ও শিশুরা মহুয়া কুড়োতে আসবে জঙ্গলে, ভোররাতে। আধো-অন্ধকারে কারওরই জঙ্গলের গভীরের এই পরিত্যক্ত, দিনমানেই নির্জন পথে আসার কথা নয়, আমাদের মতন শিকারি অথবা ডাকাত-টাকাত ছাড়া। তাই কৌতূহলী হয়ে থেমে পড়ে পথের বাঁ পাশের একটা ঝাঁকড়া আমলকী গাছের পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম, যারা কথা বলছে তাদের গলার স্বর ক্রমশই চড়ছে। তারপরই একটা আর্তচিৎকার শুনলাম এবং পরক্ষণেই ধ্বপ ধ্বপ করে মানুষের দৌড়ে আসার আওয়াজ এদিকে।
আমি তাড়াতাড়ি বন্দুকের ডানদিকের ব্যারেলে একটি বল ও বাঁদিকের ব্যারেলে একটি এল.জি. পুরে নিয়ে গাছটার আড়াল নিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম বন্দুক রেডি-পজিশনে রেখে।
পাঁচ সেকেন্ডও কাটেনি, এমন সময় একটি তীব্র আর্তচিৎকার কানে এল এবং একটি অট্টহাসি। মনে হল কেউ কাউকে জোরে লাথি মারল বা ধাক্কা দিল আর মুখে বলল, যা, যা, কামিনা, তুরন্ত ভাগ তেরা জান লেকর! আজ স্রিফ তুহর কান ঔর নাকই কাট লিয়া, ফিন কভভি বদতমিজি কিয়াতো জানহি লে লুঙ্গা।
দুটি লোক, ধুতি-পরা, গায়ে সাদা কালো দেহাতি কম্বল জড়ানো, পায়ে নাল লাগানো নাগরা জুতো, মাথাতে বাঁদুরে টুপি, তোরা যাকে ইংরেজিতে বলিস ব্যালাক্লাভা’, তাই পরে, মরি-কি-পড়ি করে দৌড়ে আসছে। তার মধ্যে একজন মাথার টুপিটা খুলে ফেলেছে আর যেখানে তার কান থাকার কথা সেখানে একটি সাংঘাতিক ভয়াবহ রক্তাক্ত ক্ষত। পেছনের জন নাকে হাত দিয়ে দৌড়ে আসছে। আর ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে তার নাক থেকে।
তাকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু সেই বাঁকের আড়াল থেকে কেউ একজন খুব জোরে জোরে হো হো করে হাসছে যেন ফুলে ফুলে আর বলছে, আজ স্রিফ তু দোনোকো কান ঔর নাকহি কাটকে ছোড় দিয়া। যা, মহল্লামে যাকর ঘর-ঘরমে দিখা। ঔর বোল যো ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েনে আজ নাক ঔর কানকি সবজি বানাকে মংগকি ডাল কি সাথ খায়েগা দোপেহরমে। যোভি হামে পাকড়ানেকি লিয়ে আয়েগা, উসলোগোঁকি হাল অ্যাইসিই হোগা।
নাক কান কাটা লোকদুটোর জামাকাপড় বেশ দামি। তারা পেছনে না-তাকিয়েপ্রাণভয়ে দৌড়ে আমি যেখানে আড়াল নিয়ে ছিলাম, তারই সামনে এসে দাঁড়াতেই তাদের হেনস্থার রকমটা পুরোপুরি জানা গেল।
ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। এ অন্যর রক্তাক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠছে আর হিক্কা তোলার মতন শব্দ করছে। আয়না তো নেই যে, নিজেদের ছিরি নিজেরা দেখবে! দেখলে, অবশ্য ওইখানেই অজ্ঞান হয়ে চিতপটাং হত।
একজন বলল, আমার বন্দুকটাও কেড়ে নিল।
নাককাটা, নাকি সুরে খোনার মতো বলল, চালানা নেই আতা তো তু শালে বন্দুক পাকড়কে আয়াথা কিউ?
ঔর তুমহারা ক্যা চাকু চালানা আতা? উওভি তো লে লিয়া!
হায়! হায়! বলে কেঁদে উঠল খোনা।
বলল, হামারা আমরিকান চাক্কুয়া। আমরিকান। হু।
লোকদুটো চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডাকু যেদিক থেকে এসে পথে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে অট্টহাসি হাসছিল সেই দিকে বন্দুক রেডি-পজিশনে ধরে এগিয়ে চললাম পথের একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে।
বলেই, ঋজুদা নামিয়ে রাখা পাইপটা তুলে নিয়ে পাইপটা ধরাল।
তুমি কি সেইদিনই ধরলে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকে?
ভটকাই প্রশ্ন করল।
ঋজুদা মাথা নাড়িয়ে জানাল, না রে না।
বলো, বলো ঋজুদা।
তিতির বলল।
ঋজুদা বলল, পুরোটাই যদি আজই শুনে ফেলিস তাহলে বিরিয়ানির হান্ডি যে কাঁদবে। এদিকে রান্না তো হয়ে গেছে। ওই দ্যাখ পেছনে চেয়ে ভগ্নদূত দাঁড়িয়ে।
আমরা একই সঙ্গে পেছনে চেয়ে দেখি গদাধরদা এসে ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়েছে। আমরা মুখ ফেরাতেই বলল, সেই মিঞায় শুদোতিচে যে হাড্ডি নিকলাবে কি না? কতার মাতা মুণ্ডু তো কিছুই বুইঝতেছি না।
ঋজুদা আমাদের দিকে নীরব ভর্ৎসনার চোখে চেয়ে গদাধরদাকে বলল, গদাধরদা, কথাটা হাড্ডি নিকলানো’ নয়, হাণ্ডি নিকালনা।
বিরক্ত গদাধরদা বলল, ওই হল্লো। মানেটাতো বইলবে।
গল্পটা এখুনি-এখুনি না শুনলে তো রেশ কেটে যাবে ঋজুদা। আমি বললাম।
আর এখুনি-এখুনি না খেলে যে বিরিয়ানিটাই মাঠে মারা যাবে।
ভেতর থেকে আজ্জু মহম্মদ বেরিয়ে এসে বলল, বিলকুল ঠিক।
ঋজুদা বলল, হবে, পরে হবে। এখন ছোট্ট করে শুনলে তো। পরে পুরোটা শোনাব।
মোচলমান তারই খাস রান্নাঘরে মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসে এক বিরাট হাণ্ডিতে বিরিয়ানি রান্না করছে, মধ্যে আবার গোল গোল ছোট ছোট বটি কাবাব মিশিয়ে দিয়েছে। কাবাব-টাবাব করতে গদাধরদা নিজেও জানে কিন্তু এই বটি কাবাবের নাম সে বাপের জম্মে শোনেনি। গুলহার কাবাবও বানিয়েছে। পার্ক সার্কাস থেকে বড়কা চর্বিওয়ালা খাসি নিয়ে এসে তার চাঁব আর রেজালাও বানিয়েছে। কিন্তু…
রান্নাঘরটাকে একেবারে নোংরা করে দিয়েছে। মনোকষ্টে গদাধরা গিয়ে একেবারে রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দার রেলিং ধরে উদাস চোখে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে থাকছে, নইলে পরক্ষণেই ভটকাই এর নাম দেওয়া ‘পোর্টার’ আসনে বারান্দাতে বসে গুণ্ডিপান খাচ্ছে নয়তো রেগেমেগে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড আবৃত্তি করছে।
যাই হোক, জম্পেশ করে কবজি ডুবিয়ে বটি কাবাব দেওয়া বিরিয়ানি, চাঁব আর রেজালা খেয়ে ওঠার পর আমরা ঋজুদাকে ধরে পড়লাম ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের গল্পটি বলবার জন্যে। আজ্জু মহম্মদও এসে বসল আমাদের সঙ্গে, নিজে খেয়ে, আজমল বাবুর্চিকে ও গদাধরদাকে খাবার পরিবেশন করে।
গদাধরদা নাকি দাড়িওয়ালা বিহারি মোচলমানের রান্না খেতে আপত্তি করছিল। ঋজুদা তাকে ডেকে বলল, দেখো গদাধরদা, আমাদের হিন্দু ধর্মের মতো মহান, গভীর ধর্ম নেই। হয়তো এমন উদার ধর্মও পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু এর এই জাতপাতের বিচার, মানুষকে মানুষ-জ্ঞান না করার শিক্ষার জন্যেই এই ধর্মের এত দুর্দশা। তুমি কি একথা জানো যে, কত নমঃশূদ্র, আর অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ তোমাদের এই ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে মুসলমান অথবা ক্রিস্টান হয়ে গেছে? মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। কে কোন দেবতা বা নিরাকারকে পুজো করে না করে তাতে কী আসে যায়? সব মানুষেরই তো একই চেহারা। তাদের সকলের খিদে-তেষ্টাও এক। তুমি আমার গদাধরা হয়ে, আমার বাড়িতে থেকে এমন ব্যবহার করে অতিথিকে অপমান করতে পারো না।
ভটকাই বলল, গদাধরদা, তুমি জানো না কি যে ‘সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই?
আমরা হেসে উঠলাম ভটকাই-এর কথা শুনে।
ঋজুদা বলল, বেচারা গদাধরদা যদি অতই জানত তবে তোর স্কুলের মাস্টারমশাই হত। আমার লোকাল গার্জেন হয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ‘ড্যাগ-মাস্টারি’ করত না।
তারপর বলল, যাও গদাধরদা, আজমল ভাইয়ের সঙ্গে বসে ভাল করে খাও। আর বিরিয়ানি আর বটি কাবাব কী করে রাঁধে, ভাল করে শিখে নাও। গুলহার কাবারটাও শিখে নিও।
আমি বললাম, রেজালা আর চাঁব কি দোষ করল?
আমি তো কিছুই জানি না রাঁধতে। বলেই, গদাধরদা চলে গেল।
তিতির বলল, ঋজুদা এবারে পাইপে তিনটে টান দিয়ে তোমার রকিং-চেয়ারে একটু চোখ বন্ধ করে দুলে নিয়ে শোনাও আমাদের ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আর তোমার এনকাউন্টারের গল্পটা।
তারপর বলল, আজ্জুবাবু বলছিলেন…
আজ্জুবাবু নয়। হয় বলবি জনাব আজ্জু মহম্মদ, নয় বলবি আজ্জু মিঞা।
তাহলে আজ্জু মিঞা বলছিলেন, ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে নাকি তোমায় শাসিয়েছিল যে তোমার আর তোমার বন্ধু গোপালকাকুর খুপরি উড়িয়ে দেবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম।
ঋজুদা একটু হেসে বলল, লোকে আমাদের সম্বন্ধে যত জানে, আমরা নিজেরাই তত জানি না। হয়তো বেচারি পিপ্পালও জানত না।
ভটকাই বলল, আরে এ তো একেবারে ‘শোলে’র গব্বর সিং। ইয়ে দুশমনি বড়া মাঙ্গা পড়েগি ঠাকুর।
মাঙ্গা নয়, ম্যাহেঙ্গা।
তিতির বলল।
ওই হল্লো। মানেতো বুঝেছ?
ঋজুদা চুপ করেই ছিল।
আজ্জু মহম্মদ বলল, হ্যাঁ বলিয়ে ঋজুবাবু। ম্যায় ভি শুন লেতে হ্যায় জারা। হামারা ভি তো কভভি শুননে কা মওকা নেহি না মিলা!
কাহে? তুমহারা আব্বা কভভি বাতায়া নেহি?
আব্বা থোরি হামলোগোঁসে বাত-চিত করতেঁ থে। আপ যব আতেথে তব তো বাঁতোকা ফোয়ারা খুল যাতা থা। হামলোগোঁনে থোরি উনকি ইয়ার থে। বাত-চিত যো হোতা থা সো আম্মাকি সাথ হি। হামলোগোঁনে থোরি শুনতা থা কিসসা?
ঋজুদা চেয়ারটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, খ্যয়ের, অব তো শুনলো ইয়ে বদমাসলোগোঁকি সাথ।
বলিয়ে ঋজুবাবু। হাম শুনলেনেসে হাজারিবাগ, টুটিলাওয়া ঔর সীমারিয়াকি বহতই আদমিকো শুনায়েঙ্গা হাজারিবাগ লওট যা কর।
বাংলা, আজ্জু মিঞা বুঝতে পারবে?
ভটকাই বলল।
হাঁ হাঁ। বিলকুল সমঝ যাবে। সমঝ তো লেতা হ্যায়, মগর বাংলা বোলি ইতনা আতি নেহি।
ঠিক্কে হ্যায়। যো লজ তুম সমঝমে না পাওগে মুঝকো বাতানা, ম্যায় তুমকো হিন্দুস্থানিমে সমঝা দেগা।
ঋজুদা বলল।
নাও এবার শুরু করো। ব্যারেল গরম করতেই করতেই বেলা গেল, তা বন্দুক ছুড়বেটা কখন?
ভটকাই বলল।
ঋজুদা বলল, তোরা ভটকাই-এর মুখে সেলোটেপ এঁটে দে। নইলে আমি কিছুই বলব না।
তিতির বলল, আজ তুমি আর একটাও কথা বলেছ তো খুব খারাপ হবে ভটকাই।
ঋজুদা বলল, আরে আঙ্গু, তুমহারা পান-সিগারেট সব মজুত তো হ্যায় না?
হিয়াকা পান ঋজুবাবু, জমতা নেহি। হাজারিবাগ যেইসা উতনা আচ্ছা মঘাই মিলতা কাঁহা! হুয়া তো পটনা সে আতা না!
ক্যা বাত করতা হায় তু আম্মু? কলকাত্তামে বাঘ কি দুধ মাঙ্গো উ ভি মিলেগা। মঘাই পান কা কেয়া কম্মি?
বলেই বলল, ভটাকাই, যাতো, মাধবকে বলে আয় জগুবাবুর বাজারে গিয়ে পণ্ডিতজির দোকান থেকে ষোলো খিলি মঘাই পান সেজে আনতে। চমন বাহার দেবে। শফ, কাথা, চুনা, আর কালি-পিলি পাত্তি জরদা।
কী জরদা?
কালি-পিলি-পাত্তি।
পয়সা দিয়ে আসব?
আরে মাধবকে তুই কি পয়সা দিবি? ওই তো আমার ক্যাশিয়ার। কলকাতার বড়লোকদের দেখে দেখে আমিও নিজে হাতে খরচ করা ছেড়ে দিয়েছি। মাধবই খরচ করে, সেই হিসেব রাখে। ক্রেডিট কার্ড রাখি সঙ্গে গোটা তিনেক অবশ্যই কিন্তু ক্যাশ রাখি না। ওটাই এখন ফ্যাশন। বিড়লা-গোয়েঙ্কা-টোডি-সরকার কেউই নিজের টাকা ছোঁয় না হাতে।
সরকার? কওনসি সরকার?
আজ্জু মহম্মদ জিজ্ঞেস করল।
বড়ে সরকার। কলকাতামে বড়ে সরকার তো একই পরিভার হ্যায়। আনন্দবাজারকি সরকার।
হাঁ?
হাঁ জনাব। ঋজুদা বলল।
আগে বাড়িয়ে। আজ্জু মহম্মদ বলল।
ভটকাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি ফিরে না আসা অবধি যদি এক পাও আগে বাড়ো তবে কিন্তু পরে তোমার নিজের পায়ের শুশ্রূষা করতে হবে।
ঋজুদা হেসে বলল, তাড়াতাড়ি আয়। তুই না-আসা অবধি আরম্ভ করব না।
প্রমিস?
প্রমিস।
বেশ কিছুক্ষণ পাইপ খেয়ে ঋজুদা বলল, হাজারিবাগে তোরা তো কেউই যাসনি।
আমি গেছিলাম।
আমি বললাম।