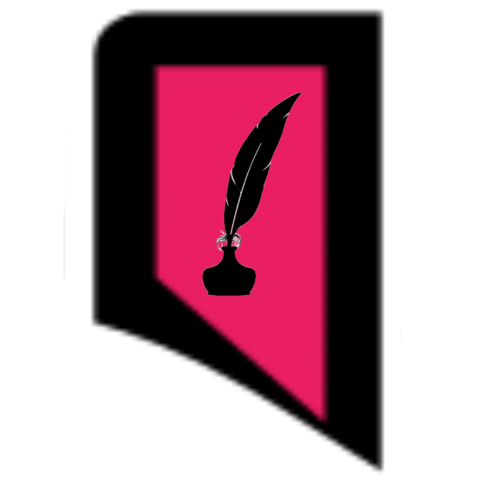নিনিকুমারীর বাঘ (ঋজুদা) – বুদ্ধদেব গুহ
দুই
এবারে মিষ্টিদিদিদের বাড়ির ভাইফোঁটার নেমন্তন্নটা মাঠেই মারা গেল। সঙ্গে ধাক্কাপাড়ে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবিটাও। ওগুলো হয়তো কলকাতায় ফিরে (যদি আদৌ ফিরতে পারি) পেলেও পেতে পারি, কিন্তু খাওয়াটা। বিশেষ করে মিষ্টিদির হাতে রান্না বড় বড় কইমাছের হর-গৌরী! একপাশে ঝাল আর অন্য পাশে মিষ্টি। ঈশ-শ-শ-শ। রিয়্যালি, গ্রেট লস্।
এখন গভীর রাত। হেমন্তের রাত। বন-বাংলোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল। অবশ্য গা ছমছম করার কারণ ছিল যে না, তা নয়। আছি যে মানুষখেকো বাঘের খাসতালুকের মধ্যেই।
বনে-পাহাড়ে হেমন্তের দিন রাতের সৌন্দর্যই আলাদা। আলাদা তার ব্যক্তিত্ব। শীতের তাপস এ আদৌ নয়। এর নেই বসন্তর চাপল্য। বর্ষার ঘনঘোর মেঘের দাড়িগোঁফের পুরুষও এ নয়, নয় গ্রীষ্মের উদাঘ রুখু রূপের কেউ। হেমন্ত ঠিক হেমন্তরই মত। এর কোনো বিকল্প নেই। হেমন্তর রাত আর হেমন্তর দিন। আহা! শিশিরের আর রাতপাখির ডানার গন্ধ। মেঠো ইঁদুরের নরম কোমল পেলব তলপেটের মত হেমন্তর বিকেল। কাছিমের পিঠের মত কালো উজ্জ্বল হেমন্তর এই স্তব্ধ শিশিরভেজা রাত। তুলনাহীন!
শেষ রাতের এক ফালি চাঁদ উঠেছে সেগুন জঙ্গলের মাথা আর কনসর নদীর পাশেই যে কুচিলাখাঁই পাহাড়, তার ঠিক মাঝখান দিয়ে দিগন্ত ঘেঁষে। অমাবস্যার পরের ঘন কালো রাতে ঐ একফালি চাঁদ তো নয়, মনে হচ্ছে যেন অর্ডার দিয়ে বানানো রুপোর একটি ছোট্ট বাঁকা তলোয়ার। বনে জঙ্গলে এসে এই কলুষহীন স্নিগ্ধ সুন্দর চাঁদকে দেখে মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় যে মানুষ চাঁদে পা না দিলেও পারতো। খুবই বোকা-বোকা ভাবনা। সন্দেহ নেই।
ভটকাই এখন ঘুমোচ্ছে। ওর বিছানাতে। একেবারে কেষ্টনগরের চূর্ণি নদীর কাদা হয়ে, কম্বল মুড়ে। একই ঘরে আমাদের দুজনের বিছানা। মধ্যে বাংলোর ডাইনিং-কাম-সিটিংরুম। আর ও পাশের ঘরে ঋজুদা শুয়েছে। যে কোন বন-বাংলোরই ঘরগুলো কেমন, মানে, ভাল কী মন্দ তা ধর্তব্যই নয়। আসল হল, বারান্দা। সারা দিন সারা রাত বারান্দাতে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। আহা! কী সব চওড়া চওড়া বারান্দা। কী সব পুরনো দিনের ইজিচেয়ার! বারান্দার সাইজ যে বাড়ির যত হোট সেই বাড়ির মানুষদের মনই ঠিক সেই সাইজের। কথাটা অবশ্য মিস্টার ভটকাই-এর। উনি মধ্যে মধ্যেই এরকম বাণী দিয়ে থাকেন।
ঋজুদার সঙ্গেও ও সমানে ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করে যাচ্ছে। ওর কথা শুনে আমি তো ভয়ে মরি। ঋজুদার সঙ্গে অমন ভাবে কথা বলার সাহস তিতিরের তো বটেই, আমারও কখনও হবে না। পূর্ব-আফ্রিকার সেই রুআহা নদীর উপত্যকাতে আমি যখন প্রায় হাতে-পায়ে ধরেই পরের বারের অভিযানে ভটকাইকে সঙ্গে আনতে রাজি করাই ঋজুদাকে, তখন কি আর জানতাম যে ও এমন ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবে? ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখাবে? কিন্তু এমন সবজান্তা ভাব করলে ওর মামাতো দাদা ঘণ্টেদার কাছে কোনক্রমে পটিয়ে-পাটিয়ে আনা জিনস্ আর নর্থ-স্টার জুতো সুদ্ধ ও নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যাবে। কোনো দেবতাই ঠেকাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে আমার অবস্থা হবে মরারও বাড়া। মাসীমাকে গিয়ে কোন্ মুখে বলব যে মাসীমা, আমা-হেন বীর এবং বিশ্ববিখ্যাত ঋজু বোস সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভটকাই নিনিকুমারীর বাঘের মেনু কার্ডে উঠে গেছে। আইটেম-এর নামটা কালকে ভটকাই নিজেই ভেবে-টেবে ঠিক করেছে। স্পেশ্যাল ফ্লেশ-ডিলাইট; কেষ্টনগর সিটি/শ্যামবাজার।
ফোক্কড় বলে ফোক্কড়।
আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেষ্টনগর সিটিই তো যথেষ্ট ছিল। আবার শ্যামবাজার কেন? ও ঠোঁটদুটো গোল করে ছোট করে ফেলে বলেছিল, মা-ন-তু! মেয়েরা আজকাল লেখে না? শ্যামলী চট্টখণ্ডী ঘোষ? অথবা নমিতা বোস বাইসন?
আমি বললাম, সে তো বিয়ে হয়ে গেলে! বাপের বাড়ি আর স্বামীর বাড়ির পদবি আলাদা আলাদা বোঝাতে। তুই কি মেয়ে? ভটকাই বলেছিল, ইডিয়ট। ব্যাপারটা হচ্ছে বাড়ির। সেটাই আসল। কেষ্টনগর সিটি ছিল বাপের বাড়ি। এখন শ্যামবাজারের মামাবাড়িই আমার নিবাস, সাকিন দাগ নম্বর, খতেন নম্বর যাই-ই বল। তবে? বাপের বাড়ির পরিচয় হাপিস করতে বলিস কোন্ আক্কেলে?
আমি আর কথা বাড়াই নি।
সকাল বেলা ঘুম ভাঙল একটা ক্রো-ফেজেন্ট পাখির জবরদস্ত ডাকে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কম্বলের পায়ের কাছে। ক্লোরোফিল ভরপুর ঘনসবুজ গাছ-গাছালির মধ্যে পড়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে সে রোদ আসছে। কী গভীর শান্তি চারদিকে। কে বিশ্বাস করবে আমরা এখানে এসেছি মৃত্যুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে! চোখ-মুখ ধুয়ে বাইরের বারান্দাতে এসেই দেখি ঋজুদা। বারান্দায় যেখানে রোদ লুটিয়ে পড়েছে, সেইখানে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়িয়ে বসে দূরের পাহাড়ের মাথায় যে দূর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে রোদে-মোড়া নীল আকাশের ফ্রেমে বাঁধানো কোনো ছবিরই মত, সেই পোড়ো-দুর্গটির দিকে চেয়ে বারান্দার থামে দুপা তুলে দিয়ে পাইপ খাচ্ছে।
মিস্টার ভটকাই বন্দুক রাইফেলগুলো নিয়ে পড়েছে। রাইফেলগুলোর নল থেকে পুল-থ্রু দিয়ে টেনে টেনে তেল পরিষ্কার করছে আর দোনলা বন্দুকগুলোর নল পরিষ্কার করছে ফ্ল্যানেল-জড়ানো ক্লিনিং-রড দিয়ে।
আমাকে দেখেই ভটকাই তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কীরে রুদ্রবাবু! আমার যোগব্যায়াম তো শেষই, মায় সর্ষের তেল গায়ে মেখে চান পর্যন্ত শেষ। আর তোর এতক্ষণে ঘুম ভাঙল? ম্যান-ইটার বাঘ মারতে এসেছিস তুই? ফুঃ!
ঋজুদা কী যেন ভাবছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, এই! তোরা সকাল থেকেই দুজনে মোরগা-লড়াই শুরু করিস না তো! যা রুদ্র। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে চান সেরে নে। আমিও যাচ্ছি আমার বাথরুমে। ঠিক আটটাতে ব্রেকফাস্ট দিতে বলেছি জগবন্ধুকে। তুই চান করতে যাবার সময় একটু তাড়া দিয়ে যাস। বালাবাবুও খাবেন আমাদের সঙ্গে। খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।
চা ঢাললাম আমি কাপে পট থেকে। ঋজুদাকে বললাম, তুমি নেবে আর?
ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, দে এক কাপ।
ঐ পাখিটার ওড়িয়া নাম জানিস? বল্ তো কী? ভটকাই ক্রো-ফেজেন্টের ডাকের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল।
সাহস কত্ত! যেন পরীক্ষা নিচ্ছে আমার! দু’দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় অন্ন। যার দৌলতে এখানে আসা তারই লেগ-পুল করছে।
জানি না। আমি তাচ্ছিল্যের গলায় বললাম। জানলেও… ।
হুঁ। হুঁ। কাটুয়া! আমি জানি।
ভটকাই চোখে-মুখে অসীম কৃতিত্ব জাগিয়ে বলল।
ঋজুদা আমাদের ঝগড়াতে কোনো পক্ষকেই সমর্থন না করে চুপ করে কী যেন ভাবছিল।
সামনের ঐ পাহাড়টার নাম যে কুচিলা-খাঁই তা তো জানিস, কিন্তু কুচিলা-খাঁই মানে কী বল তো?
অদম্য এক্স-কেষ্টনগর সিটি, অধুনা শ্যামবাজারের রাজ, কলকাতার আড্ডাবাজ ভটকাইচন্দ্র আমায় বলল।
মানেটা আমি জানি। ঋজুদার জন্যে চা ঢালতে ঢালতে বললাম আমি। তারপর বললাম, কুচিলা-খাঁই মানে, ওড়িয়াতে ধনেশ পাখি। ধনেশ পাখি দেখেছিস তো চিড়িয়াখানায়? এবারে বল তো কুচিলা শব্দটার মানে কী? উল্টে শুধোলাম আমি।
ভটকাই মনে হল মুশকিলে পড়ে গেল। মুশকিলে সে পড়তে পারে কিন্তু কোথাওই বেশিক্ষণ পড়ে থাকার পাত্রই সে নয়। কিন্তু আশ্চর্য! ভটকাই-এরও সুমতি হল। দু’দিকে মাথা নেড়ে বাধ্য ককার-স্প্যানিয়েলের মত সে জানাল, জানে না।
তারপর বলল, বলে দে আমাকে তুই।
কুচিলা একরকমের ফল। যে গাছে ঐ ফল ধরে তার নামও কুচিলা। ঐ ফল খেতে ধনেশ পাখিরা খুব ভালবাসে বলেই ধনেশ পাখিদের নাম এখানে কুচিলা খাঁই। আমি বললাম।
ভটকাই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, হাউ ডেঞ্জারাস।
এবার অবাক হবার পালা আমার। বললাম, এতে ডেঞ্জারের কি দেখলি?
ডেঞ্জার নয়? তুই কাউঠ্যা খেতে ভালবাসিস, মাসীমা কদবেল খেতে ভালবাসেন বলেই তোদের নাম হয়ে যাবে কাউঠ্যা-খাঁই আর কদবেল-খাঁই?
ঋজুদা ওর কথায় এত জোরে হেসে উঠল যে কাপ থেকে চা চকে পড়ল ভাল শালটার ওপর।
আমার আর ঋজুদার হাসি থামলে আমি বললাম, কুচিলা ব্যাপারটা কী তা জানিস?
ঋজুদার হেভি রাইফেলটার তেলমোছা শেষ করে চেয়ারের দুই হাতলের ওপর রেখে ও বলল, ব্যাপার আবার কী? কুচিলা কুচলারই খুব কাছাকাছি। কুচলা তো হিন্দি শব্দ। ময়লা-কচলা। বলে না?
কুচলা ঠিকই আছে। কিন্তু কুচিলার সঙ্গে কুচলার সম্পর্ক নেই। ওড়িয়া শব্দ এটি।
তাই?
ইয়েস স্যার! আর এই ধনেশ কিন্তু বড় ধনেশ যার ইংরিজি নাম দ্য গ্রেটার ইন্ডিয়ান হর্নবিলস্।
সে যাই হোক, কিন্তু কী বিটকেল নাম রে বাবা! কুচিলা খাঁই।
নাম বিটকেল হলে কি হয় এ বড় গুণের গাছ। এই কুচিলা।
কেন? কিসের গুণ?
এই গাছের ফল দিয়ে যে ওষুধ তৈরি হয় তা খাইয়েই তো মাসীমা তোর মত ছিঁচ-রুগীকে দু’পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ব্যামো একেবারে টাইট।
আমার ব্যামো? যেন গাছ থেকে পড়ে বলল ভটকাই।
ওষুধটা কি তা তো বলবি?
নাক্স-ভমিকা।
কী রে। বলিস কি তুই! নাক্স-ভমিকা থাট্টি?
ঋজুদা আবারও হেসে ফেলল, ভটকাই-এর কথা শুনে। বলল, নাক্স ভমিকার বুঝি থার্টি ছাড়া আর স্ট্রেংথ হয় না? কি রে ভটকাই?
ভটকাই ক্ষণকালের জন্যে অফ-গার্ড হয়ে হেসে নিজের বোকামি মেনে নিল।
ভারী সুন্দর জায়গাটা কিন্তু। চায়ের কাপে আর এক চুমুক দিয়ে আমি বললাম ঋজুদার দিকে চেয়ে।
হ্যাঁ! ভয়াবহ বলেই হয়ত বেশি সুন্দর। এবারে চল ওঠা যাক। ঠিক আটটায় খাবার টেবলে দেখা হবে।
আমরা যখন ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে জগবন্ধুর ভাজা গরম গরম লুচি, বেগুনভাজা, ওমলেট আর রেঞ্জার বেহারা সাহেবের দিয়ে যাওয়া অতি উপাদেয় পোড়-পিঠা দিয়ে প্রাতরাশ সারছি, সেই সময়ে বাইরে একটি জিপ-এর শব্দ শোনা গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হতেই সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন রঘুপতি বিশ্বল সাহেব–ডি, এফ ও.।
ঋজুদা খাওয়া থামিয়ে বলল, নমস্কার। আসন্তু আঁইজ্ঞা। বসন্তু বসন্তু।
বিশ্বল সাহেব হেসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বসিবি নিশ্চয়। কিন্তু কিচ্ছি খাইবা-পীবা পাঁই কহিবেনি আঁপ্পনি মত্বে।
কাঁই? গুট্টে কাপ চা পীইবাকু টাইম হেব্বনি কি? এত্বে তাড়া কাঁই আপনংকু? ঋজুদা বললো।
গম্ভীর মুখ করে বিশ্বল সাহেব বললেন, সে বাঘটা কালি মধ্যরাতিরে গুট্বে হিউম্যান কিল করিলা।
ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে খাওয়া থামিয়ে বলল, সত্য?
সত্য না হেল্বে মুই শুনিনি এটি দৌড়িকি এমিত্বি আসিলি কি?
আমি দেখলাম, ভটকাই-এর মুখে লুচি-বেগুন ভাজা আটকে গিয়ে ওর চোখ গোল গোল হয়ে গেল হিউম্যান কিল-এর কথা শুনে।
কুয়াড়ে করিলা? কিল?
ঋজুদা শুধোল।
বিশ্বল সাহেব চেয়ারে ঘুরে বসে ডান হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গরাদহীন জানালা দিয়ে বাইরে দেখিয়ে বললেন, পর্বতোপরি যে গড়টা দিশিছি…
হাঁ। সে গড়ুকু কোন্ পাখেরে?
সেটু যীবাব্বেলে গুট্টে সাম্ব গাঁ মিলিব সে পর্বতর নীচ্চেরে। গড়ুটু যাইবা পথকু বাম পাখেরে। তা নাম ঝিংকুপানি। আট-দশ ঘর কাবাড়ি রহিছি সেটি। সেই গাঁ টারু গুট্টে ঝিওংকু ধরি সারিলা বাঘ টা।
ঋজুদাকে চিন্তিত দেখাল। তাকে এত উত্তেজিত কখনও দেখিনি। উত্তেজিত হলেই চিন্তিত দেখাল। এ চিন্তা অন্যরকম।
আমাদের বলল, চল। তাড়াতাড়ি খেয়েনে রুদ্র, ভটকাই। বলেই নিজে নাকে মুখে খাওয়া সেরে চেয়ার ছেড়ে উঠল। জামাকাপড় পরতে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়ে বিশ্বল সাহেবের আপত্তি সত্ত্বেও জোর করেই এক টুকরো পোড়-পিঠা আর এক কাপ চা ঢেলে দিয়ে গেল তাঁকে।
একটু পরই আমরা তিনজনে তৈরি হয়ে বারান্দাতে এলাম। বনবিভাগ আমাদের যে জিপটি দিয়েছিলেন সেটি মাহিন্দ্রর জিপ। বলতে গেলে, নতুনই। বনেট খুলে ব্যাটারির জল, মবিল সব নিয়ে দেখে নিল ঋজুদা। আমি ড্রাইভিং সিটে উঠে ইগনিশন সুইচ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। পেট্রলের ট্যাঙ্ক প্রায় ভর্তিই আছে। তেলের দরকার হলে আমাদের যেতে হবে সাম্বপানিতে। এখান থেকে প্রায় চল্লিশ কিমি মত পথ। পথটা আগাগোড়াই কাঁচা। গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। নালাও পেরতে হয় তিনটে। ফেয়ার ওয়েদার রোড। সবে খুলেছে। জুন মাসের শেষে বন্ধ হয়ে যাবে। ওর চেয়ে কাছে আর কোনও পেট্রলপাম্প নেই।
ঋজুদার ইশারাতে আমি এঞ্জিন স্টার্ট করলাম। ঋজুদা বিশ্বল সাহেবকে বললেন গোটা দুই ড্রামে করে যদি পেট্রল আনিয়ে বাংলোতে রাখবার বন্দোবস্ত করেন তাহলে খুবই ভাল হয়।
বিশ্বল সাহেব বললেন, ঠিকাদারের ট্রাকে করে কালই পাঠিয়ে দেবেন পেট্রল।
ঋজুদা হাত জোড় করে বিশ্বল সাহেবকে নমস্কার করে বললেন, কালি কী পড়শ্বু আপনংকু সেঠি যাইকি ভেটিবি।
বিশ্বল সাহেবও নমস্কার করে বললেন, হঁ আইজ্ঞা।
জিপ এগিয়ে নিয়ে গেলাম আমি। বিশ্বল সাহেব নিজের জিপের দিকে যেতে যেতে বললেন, টেক কেয়ার।
আমি বললাম, কী ভাল, না?
ভটকাই শুধলো, কী?
এই বিশ্বল সাহেব।
ঋজুদা বলল, আমাদের দোষ কী জানিস? আমরা বাঙালীরা নিজেরা নিজেদের মস্ত বড় বলে মনে করি। আমাদের প্রতিবেশীদের-ওড়িয়া, অহমীয়া, বিহারী এঁদের কাউকেই ভাল করে জানারও প্রয়োজন বোধ করিনি আমরা কোনওদিন! আমি তো ওড়িশা আর ওড়িশার সংস্কৃতি, নাচ, গান, সাহিত্য সব কিছুরই দারুণ অ্যাডমায়রার। অনেক কিছুই শেখার আছে আমাদের ওঁদের কাছে। বিনয় তো অবশ্যই। আমরা ছেলেবেলায় শিখেছিলাম, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়, নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়। কিন্তু ঐ মুখস্থই করেছিলাম। জীবনে কাজে লাগাইনি।
আমি চুপ করে থেকেই সায় দিলাম ঋজুদার কথায়।
রেঞ্জার সাহেব একজন ফরেস্ট গার্ডকে আমাদের গাইড হিসেবে এবং বন-বিভাগের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সেতু হিসেবে এই বন-বাংলোতেই পোস্ট করে দিয়েছেন। উনি জিপও চালাতে জানেন। ভদ্রলোকের নাম হরেকৃষ্ণ বালা। কাল রাতেও উনি বাংলোতেই ছিলেন। জগবন্ধুরই কোয়ার্টার্সে।
ঋজুদা নিজের ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারে রাইফেলটা নিয়েছে সঙ্গে। জেফরি নাম্বার টু। আমার হাতে থ্রি-সিক্সটি-সিক্স ম্যানালিকার শুনার। সিঙ্গল ব্যারেল ম্যাগাজিন রাইফেল। ভটকাই শিকারি নয়। তবে ওর মেজমামার বন্দুক চালিয়ে বহরমপুরের বিলে-বাদায় কাগা-বগা-জলপিপি-কামপাখি যে দু-চারটে মারেনি এমন নয়। ঋজুদার ডাবল ব্যারেল বন্দুকটা ভটকাই-এর হাতে। যতটা এবারে ব্যবহার করার জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি মরাল-সাপোর্ট-এর জন্যে। বালাবাবু আর ভটকাই পেছনে বসেছিলেন। আর ঋজুদা আমার পাশে।
ঋজুদা বালাবাবুকে শুধোলেন সামনে যে দুর্গটা দেখা যাচ্ছে তার নাম কী হরেকৃষ্ণবাবু?
সে গড়টা, তার নাম শিকার-গড়।
ও। এই তাহলে সেই বিখ্যাত শিকার-গড়। অনুমান করেছিলাম অবশ্য।
শিকার-গড়-এর নাম শুনে আমরা সকলেই তাকালাম, ভাল করে সেদিকে। মানুষ আর হাতিতে পাথর বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ পাহাড়-চুড়োর গড় বানিয়েছিল। কত মানুষের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে ঐ গড়-এর পাথরে পাথরে, তা ঠাকুরানীই জানেন। আর..
এখন? এখন কারা থাকে ঐ গড়ে? কেউই থাকে না? ঋজুদা হরেকৃষ্ণবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল সামান্য অধৈর্য গলাতে।
জায়গাটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা, হয়নি ঋজুদার এখনও। বিশ্বল সাহেবের কাছে আগেই একটি ম্যাপ চেয়েছিল এই ফরেস্ট ডিভিশনের। সমস্ত গ্রাম এবং ফরেস্ট ব্লক-এর এবং বিট-এর ডিটেইলস চেয়ে। বিশেষ করে কোন কোন জায়গায় বাঘ মানুষ ধরেছে তা লাল কালিতে চিহ্ন দিয়ে। এবং কোন্ কোন্ তারিখে ধরেছে তাও। বিশ্বল সাহেবের অফিস সেই ম্যাপটা এখনও দিয়ে উঠতে পারেনি বলে ঋজুদা একটু বিরক্ত আছে মনে মনে। এই ম্যাপটা কলকাতাতেই ঋজুদার কাছে যাতে পৌঁছয় তারই অনুরোধ করেছিল ঋজুদা। আর এদিকে বাঘে মানুষ মেরেছে, সেই কিল-এর দিকে এগোচ্ছি আমরা অথচ নানারকম গল্প, কিছু প্রেসকাটিং এবং চিল-সেক্রেটারির পাঠানো একটা নোট ছাড়া অন্য কিছুই হাতে আসেনি।
ঋজুদার প্রশ্নর উত্তরে হরেকৃষ্ণবাবু বললেন, এখন ঐ গড়ে ভূত-প্রেত বাস করে। সাপ, নানারকম। একটি ভাল্লুক পরিবার। আর নিনিকুমারীর বাঘও থাকে মাঝে মাঝে। গড়-এর ভেতরের ঘরে বাদুড়দেরও বাস আছে। আগে কখনও কখনও মানুষজন আসত দূর থেকে। কোনও স্কুল কলেজের বা অফিসের ছেলেমেয়েরা বা বাবুরা পিকনিকে আসত শীতকালে। কিন্তু পরপর দুটি পিকনিক পার্টির একজন পুরুষ এবং একজন মেয়েকে বাঘে ধরার পর কেউই আর ঐ দিকই মাড়ায় না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ ওঠেনি ঐ গড়ের পথে আজ বহু বছর। পাহাড়ের ওপরে শিকার-গড়ে যাওয়ার পথটাও আর পথ নেই। জঙ্গলে আর কাঁটা ঝোপে ছেয়ে গেছে।
ঝকঝক করছে রোদ পথের পাশের সেগুন প্ল্যানটেশানে। প্ল্যানটেশান যত্ন করেই করেছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু বাঘের জন্যে তলার আগাছা পরিষ্কার করা হয়নি কম করে তিন-চার বছর। গরমের আগে দাবানলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নালাও কাটা হয়নি। ফলে পথটাকে আগাছা আর ঘাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। জিপও আজকাল আসে কালে-ভদ্রে। পায়ে-চলা পথটি আগের চওড়া পথের মধ্যে। এঁকেবেঁকে জেগে রয়েছে কোনওক্রমে। তাতে সৌন্দর্য আরও বেড়েছে বই কমেনি।
জিপটা চলেছে পাহাড়ী ঝর্ণা পেরিয়ে, হীরেকুচির মত জল ছিটিয়ে টায়ারে, লালমাটি ভিজিয়ে। প্রায় হারিয়ে-যাওয়া পথ ছুটেছে ক্রমাগত চড়াইয়ে-উতরাইয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শিকার-গড়ের দিকে।
মিনিট কুড়ি জিপ চালানোর পর একটা সমকৌণিক বাঁক ঘুরতেই নাকে এল হেমন্তর পাহাড় বনের এক ঝলক প্রভাতী গন্ধ। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও একটি ঝলক চোখে ঝিলিক মেরে গেল। তারপরই পথটা আবার বাঁক নিতেই গ্রামটা মুছে গিয়ে গন্ধটা জোরদার হল। তার একটু পরেই পথটা আবার সোজা হয়ে ঝিংকুপানি গ্রামের দিকে মুখ করল।
নামেই গ্রাম। অল্প কয়েকটি ঘর। ভেরাণ্ডার বেড়া লাগানো। পেঁপে গাছ। আম, লিচু, কাঁঠাল। গোবর লেপা উঠোন। স্নিগ্ধ ছায়া। গরু-ছাগলের ডাক। মন্থর, ঢিলে-ঢালা চাল এখানের জীবনের। উলঙ্গ শিশু, অপুষ্টির শিকার-হওয়া হাড়-লিকলিক পিলে-বের-করা সব যুবকেরা। অন্ধ বৃদ্ধ। চারিদিকে চরম দারিদ্র। আর হতাশা। অসহায় মানুষের করুণ সমর্পণ, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত; সমাজের পায়ে, সমাজ ব্যবস্থার পায়ে। নিনিকুমারীর বাঘেরও পায়ে।
ঋজুদা বলল, দ্যাখ রে, কলকাতার ভটকাই। এই হল আমাদের ভারতবর্ষের গ্রাম। এই গ্রামই আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের আয়না।
আমি বাইনাকুলারটা তুলে দুর্গটাকে ভাল করে দেখছিলাম।
এই ঝিংকুপানি গ্রাম থেকে শিকার-গড় সামান্যই দূর। তবে এই গ্রামের সমতা থেকে প্রায় তিন-চার শ ফিট উঁচুতে হবে। গড়-এর তোরণটি ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি। কোথাও কোথাও এবং বিশেষ করে তোরণের কাছে কোয়ার্জাইটও ব্যবহার করা হয়েছে। আর দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে রেড-স্টোন আছে। বোগোনভিলিয়া লতা আর জ্যাকারান্ডা গাছে পুরো এলাকাটাই জঙ্গল হয়ে আছে। গড়-এর দেওয়ালের পাশে পাশে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, অমলতাস ইত্যাদি গাছ। একটা ময়ূর হঠাৎই ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ ক্বেঁয়া ক্বেঁয়া ক্বেঁয়া করে গড়ের দিক থেকে।
ঋজুদা বলল, আমাকে দে তো একবার বাইনাকুলারটা, রুদ্র।
বুনো ময়ূরের অতর্কিত তীক্ষ্ণ ডাক শুনে ভটকাই চমকে উঠেছিল। জঙ্গলে প্রথমবার ময়ূর বা হনুমানের ডাক শুনে না চমকানোটাই আশ্চর্য!
আমি ওর পিঠে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, ময়ূর!
ভটকাই-এর মুখে তখন ঠাট্টা ছিল না। জঙ্গল, পাহাড়, এই গ্রাম, নরখাদক বাঘের জান্তব অস্তিত্ব এবং সামনের রহস্যময় নিথর হয়ে যাওয়া শিকার-গড় এই সব কিছুরই প্রভাব ভটকাই-এর ওপরে এরই মধ্যে বেশ গভীরভাবে পড়েছিল। আমি ভাবছিলাম, ঝিংকুপানি গ্রামের মানুষেরা এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে কিসের জন্যে পড়ে আছে? চাষবাসের কোনো চিহ্নই তো দেখলাম না। খড়ের চালে দু-একটা লাউ-কুমড়ো গাছ। তাকে চাষ বলে না। এখানে চাষ-বাস হলে এতদিনে সর্ষে, বিরি-ডাল, রাঙা আলু, তামাকপাতা এসব লাগানো হত। হেমন্তর সকালের রোদে উজ্জ্বল দেখাত তামাকের খেতকে।
হরেকৃষ্ণবাবুকে ঋজুদা কি আমার মনের কথাটাই শুধলো।
উনি বললেন, এরা সব কাবাড়ি। কাবাড়ি মানে কাঠুরে। ওড়িশাতেও তো অন্য অনেক রাজ্যেরই মত ফরেস্ট কর্পোরেশান হয়ে গেছে। ফরেস্ট কর্পোরেশান হবার আগে এরা সবাই ঠিকাদারদেরই কাঠ কাটত। তাদের এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে চলে যেত, ভাল ঝর্ণা দেখে, হাতি ও বাঘের চলাচলের পথ এড়িয়ে। থাকত সেখানে যতদিন না কাজ শেষ হত। কোথাও সেগুন, কোথাও শাল, কোথাও হরজাই জঙ্গল, করম, কুসুম, গেণ্ডুলি, সাজা, চার, হলুদ, জংলি আম, আরও কত কাঠ। কাঠ কেটে পাহাড়ের ওপর থেকে বা নিচ থেকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে এসে ঠিকাদারদের বানানো পথের পাশে গাদা দিয়ে রাখত। তারপর সেখান থেকে ট্রাক-এ করে ঠিকাদারেরা নিয়ে যেত সেই সব কাঠ করাতকলে, কাঠ-গোলায়। বামরা, ভুবনেশ্বর, কটক, রাইরাঙ্গপুর, বারিপদা, ঢেকানল, অঙ্গুল এবং আরও কত বিভিন্ন জায়গাতে। মহাজনেরা সেখানে থেকে নিলামে কাঠ কিনে নিয়ে আবার চালান করত কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, পাটনা, মাদ্রাজে। কোথায় না কোথায়!
জিপ থেকে আমরা নামার পরই গ্রামের ঘর ও সংলগ্ন জঙ্গল থেকে তিন-চারজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দুহাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, প্রণাম আঁইজ্ঞা। তাদের মধ্যে একজন শব্দ না করে কাঁদছিল। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। লোকটির চোখদুটো হলদেটে। দেখে মনে হয় যেন ন্যাবা হয়েছে।
হরেকৃষ্ণবাবু এগিয়ে গেলেন ওদিকে। ঐ লোকটির বউকেই কাল সন্ধের একটু আগে বাঘে নিয়ে যায়। গ্রামে কারও ঘরেই বাথরুম থাকে না। সূর্য ডোবার আগে গ্রামের সকলেই সান্ধ্যকৃত্য সারতে গ্রামের আশপাশেই আড়াল দেখে বসে। লোকটি বলছিল, হাতে ঘটি নিয়ে সে সন্ধের আগে যখন বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল তখন ঐ কাঁঠাল গাছটার নিচে, প্রায় বাড়ির উঠোন থেকেই বলতে গেলে, আমার বউকে ধরে নিয়ে গেল।
অন্য একজন বলল, কড়িবি কঁড়্ব,? সে বাঘ্বটা তো এমিত্বি বাঘ্ব না। সেট্বা হেল্বা ঠাকুরানীর বাঘ্ব।
একটু এগিয়ে গিয়ে পথের লাল ধুলো আর ঝাঁটি জঙ্গলের সবুজ পাতায় পাতায় রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ দেখাল ওরা আমাদের। যেখানে মেয়েটিকে ধরেছিল সেখানকার জমিতে ধস্তাধস্তির চিহ্ন এবং বাঘের পায়ের দাগও স্পষ্ট দেখা গেল। প্রকাণ্ড পুরুষ বাঘ। সেখান থেকে ঘাড়-কামড়ে ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে লোকটির বউকে বাঘ গড়ের দিকে। গাঁয়ের কোনও লোকই তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। কাল সন্ধের মুখে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টার কথা ছেড়েই দিলাম, সকালবেলাতেও কেউই যেদিকে বাঘ মেয়েটিকে নিয়ে গেছে সেদিকে যায়নি। শুধু তাই নয়, যায়নি বলে কারও কোনও অপরাধবোধও নেই। যেন না-যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ বউটির শরীরের যে-কোনো একটি অংশ অন্তত পাওয়া দরকার দাহ করার জন্যে। জাতে হিন্দু এরা সকলেই। হিন্দুর মৃতদেহ, অন্তত মৃতদেহের কোনও অংশও দাহ করা না গেলে তো সকার হবে না। আত্মা মুক্ত হবে না। আর মানুষখেকো বাঘের হাতে যেসব মানুষের প্রাণ যায়, অপঘাতে মৃত্যু হয়, তারা ভূত-প্রেত হয়ে যায় এমনই বিশ্বাস করে এরা।
ঋজুদার কাছে শুনেছিলাম যে ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার গভীর বন-পাহাড়ের লোকেরা বিশ্বাস করে যে মানুষখেকো বাঘের হাতে মৃত্যু হলে সেই মানুষ ‘বাঘ্বডুমবা’ বলে একরকমের ভূত হয়ে যায়। রাত-বিরেতে গাছের মগডাল থেকে তাবড় তাবড় সাহসী লোকেদেরও হার্টফেল করিয়ে কিরি-কিরি-কিরি-কিরিধূপ-ধূপ-ধূপ-ধূপ করে চেঁচিয়ে ওঠে নাকি!
এদিকে সময় নেই। তখন সাড়ে নটা বাজে ঘড়িতে। বালাবাবু আর ভটকাইকে ঋজুদা এই গ্রামেই থাকতে বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগোল। বালাবাবু গ্রামের লোকদের একজনকে আমাদের সঙ্গে যেতে বললেন। কিন্তু আশ্চর্য! কেউই রাজি হল না। একজনও নয়। এমনকি যার স্ত্রী বাঘের পেটে গেছে সেও নয়। অথচ এরা কেউই তেমন ভীতু নয়। তাই ভারী অবাক হলাম আমি। মানুষের স্নায়ু কতখানি অত্যাচারিত হলে, ভয় মানুষের মজ্জার কত গভীরে সেঁধিয়ে গেলেই যে ঐ সব অসমসাহসী মানুষেরাও এমন লজ্জাকর অবস্থাতে নিজেদের নামিয়ে আনতে পারে তা অনুমান করা যায়।
ঋজুদা মাথার টুপিটা চেপে বসিয়ে নিল। তারপর অলিভ-গ্রীন বুশশার্টের সাইড পকেট থেকে বের করে দুটো ঝকঝকে সক্ট-নোজড বুলেট ভরে নিজের রাইফেলটা লোড করে নিয়ে আমাকে বলল, ব্যারেলে একটা আর দুটো ম্যাগাজিনে রাখ গুলি। মিছিমিছি সব গুলি ম্যাগাজিনে ভর্তি করে রাইফেলটাকে ভারী করিস না। তারপর এগোবার ঠিক আগে একবার হাতঘড়ি দেখে বালাবাবুকে বলল যে তোমরা একটা অবধি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। হরেকৃষ্ণ, তোমাকে আমি তুমিই বলছি। আশা করি মনে কিছু করবে না।
বালাবাবু বললেন, না, না, খুশিই হব স্যর।
একটার মধ্যে আমরা না ফিরলে বা আমাদের গুলির আওয়াজ না শুনলে তোমরা বাংলোয় ফিরে যাবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে আমাদের দুজনের জন্যে কিছু খাবার ও জলের দুটো বোতল নিয়ে এখানেই ফিরে এসে আবার অপেক্ষা করবে। যদি সন্ধের মধ্যেও আমরা না ফিরি তাহলে তোমরা আবার বাংলোতে ফিরে যাবে। একটু থেমে ভটকাইকে বলল, শুনেছিস তো! সন্ধের আগেই! ভাল করে দরজা জানালা বন্ধ করে বাইরের বারান্দাতে একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে শুয়ে পড়বে রাতের খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে। আর আমরা যদি রাতেও বাংলোতে না ফিরি তো কাল সকালে আবারও এখানে আসবে।
ভটকাই আতঙ্কিত গলায় বলল, জিপ তো আমরা নিয়ে যাব। অন্ধকার রাতে বাংলোয় হেঁটে ফিরবে কী করে?
ঋজুদা বলল, তা নিয়ে তোর চিন্তা নেই।
বালাবাবু আর ভটকাই কি একটা বলতে গেল প্রতিবাদ করে একই সঙ্গে।
ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বলে জিপটা দেখাল আঙুল দিয়ে। মানে ইশারা করল জিপে গিয়ে বসতে।
ভটকাই দৌড়ে জিপে গিয়ে ওয়াটার বটলটা নিয়ে এল।
ঋজুদা হাত নেড়ে মানা করল।
মানুষখেকো বাঘের বা চিতার মোকাবিলা করার সময় নিজেকে যতখানি সম্ভব হালকা রাখার চেষ্টা করে ঋজুদা। গুলি, রাইফেল, পাইপ এবং টোব্যাকো ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই থাকে না। আমার গলার সঙ্গে ঝোলানো থাকে ঋজুদার জাইস্ এর বাইনাকুলারটি। আর রাইফেল-গুলি। ব্যাসসস।
আমরা দুজনে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। এগোতে লাগলাম মানে চড়াই উঠতে লাগলাম। খুবই আস্তে আস্তে। আগে-পিছনে নয়, পাশাপাশি।
এখন এমন সময় ঋজুদার চোয়ালটি শক্ত হয়ে ওঠে। সবসময় হাসি-ঠাট্টা করা যে মানুষকে আমি খুব কাছ থেকে জানি তার সঙ্গে এই মানুষটার কিছুমাত্রই মিল থাকে না আর। কিছুদূর এগোতেই মনে হল যেন কবরস্থানে এসে পৌঁছেছি। যেন কোনো সাসানডিরি। কোনো প্রাণের সাড়া তো নেইই, এমনকি গাছপালা মাটি পাথর তারাও যেন মৃত। ঠাণ্ডা। হেমন্তের রোদেও উষ্ণতা নেই কোনখানেই।
আমরা এক পা এক পা করে এগোচ্ছি। পঞ্চাশ মিটার মত যাবার পর হঠাৎই আমার সামনের একটা পুটুসের ঝোপের বাইরের দিকে রক্তের দাগ দেখা গেল। শুকিয়ে রয়েছে। তারপরই একটি লালপেড়ে শাড়ির রক্তমাখা অংশ। দাঁড়িয়ে পড়ে শিস দিলাম বুলবুলির মত, ঋজুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। ঋজুদা শিস শুনে এদিকে তাকাতেই থুতনি তুলে ইশারা করলাম। এবং এগিয়ে গিয়ে জায়গাটাতে দাঁড়ালাম। ঋজুদাও আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। পরক্ষণেই একটা বনমোরগ ডানদিকের বেজাত গাছের ঝুপড়ি থেকে হঠাই ভয় পেয়ে মুখে কঁক্-কঁক-কঁক আওয়াজ করতে করতে আর ডানাতে ভর-ভর-ভর-ভর আওয়াজ করতে করতে উড়ে গেল আরও ডাইনে শিকার-গড়-এর সীমানার ডান প্রান্তের দেওয়ালের দিকে। এবং পরক্ষণেই আমাদের দুজনের চোখ একই সঙ্গে পড়ল সাদা শাঁখা আর লাল গালার চুড়ি পরা একটি ফরসা হাতের দিকে। কনুই থেকে হাতটি যেন কেউ ইলেকট্রিক করাতে কেটেছে এমনই পরিচ্ছন্ন ভাবে কাটা সেটি। কোনো মেয়ের হাত। হাতের পাশেই একটি সবুজ রঙা কাচের চুড়ি ভেঙে রয়েছে।
ঋজুদা রাইফেল কাঁধে তুলে নিল। আমিও। দুজনেরই বুড়ো আঙুল সেফটি-ক্যাচে এবং তর্জনী টিগার-গার্ডের ওপরে। খুবই সাবধানে সেই হাতটিকে ছাড়িয়ে আমরা এগোলাম। কনুইয়ের একটু ওপরে, যেখান থেকে হাতটিকে কাটা হয়েছে এক কামড়ে, সেইখানে রক্ত শুকিয়ে গিয়ে বাদামী রঙা হয়ে গেছে। মেয়েটির হাতের আঙুলগুলি ভারী সুন্দর। এমন যার আঙুল সে নিশ্চয়ই ভাল আলপনা দিত। বা ছবি আঁকত নয়তো কবিতা লিখত নিশ্চয়ই। হঠাৎই আমার গা গুলিয়ে উঠল। বমি-বমি পেল ভীষণ। আর তক্ষুণি শিকার-গড় পাহাড়ের ডানদিকে গভীর জঙ্গলে ভরা উপত্যকার গড়ানো আঁচলের সবুজ প্রান্তরের শেষ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে একটি কোটরা হরিণ পাগলের মত ডেকে উঠল। ডাকতে ডাকতে দৌড়ে যেতে লাগল। নদীর এদিকের পার বরাবর।
আশা ভঙ্গ ঋজুদা একটা বড় পাথরের চাঁই-এর ওপরে বসে রাইফেলটা পাশে রেখে পাইপটা ধরাল। আমাকে বলল আজকের চান্সটা মিস্ করলাম আমরা।
কী করে বুঝলে?
কোটরাটার ডাক শুনলি না? বাঘ এখানেই ছিল। আমাদের আসতে দেখে অথবা আওয়াজ শুনেই সরে যায়। সরে যাওয়া মাত্রই মোরগটা বাঘকে দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠে। কতটুকু সময়ের মধ্যে বাঘটা কতখানি দূরত্ব নিঃশব্দে অতিক্রম করল, দেখলি তা? সে নিশ্চয়ই অনেকখানি নিচে চলে গেছে, নইলে কোটরাটা তাকে দেখতে পেয়ে হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচাত না। বলেই বলল, আমার কিন্তু মনে হয় না যে এই বাঘের সামনের পায়ের ডান কব্জি বা পাঞ্জার ওপরের হাড় একেবারেই ভাঙা। একেবারেই ভাঙা থাকলে তার গতি এতখানি দ্রুত হত না। না, তা হতেই পারে না।
ঋজুদা বলল, এদিকে ওদিকে খুঁজে দ্যাখ সম্ভাব্য জায়গায়, লাশের অন্য কোনো অংশও দেখা যেতে পারে।
নিরুপায় হয়েই বললাম আমি ঋজুদা, আমার গা গোলাচ্ছে।
মার খাবি তুই। যা বললাম, কর।
কাছের মোরগের আর দূরের কোটরার চকিত ভীত পিলে-চমকানো অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মত ডাক শুনে না হয় জ্যোতিষীর মতই বলে দিতে পারে ঋজুদা যে বাঘ চলে গেল, তাই বলে আমি তো আর জ্যোতিষী নই। তাছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার বিশ্বাসও নেই। তাই আমার মোটেই পেত্যয় হল না, যে সাঙ্ঘাতিক মানুষখেকো বাঘ, যার দাঁতে-ছেঁড়া সুন্দর হাতখানি একটু আগেই ঝোপের নিচে দেখে এলাম; সে এই পাড়া ছেড়ে সত্যিই চলে গেছে। প্রমাণ নেই কোনো। কিন্তু মন বলল। তাই রাইফেলটাকে বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে তুলে রেখেই এগোলাম। একটু এগোতেই একটা জায়গা দেখে মনে হল এরই আশে-পাশে বাঘ ছিল। বনে জঙ্গলে এরকম অনেকই ব্যাখ্যাহীন মনে-হওয়ার ব্যাপার ঘটে। যাঁরা জানেন তাঁরা আমার কথা মানবেন।
এদিকে কোথাওই পরিষ্কার মাটি বা ধুলো নেই যে বাঘের পায়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাবে। তেমন জায়গা হয়তো আছে কিন্তু এখনও চোখে পড়েনি আমাদের। কিন্তু এতখানি চড়াইয়ের পথ আমরা ক্বচিৎ-রক্ত এবং ঘষটানোর দাগ দেখে দেখেই এগিয়েছি। পরিষ্কার চিহ্ন দেখা গেলে নিনিকুমারীর বাঘ আদৌ অশক্ত কিনা অথবা সত্যিই কতখানি অশক্ত তা বোঝা যেত কিছুটা। ঋজুদা সবসময়েই বলে, কখনও পরের মুখে ঝাল খাস না। এই সব ব্যাপারে তো নয়ই। দশজনের কাছে শোনা কথাও নিজে না দেখে বা না শুনে কখনও মেনে নিবি না। গল্প-গাথাতে আর সত্যে অনেকই তফাত থাকে। বিশেষ করে বনে জঙ্গলে।
সামনেই মস্ত একটি চাঁর গাছ। চিরাঞ্জীদানাও বলে চাঁরকে বিহারে। এর ওড়িয়া নাম জানি না। গাছটা উঠেছে একটা পাথরের চাঁই-এর জগাখিচুড়ি থেকে। পূর্ব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্-এ এমন রক আউটক্রপকে বলে কোপজে। সিংহের আড্ডাখানা সে সব জায়গাতে। বড় কালো পাথরের স্তূপের মত হঠাৎই মাটি-ফুঁড়ে-ওঠা পাথরের খিচুড়ি। এটি সেই রকমই প্রায়। তফাত এই যে এটির মধ্যে একটি অগভীর গুহা। মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠকাতে যেমন আছে। খুবই ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি তিরতিরে ঝরনা গেছে ছায়ায় ছায়ায়। স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে জায়গাটা এবং রৌদ্রালোকিত জায়গা থেকে অনেকই বেশি ঠাণ্ডা। নিজেকে এবং অন্যকেও লুকিয়ে রাখার পক্ষে অতি চমৎকার জায়গা। চোখের আড়ালে বসে এক জোড়া রক-পিজিয়ন ডাকছে ভুকু-ভুকু-ভুকু-ভুকুম ভুকু-ভুকু-ভুকু-ভুকুম। খুব সাবধানে একটু একটু করে এগোতে লাগলাম ওদিকে। সেই গুহামত জায়গাটাতে পৌঁছবার আগে একটু বাঁদিকে চেপে গেলাম। ঋজুদার ওপরে রাগ হচ্ছিল খুব। এই সাঙ্ঘাতিক বাঘের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে পাইপ খাচ্ছে রাজার মত। একটুও কমোনসেন্স নেই ঋজুদার। সাহস ভাল, দুঃসাহস ভাল নয়। আর দুঃসাহস থাকলেও তা নিজের আত্মহত্যার কাজে লাগানোই ভাল, পরস্য পরকে বাঘে-খাওয়ানোর জন্যে ব্যবহার করা অত্যন্তই অনৈতিক কাজ।
এবার নিচু হয়ে একটা ছোট্ট পাথর ছুঁড়ে দিলাম গুহামুখের দিকে। খটাং করে আওয়াজ তুলেই পাথরটা গুহার ভিতরে গিয়ে থিতু হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চাঁর গাছের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটার পাথুরে খিচুড়ি নৈঃশব্দ্য স্তব্ধতর হয়ে গেল। এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম গুহার দিকে। এই গুহা কিন্তু গুহা বলতে আমরা সচরাচর বুঝি সেরকম একেবারেই নয়। মানে, গভীর তো নয়ই, সুড়ঙ্গের মতোও নয়। একে গুহা না বলে প্রস্তুরাশ্রয় বা রকশেলটারই বলা ভাল। ভীমবৈঠকাতে এইরকম অসংখ্য প্রস্তরাশ্রয়ের ভিতরে ভিতরেই আদিম মানুষদের আঁকা নানারকম গুহাচিত্র আছে।
গুহামুখে পৌঁছেই চমকে গেলাম। চমকে গেলাম না বলে আঁতকে উঠলাম বলাই ভাল। সেই লাল-পাড় ঘেঁড়া শাড়িটির আরও কিছুটা। রক্তমাখা চেবানো হাড়-গোড়। মানুষের মেয়ের হাড়-গোড়। ইঃ বাবাঃ। এবং একটি করোটি। তার গায়ে মাংস লেগে আছে এবং একটি মাত্র চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে হাঁ করে, কর্তিত-কঙ্কালের সেই কুৎসিত করোটি থেকে।
মানুষখেকো বাঘের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম : ঋজুদা!
ডেকেই, গুহামুখের পাশের একটি পাথরে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম যাতে এদিকে আর না দেখতে হয়। আমার ঐ হঠাৎ চিৎকারে চমকে উঠে রক্-পিজিয়নের দলটি শক্ত ডানা ফটফটিয়ে উড়ে গেল। এক জোড়া ছিল ভেবেছিলাম আগে। তা ভুল। ঝাঁকে ছিল।
আশ্বাস-ভরা ঋজুদা মুহূর্তের মধ্যে রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে লাফাতে লাফাতে উদিত হল। উত্তরমেরুর স্বাগতম সূর্যেরই মত বলল, কোথায়?
আমি গুহার দিকে আঙুল তুলাম। ঋজুদা গুহামুখে গিয়ে দারুণ বিরক্তিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল। বলল, স্টুপিড।
আমি খুবই আহত হলাম।
বললাম, ঐ দৃশ্যে তুমি ভয় পেতে না?
না। আমি ভেবেছিলাম বাঘ বুঝি তোকে ধরেই ফেলেছে। ভবিষ্যতে কক্ষনো এরকম করিস না আর। রাখালের পালে বাঘ পড়ার গল্পের মত হবে তা হলে কোনদিন। তোর সত্যি-বিপদেও আমি ভাবব, না গেলেও চলে!
বলেই বলল, যা। দৌড়ে যা। পাইপটা পাথরের উপরেই পড়ে রইল। হারিয়ে যাবে এখুনি না তুলে আনলে। তোর সেন্স নেই কোনো। মনমরা এবং আতঙ্কিত অবস্থাতেই আমি যখন ঋজুদার পাইপ হাতে করে এখানে ফিরলাম দেখি ঋজুদা রাইফেলটাকে আমি যে-পাথরে বসেছিলাম তার গায়ে শুইয়ে রেখে ঐ করোটির প্যাঁটপ্যাঁট করে তাকিয়ে থাকা চোখটির প্রায় গা ঘেঁষেই বসে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে।
দেখেই ঘা ঘিন ঘিন করে উঠল। মানুষটার ভয় নেই না হয় মানলাম। কিন্তু ঘেন্না-পিত্তি? তাও কি নেই কোনো?
পাইপটা হাতে দিতেই বলল, বোস পাশে।
খুব রেগে গেছিলাম। বসলাম না তাই।
আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাখ।
ঋজুদার চোখকে অনুসরণ করে চেয়ে দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য। এই প্রস্তরাশ্রয় যেন কোনো দূরবীনেরই চোখ। অন্ধকার ঘরের দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দূরের আলোকিত কোনো ঘর বা বারান্দা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, সামনের ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড় বন এবং উপত্যকা তেমনই দেখাচ্ছে। এমনকি নদী এবং নদীর ওপারে আবারও চড়াইতে উঠে-যাওয়া গভীর বনাবৃত ধুঁয়োধুঁয়ো পাহাড়শ্রেণী সবকিছুই চমৎকার দেখা যাচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা এই ঝিংকুপানি গ্রামে আসার পথটি যেখানে কনসর-এর শাখা নদীটি পেরিয়ে এসে ডাইনে বাঁক নিয়েছে তাও পরিষ্কার চোখে পড়ছে এখান থেকে। স্কাউটিং-এর এমন ভাল্টেজ-পয়েন্ট আর হয় না। এবং বাঘের চেয়ে ভাল স্কাউট তো কেউই নয়। মানুষখেকো বাঘ হলে তো কথাই নেই!
মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম ঐ দিকে। পাথরের গুহাতে বসে বাইরের রৌদ্রালোকিত প্রান্তর ঝাঁটি আর গভীর জঙ্গলে, ইন্দ্র দুর্গার এর আঁকা ছবি নদীর মত নদী, দূরের রহস্যময় ধোঁয়া-ধোঁয়া পাহাড়শ্রেণী; সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে।
ঋজুদা বলল, চল্ এই শিকার-গড় জায়গাটাকে আজ ভাল করে সার্ভে করি। এই কিল-এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই যে বাঘ এখানে ফিরে আসবে। বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিস না? এই হল নিনিকুমারীর বাঘের একটা বড় ঘাঁটি। এখানে সে প্রায়ই থাকে। আমরা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিতে একটা ভুল করে ফেললাম। বিনা-নিমন্ত্রণে তার বাড়িতে আমাদের আসা উচিত হয়নি। কারণ সে দেখে গেল যে আমরা তার অন্দরমহলের খোঁজ পেয়েছি। দেখে গেল বলেই এখানে সে আর ফিরে নাও আসতে পারে। কিছুদিন যে আসবেই না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অথচ এই বাঘের যা রেকর্ডস তাতে ওর পেছনে দৌড়ে বেড়ানো প্রায় অসম্ভবই। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত ব্যাপার। দৌড়ে বেরিয়েছে বলেই কেউ তাকে বাগে পাননি। আমরা দৌড়ে না বেড়িয়ে তার বাড়িতেই চৌকি বসাব। যে সময়ই সে চায়, নিক। বাড়িতে সকলকেই ফিরতে হয় কখনও না কখনও। সে খুনী, ডাকাত বা মানুষখেকো বাঘ যেই হোক না কেন!
আমি বললাম, নিনিকুমারীর বাঘের বাড়িতে আছেটা কোন্ আপনজন? মা, না বৌ, না ছেলেমেয়ে?
ঋজুদা হেসে, নাক তুলে গন্ধ নিল। মানুষের পচা মাংসের গন্ধ ছাপিয়েও বাঘের গায়ের গন্ধ ভাসছিল। বলল, আছে। নিজের গায়ের গন্ধ। বাঘই হোক কী মানুষ, কারও কাছেই তার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসার জন আর কেউই নেই। বাঘ বেঁচে থাকার জন্যে আর কারও দয়ার বা সঙ্গর বা ভালবাসার বা সেবার ওপরে নির্ভর করে না। সে বলতে পারিস নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। নিজের গায়ের গন্ধ নিতে সে আবার ফিরে আসবে। দেখিস। বলেই, উঠে পড়ে বলল, চল্।
আমরা ঐ জায়গাটা ছেড়ে আসার আগে গাছটার দিকে ভাল করে চাইলাম নিচ থেকে। মাচা বাঁধলে কোথায় বাঁধা যায় তাই দেখতে।
ঋজুদাও আমার চোখ অনুসরণ করে দেখল। বলল, এখানে বসতে হলে শুধু দিনের বেলাতেই। মানে, সকাল থেকে প্রথম বিকেল অবধি। রাতে বসতে হলে বাইরের দিকে কোনো গাছে বসতে হবে যাতে তার যাওয়া আসার পথে তাকে গুলি করা যায়।
বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঋজুদা বলল, দ্যাখ রুদ্র।
চেয়ে দেখি, শিকার-গড়-এর সীমানার পাঁচিলের একটা অংশ সরে গেছে একেবারে এই চাঁর গাছটিরই গা ঘেঁষে। পাঁচিলটা ভেঙে ভেঙে গেছে অনেক জায়গাতেই। অশ্বত্থ আর বটের চারা গজিয়েছে জায়গায় জায়গায়। নানারকম বুনো ফুলের লতা, যারা পাথরের কাছ থেকেও জল চায়, জল নিংড়ে নিয়ে ফুল ফোঁটায়। লাল, হলুদ, হালকা-বেগুনি, ছেলেবেলার সুন্দর সব স্বপ্নর মত।
বললাম, বাঃ।
বাঃ কী রে রুদ্র! বল বাঃ বাঃ বাঃ। এর চেয়ে বড় বাঃ আর কিছুই নেই। বাঘ শিকার-গড়ে ঢোকে তার এই গুহার ডেরা ছেড়ে এই পাঁচিল পেরিয়েই। তার কোন দায়টা পড়েছে যে তাকে শিকার-গড়ের প্রধান ফটক দিয়ে যাতায়াত করতে হবে? ওরা তো আর মানুষের মত স্ট্যাটাস সিম্বলের শিকার নয় যে গরমের শহর কলকাতায় গলায় বো লাগিয়ে, ডিনার জ্যাকেট পরে, ক্লাবের ডাইনিং রুমে গিয়ে বসবে! দেশ স্বাধীন হবার চল্লিশ বছর পরেও ইংরেজদের বাঁদর সাজার মত কোনরকম হীনম্মন্যতায় ভোগে না তারা! বাঘেরা নিজেরাই নিজেদের মালিক। দিল্লির লালকেল্লা বা সাউথ ব্লক তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়। ওর যেখান খুশি সেখান দিয়েই যাবে ও। এবং এইখান দিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক বলে আমার মনে হয়, এইখান দিয়েই ও যায়। চল্। একটু এগোলেই বোঝা যাবে।
বেশিদূর এগোতেও হল না। একটু যেতেই বাঘের এবং হয়তো অন্যান্য জানোয়ারেরও চলার চিহ্ন পরিষ্কার দেখা গেল। গেম-ট্র্যাক। সেই গেম-ট্র্যাকটি সত্যিই পাঁচিল টপকে শিকার-গড়ের চত্বরে গিয়ে পড়েছে। ঠিকই। কিন্তু আমাদের দুজনের কারওই লেজ না থাকায় অতখানি উঁচু পাঁচিল দাঁড়ানো অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে পেরোনো অসম্ভব ছিল। দাঁড়ানো অবস্থাতে কেন, হাই জাম্পের দৌড়বার মত সমান জায়গা থাকলেও ওলিম্পিকে প্রথম হওয়া হাই-জাম্পারও এই পাঁচিল পেরোতে পারত না। তাই ঘুরেই গেলাম আমরা। একটু ঘোরা পথ। তারপর শিকার-গড়ের মধ্যে ঢুকে যেখানে গেম-ট্র্যাকটি চত্বরে ঢোকার কথা সেখানে এসে আবার পথটিকে দেখা গেল। চত্বরের এক জায়গায় নরম মিহি মাটি ছিল। সুরকি মেশা। যেখানে বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট। অনেক দাগ। নতুন এবং পুরনো।
ঋজুদা বলল, পরে এখানে ফিরে আসব। এখন এগিয়ে চল্।
গেম-ট্র্যাক ধরেই আমরা সাম্বপানির রাজাদের একসময়ের বিলাসবহুল শিকার লজে ঢুকলাম। সদর দরজার একটা পাল্লা খোলা।
দরজার সামনের ধুলোতে কত জানোয়ারের আর সাপের চলাচলেরই যে চিহ্ন তার ঠিক নেই। কিন্তু নিনিকুমারীর বাঘের পায়ের দাগ ছিল না। দেখা গেল যে তার নিজস্ব গেম-ট্র্যাক প্রধান দরজাকে অনেক দূর থেকে এড়িয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে নহবৎখানাতে। মন্দিরের সানাই বাজত যেখান থেকে, কটক থেকে আসা নামকরা সানাইওয়ালারা যখন সানাই বাজাতেন তখন প্রভাতী সূর্যের আলোয় কেমন লাগত সাম্বপানির রাজাদের শিকার-গড়ের এই গা-ছমছম জায়গাটিকে, কে জানে!
ঋজুদা বলল, কী রে রুদ্র! নিনিকুমারীর বাঘের আরেক আস্তানা তাহলে এই নবহৎখানা! সেখানে উঠেই দেখলাম চমৎকার বন্দোবস্ত থাকার। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা এমন সুন্দর আস্তানার কথা ভাবাই যায় না। চাঁদ, রোদ ইচ্ছে করলেই হাতের মুঠোয়। আর ইচ্ছে না করলে তাদের মুখ দেখারই দরকার নেই।
সেখান থেকে নেমে আমরা চণ্ডীমন্দিরের দিকে এগোলাম। এই সেই জাগ্রত ঠাকুরানী। যাঁর কৃপাধন্য হয়ে বাঘ অমরত্ব লাভ করেছে বলেই বিশ্বাস করেন এখানের মানুষেরা।
ঋজুদা বলল, ভটকাই-এর কাছ থেকে শটগানটা নিয়ে এলে ভাল হত।
–কেন?
মন্দিরে নিশ্চয় সাপের আড্ডা থাকবে। কেন জানি না। আমার মন বলছে। মানুষের পরিত্যক্ত মন্দিরে কেন যে সাপ থাকে তা আমি জানি না। কিন্তু বহু জায়গাতেই দেখেছি যে, থাকে।
বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম চণ্ডীমন্দিরের সামনে। মন্দিরের দরজার পাশে বড় বড় দুটো জবা গাছ। না বলে দিলে কেউ বিশ্বাসই করবে না জবা বলে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছ দুটি। হাজার হাজার ফুল ফুটেছে ঝুমকো জবার। সেই গাছ দুটির পাশে দুটি জ্যাকারাণ্ডা গাছ।
ঋজুদা বলল গাছদুটিকে দেখিয়ে, নিশ্চয়ই এ দুটি পরে কেউ লাগিয়েছে বুঝলি! মানে, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর। ইংরেজরা পূর্ব-আফ্রিকারও একটি অংশের মালিক ছিল। তাই বহু ভাল ভাল গাছ তারা ভারতে এনে লাগিয়েছিল। ভারতের গাছও নিয়ে গিয়ে লাগিয়েছিল অন্যান্য দেশে। ভারতে লাগানো পূর্ব-আফ্রিকার গাছেদের মধ্যে ছিল আফ্রিকান টিউলিপ, কেসিয়া ও অ্যাকাশিয়া ভ্যারাইটির নানারকম গাছ এবং আরও অনেকই গাছ। এই জ্যাকারাণ্ডাও সম্ভবত সাহেবদেরই আনা। তবে এখন তো এর ফুল ফোটার সময় নয়। তাই শুধু পাতাই আছে ডালে ডালে।
জ্যাকারাণ্ডার সঙ্গে অ্যানাকোণ্ডার বেশ মিল না?
পাণ্ডিত্যে আমিও কিছু কম যাই না, এমনই ভাব দেখিয়ে বললাম।
ঋজুদা হেসে ফেলে বলল, ধ্যুৎ। অ্যানাকোণ্ডা তো সাপ। দক্ষিণ আমেরিকার সাপ। তার সঙ্গে পূর্ব আফ্রিকার গাছের কী সম্পর্ক?
ইচ্ছে হল ভটকাই-এর মত বলি, ঐ হল। একই কথা।
ঐ দ্যাখ। ঋজুদা বলল।
তাকিয়ে দেখি, হেমন্তকাল হলে কি হয় এক জোড়া প্রকাণ্ড কালো গোখরো মন্দিরের দরজার কাছে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে লকলকে জিভ বের করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।
আমি সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের স্লিং কাঁধে ঝুলিয়ে দু-হাত জড়ো করে বললাম : জয় মা চণ্ডী।
ঋজুদা ধর্ম-টর্ম মানে না। তবে অন্যের বিশ্বাসে আঘাতও দেয় না। সাপেদের দিকে মনোযোগভরে চেয়ে রইল রাইফেল রেডি-পজিশনে ধরে। যদিও ঐ হেভি রাইফেল সাপ মারার পক্ষে অকেজো। হেভি বা লাইট কোনও রাইফেল দিয়েই সাপ মারা সুবিধের নয় আদৌ। কিন্তু মারামারি করতে হল না। সাপদুটি নিজে থেকেই সরে গেল মন্দিরের একেবারে ভিতরের অন্ধকারে। আমরা পায়ে পায়ে মন্দিরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে এবং জানালা দিয়েও সূর্যের আলো ঢুকছে।
ঋজুদা বলল, কোণারকের সূর্য মন্দিরের সঙ্গে কিন্তু আশ্চর্য মিল আছে এই মন্দিরের। যদিও খুবই ছোট। দেওয়ালে বা গায়ে কোনও অলঙ্করণও নেই। অথচ ওড়িশার রাজা লাঙুলা নরসিমাদের আমলে বানানো কোণারকের মন্দিরের সঙ্গে সূর্যের যেরকম বার ঘণ্টার সম্পর্ক সকাল-দুপুর-সাঁঝের, এর সঙ্গেও তাই। আমি জুতো খুলে প্রণাম করলাম।
ঋজুদা বলল, দ্যাখ খুশি করতে পারিস কি না! ঠাকুরানীর দয়া যদি বাঘের ওপর থেকে শিকারির ওপরে একবার সরিয়ে আনতে পারিস তবে তোকে আর পায় কে?
আমি বললাম, দেবীর দয়া হলে সবই হতে পারে। কাল সকালে আমি পুজোর পোশাকে আসব এখানে।
ঋজুদা বলল আপাতত দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে আয়। বলে আয়, যেন অপ্রসন্ন না হন।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এগারটা বাজে প্রায়। কী করে যে সময় যায়। দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে এলাম। দেখি, ঋজুদা ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হঠাৎই আমার দিকে ঘুরে বলল, রুদ্র, বি কেয়ারফুল। বাঘ উপত্যকাতে যায়নি। আমাদের সাড়া পেয়ে পাঁচিল টপকে এই শিকার-গড়েই এসেছে।
আমি তাড়াতাড়ি কাঁধের রাইফেল হাতে নিয়ে বললাম, কী করে জানলে? প্রমাণ?
প্রমাণ নেই। আমার মন বলছে। প্রমাণও হয়ত এক্ষুনি পাওয়া যাবে। বলেই, যেখানে নরম ধুলোতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছিল সেদিকে ফিরে চলল ঋজুদা।
আমাকে বলল, তুই গার্ড দে, আমি একটু দেখি। বলে, নিজের রাইফেলটাকে ঘাড়ের ওপরে হেলান দিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে বাঘের পাগ-মার্কসগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল। বলল, অ্যাই দ্যাখ।
এগিয়ে গিয়ে দেখি পুরনো দাগের ওপরে একেবারে টাটকা দাগ। সত্যিই বিরাট বাঘ। নদীর বালিতে বা বৃষ্টির পরের কাদায় অনেক সময়েই পায়ের চিহ্নকে বড় দেখায়। কিন্তু এই শিকার-গড়ের পাথুরে চত্বরে শক্ত জমির ওপরেও এই ছাপ এত বড় হয়ে পড়েছে যে বাঘটার প্রকাও সাইজ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকার কথা নয়। যে-সব গল্প কলকাতায় এবং এখানেও শুনেছি এই নিনিকুমারীর বাঘ সম্বন্ধে তাই যথেষ্ট ছিল। তার ওপরে তার প্রমাণ বহর দেখে তলপেট সত্যিই গুড়গুড় করে উঠল।
ঋজুদা আমার মনের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বলল, লাজার দ্যা টাইগার, দ্যা মেরিয়ার। বড় টার্গেট হলে নিশানা নিতে সুবিধে, গুলি ঠিক জায়গায় লাগাতে সুবিধে। ভালই তো! বাঘ যত বড় হয় শিকারির বুক তত ফোলে। বলেই, পায়ের দাগগুলো খুব ভাল করে আরও একবার নিরীক্ষণ করে বলল, বুঝলি রুদ্র, সব বাজে কথা। এই বাঘের সামনের ডান পায়ের থাবাতেই চোট আছে। দ্যাখ না ডানদিকের ওপরের ছাপ কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু কব্জিতে চোট থাকলে ছাপ অন্যরকম হত। হয়ত জখম হওয়ার পর নিনিকুমারীর বাঘ হাঁটার সময়ে ডান পা ফেলার আগে আহত থাবাটি গুটিয়ে নিত। তাই দেখে কেউ এই তত্ত্ব প্রচার করে দিয়েছিল। পরে কেউই আর তার সত্যাসত্য বিচার করতে যায়নি। শিকার আর শিকারিদের জগতে যত বড় বড় গুলেড়ু আছে তেমন বাঘা বাঘা গুলেড়ু আর তিড়িবাজ খুব কম জগতেই আছে। গুলবাঘ ডেঞ্জারাস নয়। কিন্তু গুলবাজরা হাইলি ডেঞ্জারাস।
বলেই, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রাইফেলটা তুলে নিল হাতে।
আমি বললাম, তুমি তো আচ্ছা লোক। বলছ, বাঘ এই শিকারগড়ে এসেছে আর তুমি এখানে আড্ডাখানার মেজাজে কথা বলছ?
ঋজুদা বলল, হুঁ। সেটাও স্ট্রাটেজি। বদল করেছি শুধু এইমাত্রই। যদিও এ সেয়ানা বাঘ রাইফেল বন্দুক চেনে। তবুও এমনই ভাব কর যেন আমরা মন্দির দেখতেই এসেছি।
বাঃ। মন্দির দেখতে এলে তো শিকার-গড়ের প্রধান ফটক দিয়েই ঢুকতাম। আমরা ঐ চাঁর গাছের ছায়ায় পাথরের জগাখিচুড়িতে যেতে যাব কেন ওর লেজে লেজে?
ভুল করে। ট্যুরিস্টরা পথ না ভুললে আর কে পথ ভুলবে? তাছাড়া এ তো আর কনডাকটেড ট্যুরও নয় যে গাইড আছে! চল্ আমরা গড়ের দেওয়ালে বসি। আমি পাইপ খাই আর তুই গলা ছেড়ে গান গা।
গান?
আমি চোখ কপালে তুলে আকাশ থেকে বললাম। ভাবলাম আমি কি চোঙা লাগানো গ্রামোফোন যে রেকর্ড চালালেই বেজে যাব?
ইয়েস। আমার অর্ডার। গান। কথা কম। গান।
যাঃ বাবাঃ। কী অন্যায়। বলে, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দেওয়ালে বসলাম।
ঋজুদা বলল, গ্রামের দিকে মুখ করে বোস। গ্রামের লোকদেরও গান শোনানো দরকার। এই বাঘটাকে মারতে হলে ওদের প্রত্যেকের মন থেকে এই ঠাকুরানীর বাঘের মীথটাকে এক্সপ্লোড করতে হবে। কীরকম ভূতে-পাওয়া ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া হয়ে আছে মানুষগুলো দেখলি না। শরীরের শীত ছাড়ানো সোজা। মনের মধ্যে শীত ঢুকলে তা ছাড়ানো ভারী কঠিন। আর মানুষের মতই তো সব! বাঘটাও যে-সম্মানের সে যোগ্য নয় সেই সম্মান পেতে পেতে হয়ত অনেক মানুষেরই মত নিজেকেও ভগবান ভাবতে আরম্ভ করেছে। এবার বাঘ-ভগবানকে ভূত বানাবার ভার নিয়েছি আমরা। নে। তাড়াতাড়ি। গান।
কী গান?
আঃ। দরকারের সময় দেরি করিস কেন? গলা ছেড়ে গা না! তাড়াতাড়ি। বাঘ যেন শুনতে পায় সরে গিয়ে থাকলেও।
ঋজুদা এমনিতে যে-স্কেলে কথা বলে তার চেয়ে অনেকই উঁচু স্কেলে কথাকটি বলল।
এলো যে শীতের বেলা গাইব? আমি শুধোলাম।
আরে ধুৎ। ওসব গান তুই বালিগঞ্জের ড্রইংরুমে গাস। দেখছিস গান দিয়ে বাঘকে ভয় পাওয়ানোর ব্যাপার আর…। নজরুলের গানই বরং গা কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট। নইলে ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের কোনও গান? ও চিও চিও চিও চি। ও চিও চিও চিও চি?, জানিস না?
জানি না।
তবে জানিসটা কি?
সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা গাইব?
ঋজুদা বলল, একদম না। দিল্লিওয়ালারা রবিঠাকুরের জনগণমন অধিনায়ক জয় হে-কে সুপারসিড করে ইকবাল-এর ঐ গান এখন ন্যাশনাল সঙ বলে চালাবার চেষ্টা করছে দেখছি। আই প্রোটেস্ট। সারে জহাঁসে আচ্ছা গাইতে হবে না।
তবে? ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা গাইব?
–গা! গা! আমিও গলা দেব।
গলার শিরা ছিঁড়ে গেলেও তা আবার গিট দিয়ে বেঁধে নেওয়া যাবে এমনই মনোভঙ্গি নিয়ে আমি একেবারে তারাতে ধরলাম গান। সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদাও। যদিও আমাদের দুজনের কেউই বেসুরো গাই না, তবুও ঐ তারস্বরের দ্বৈতসঙ্গীতে শিকার-গড়-এর দানো-প্রেত প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই আঁতকে উঠল। শিকার-গড়ের চত্বর জুড়ে, নিচের উপত্যকায় আমাদের ডুয়েটের সঙ্গে অসংখ্য পাখি, হনুমান, ময়ূর, বার্কিং ডিয়ার তাদের ভয়ার্ত গলা মেলাল। কী ট্রেমেলো! ইংরেজীতে যাকে বলে ‘ক্যাকোফনি’ তাইই আর কী? নিনিকুমারীর বাঘ যদি তখনও সে তল্লাটে থেকে থাকে এবং আড়াল থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করেও থাকে তবে তারও পিলে চমকে যাবার কথা। এমনই দুই শিকারি এবং শিকারের এমন প্রক্রিয়া কোনও বাঘেরই চোদ্দপুরুষে কেউ দেখেনি। শোনে তো নিই! নিনিকুমারীর বাঘের দোষ কী?
মানুষ, হনুমান, হরিণ, পাখ-পাখালি সকলের সম্মিলিত ‘ক্যাকোফোনি’ যখন থামল তখন ঋজুদা বলল, চল্ আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। আরও বেশি করলে শেষে বাঘ হার্ট-ফেল করেই না মরে। আর হার্ট-ফেল করে মরলে মৃত মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে তোর রাইফেল-হাতে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ছবিও ছাপা হবে না খবরের কাগজে।
আমি বললাম, কেন? হার্টফেল করা বাঘের বুকে একটা গুলি ঠুকে দিলেই হবে। জানব তো আমরাই! দেখছেটা কে? তা না হলে ভটকাই কি কলকাতা গিয়ে আর ওই পোড়ামুখ দেখাতে পারবে? কেষ্টনগর সিটিতেও পারবে না।
তা ঠিক। সেটা একটা ভাবার মত কথা বটে! ঋজুদা হেসে বলল।
তারপরই বলল, চল্ আবার ঐ দিকে। বউটার হাতটা আর শাড়ির যতটুকু অবশিষ্ট আছে নিয়ে যেতে হবে। নইলে দাহ করতে পারবে না ওর আত্মীয়রা। আর শবদেহ বা তার কিছু অংশও দাহ না করতে পারলে তো তার আত্মা মুক্ত হবে না। শান্তিও পাবে না। এইরকমই বিশ্বাস হিন্দুদের।
তুমিও তো হিন্দুই, না কি?
হ্যাঁ। আমিও। ঋজুদা বলল।
তবে? তুমি তো ধর্ম মান না।
এইসব আলোচনা পরে কোনদিন করব। তাছাড়া এসব কথা বোঝার মত বয়সও তোর এখনও হয়নি।
আমি বললাম, আমরা ফটক দিয়ে যাচ্ছি আর বাঘ যদি দেওয়াল টপকে গিয়ে ওখানে অপেক্ষা করে থাকে অন্যদের জন্যে?
করুক। তাইই তো চাই আমরা। চার চোখের মিল হলেই তো গুড়ুম। কিন্তু তা সে করবে না। অত কাঁচাছেলে সে নয়।
কেন?
বলছি তোকে। বুদ্ধি নিনিকুমারীর বাঘও কিছু কম ধরে না আমাদের চেয়ে। তবে এই মুহূর্তে সে যে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওকে এইখান থেকে তাড়াব কাল। দেখবি। তারপর ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা। ফিরে ও আসবেই। তিনদিন পরেই আসুক, কী সাতদিন পর। আর তখন ওকে সারপ্রাইজ দিতে হবে। শিকারটা যতখানি শারীরিক সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার ব্যাপার তার চেয়ে একটুও কম মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। এবং প্রতিপক্ষ যত বেশি যোগ্য, যুদ্ধও তত আনন্দর। বিপদেরও বটে। বিপদটাই তো আনন্দ। কী বল্?
শিকার-গড় ফটক পেরোবার পর আর কোনো কথাবার্তা বললাম না আমরা। মুখে বললেও, ঋজুদা তো আর ভগবান নয়, তাই বাঘ যে ওদিকে যাবেই না একথা জোর করে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। নিঃশব্দেই আমরা গিয়ে আমাদের কাজ সমাধা করলাম। ঋজুদাকে ইশারাতে বললাম, কাটা হাতটা নিতে। আমি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ঐ গুহা থেকে রক্তে ভারী হয়ে থাকা ছেঁড়া-শাড়ির যতটুকু ছিল ততটুকু নিয়ে এলাম। যখন ফিরছি, কেবলই মনে হচ্ছিল কেউ যেন লক্ষ করছে আমাকে আড়াল থেকে। ঋজুদার কাছে এসে যখন পৌঁছলাম তখনও সেই মনে হওয়াটা গেল না। ঋজুদাকে বললামও। ঋজুদা বলল, মাঝে মাঝে পেছন দিকে নজর রেখে এগুতে। তারপর বলল, বাঘ যদি আমাদের পিছু নেয় তো নিক না। কোনো কিছুই যে আগেকার মত নেই, আর থাকবেও যে না, তা তার জানা দরকার। পিছু নিলে খুশি হব আমি।
পাহাড়ের চড়াই ওঠা বরং সহজ, কিন্তু উৎরাই নামা কঠিন। বিশেষত পেছনে মানুষখেকো বাঘ অনুসরণ করছে তা জানার পর। আমাদের আসতে দেখেই ভটকাই আর বালাবাবু জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এলেন এদিকে। আর দৌড়ে এল যে মানুষটির বৌকে বাঘে নিয়ে গেছিল সে। বৌয়ের কাটা হাত নিয়ে কী কান্না যে কাঁদতে লাগল শিশুর মত, তা চোখে দেখা যায় না। ভটকাই আতঙ্কিত চোখে সেই নিপুণভাবে কাটা হাতের দিকে চেয়ে ছিল। ঋজুদা আমাকে বলল জিপে গিয়ে খুব জোরে জোরে হর্ন বাজা তো রুদ্র। এই ঘুমিয়ে-পড়া গ্রামকে জাগিয়ে দে। মানুষগুলোকে একটু নড়িয়ে দেওয়া দরকার।
আমি গেলাম হর্ন বাজাতে। ঋজুদা বালাবাবুকে ডেকে কাঁঠাল গাছের নিচে পাতা আমকাঠের তক্তার বেঞ্চে বসে কী সব শলা পরামর্শ করতে লাগল।
হর্ন শুনে ভটকাই দৌড়ে এসে বলল, কী রে! বাঘ পালিয়ে যাবে না? কী করছিস কি?
বললাম, বাঘকে তাড়াবার বন্দোবস্তই হচ্ছে।
-সে কি?
–হ্যাঁ।
–গান গাইছিলি কেন? তুই আর ঋজুদা? আমরা তো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাবলাম, আমিও এখানে বসেই গলা মেলাই তোদের সঙ্গে।
গ্রামের প্রধানকে বালাবাবু ডেকে আনলেন। ঋজুদা আর বালাবাবু তাকে সব ভাল করে বোঝালেন। আমি একটু একটু ওড়িয়া বুঝি। ভটকাই কিছুই বুঝতে পারছিল না বলে কেবলই বলছিল, কী বলছে রে? কী বলল রে ঋজুদা? কী হবে রে?
বললাম, কাল দেখতে পাবি।
আঃ। কালের তো দেরি আছে। বলই না।
ঋজুদার কথা শুনে সকলেরই চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল। ওদের পক্ষে যেন একথা বিশ্বাস করাই অসম্ভব যে কাল সারা গাঁয়ের লোকে শিকার-গড়ে গিয়ে ভাল করে ঠাকুরানীর পুজো দেবে। প্রধান অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু হবে কী করে? এত মানুষের প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে?
আমি নেব। ঋজুদা বলল।
তুমি? একা? আর এই দুটি ছোট ছেলে?
ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। আমি আর ও নেব। যদি কারও গায়ে আঁচড়ও লাগে তার জন্যে আমরা দায়ী।
প্রধান অবিশ্বাসী গলায় বললেন, বড়লোকেরা ওরকম কথা অনেকই বলে। আমাদের চিরদিনই বলে এসেছে। রাজাও কম মিথ্যে কথা বলেননি। গরিবের প্রাণের দাম কে দেয়? কারও কিছু হলে আপনি কী করে প্রাণের দাম দেবেন?
ঋজুদা একটু ভাবল। তারপর বলল, কাল পুজো দিতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তবে তার পরিবারকে দশ হাজার টাকা দেবো। আর কেউ খণ্ডিয়া হলে পাঁচ হাজার।
খণ্ডিয়া কী রে? ভটকাই শুধোল।
বললাম উনডেড। ইনজিওরড।
ঋজুদার মুখে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটার কথা শোনার পর একাধিক লোকের মুখ দেখে মনে হল তারা মরে বা আহত হয়েই ধন্য হতে চায়। অত টাকা কোনদিন একসঙ্গে হাতে ধরার কথা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল হবে কিনা এই চিন্তা যেন। সকলেরই চোখে-মুখে।
প্রধান আবার প্রশ্ন করলেন, সাম্বপানি থেকে পুরোহিতকে না আনলে পুজো কে করবে? রাজার মন্দির! তাছাড়া ঠাকুরানী এখন বাঘের হয়ে গেছেন। আমরা পুজো দিলে উনি যদি আরও চটে যান আমাদের ওপরে?
ঋজুদা একমুহূর্ত কী ভাবল। তারপর বলল, আমিই সকালে সাম্বপানি থেকে পুরোহিত নিয়ে আসব। তোমরা পুজোর অন্য সব বন্দোবস্ত করে রেখ। অনেক লোক লাগবে মন্দির আর মন্দিরের পথ পরিষ্কার করতে। সব জঙ্গল হয়ে আছে। কাল যত লোক মন্দিরে যাবে সকলের জন্যে শিকার-গড়েই খিচুড়ি রান্না হবে। সকলে ওখানেই ভোগ খেয়ে আসবে। মাংস আর খিচুড়ি। আমরা ঠিক সকাল আটটার সময়ে এসে পৌঁছব। আমাদের পাহারাতে সকলে যাবে। আবার আমাদের পাহারাতেই গ্রামে ফিরে আসবে।
বালাবাবু সকলকে সব বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন এই বাবু কলকাতা থেকে এসেছেন শুধু তোমাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে। এবং উনি বাঘের পেছনে দৌড়োদৌড়ি করে বাঘকে এই শিকার-গড়ে বা তার আশপাশেই মারতে পারবেন বলে মনে করছেন। তোমরা ওঁকে সাহায্য করো। কোথাও কোনও মানুষ বা জানোয়ার মারা যাওয়ার খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে কুচি-খাঁই পাহাড়ের নিচের বাংলোয় গিয়ে খবর দেবে।
ঋজুদা বালাবাবুকে বলল, কত চাল, ডাল, মশলা, আনাজ, মাংস হবে তার একটা হিসেব করতে হবে তাড়াতাড়ি। বলে, যে মানুষটির বৌয়ের কাটা হাত আমরা নিয়ে এলাম তাকে সঙ্গে নিয়ে জিপে করে চলে গেল নদীর দিকে শবের অবশিষ্টাংশ দাহ করার জন্যে। সঙ্গে সেই লোকটির ছোট ভাইও গেল। আমাকে আর ভটকাইকে বলে গেল তোরা এখানে থাক। বালাবাবুদের সঙ্গে। আমি আসছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। লোকটার ছোট ভাইয়ের হাতে টাঙ্গি। জাল কাঠ কেটে নেবে দাহ করার জন্যে নদীপারের জঙ্গলের মধ্যে থেকে।
ভটকাই কোনদিনও গ্রাম দেখেনি। গ্রামের মানুষেরা যে গরিব তা ও জানত, কিন্তু এত গরিব, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না ওর। ওর মুখ-চোখ দুঃখে বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আমারও হত প্রথম প্রথম। তারপর সয়ে গেছে এখন। ভটকাই চুপ করে বসে ছিল। পথের পাশের একটি বড় পাথরের ওপরে। আমিও কোনো কথা বলছিলাম না। বালাবাবু অত্যাচারিত, অবিশ্বাসী, ভয়ে কুঁকড়ে-থাকা গ্রামের মানুষদের একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঋজুদা আর আমার গুণপনার কথা বলছিলেন। বলছিলেন যে, এবারে নিনিকুমারীর বাঘের দিন সত্যিই শেষ হয়েছে। এদের কাছে বাঘের জারিজুরি টিকবে না।
একজন বালাবাবুকে বলল, তাহলে এতদিন এঁদের আনেনি কেন? আমাদের গ্রাম আর লাগোয়া গ্রাম থেকেই তো বাঘ নিয়েছে তিরিশজন মেয়ে-পুরুষ। গরু ছাগলের তো শেষই নেই।
বালাবাবু দুহাত নেড়ে বললেন, সে তো আমার ব্যাপার নয়। আমাদের ডি এফ ও সাহেবেরও নয়। তাছাড়া এরা তো ভারতবর্ষেই ছিলেন না। তারপর বললেন, তোমরা যদি নিজেরা এখন একটু সাহস না করো তবে উনি ফিরে যাবেন। তোমরা কি এইরকম মরার মতই বাঁচতে চাও চিরদিন, না যেমন করে বাঁচতে আগে তেমন করে?
একটি মাঝবয়সী লোক বলল, আমাদের আবার বাঁচা। কেউ না কেউ তো আমাদের চিরদিনই খেয়েছে। কখনও রাজা, কখনও সুদখোর, কখনও ঠিকাদারবাবুরা। আর এখন খাচ্ছে বাঘে। ঐ সব খাদকদের খাওয়ার কথা সকলে জেনেও জানেনি। বাঘে খেলে রক্ত বেরোয়। সকলেই জানে তাই। নইলে বাঁচা মরায় আর তফাত কী আমাদের? পাঁচ বছর বাদে মাইক আর ঝাণ্ডা লাগানো জিপে করে পার্টির নেতারা ধবধবে পোশাক পরে আসেন একবার করে। হাতজোড় করে বলেন, মা ভ্রাতা ভগিনীমান, মু ভোট পাঁই ঠিয়া হইছি আইজ্ঞা, তমমানে মত্ত্বে ভোট দিয়ন্তু। ভোট নেবার আগেই হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। ভোট পাবার পর সব ভোঁ-ভাঁ। এই তো চলল চল্লিশ বছর। আমার বয়স হল পঞ্চাশ বছর। দশ বছর থেকেই এই দেখে আসছি। আমার বাবা যেমন গরিব ছিল আমি তার চেয়েও অনেক বেশি গরিব হয়ে গেছি। নিনিকুমারীর বাঘকে যদি এ বাবুরা সত্যিসত্যিই মেরে দিয়ে যেতে পারেন তাহলে এর পরে আমরা ঐ মিথ্যেবাদী নেতাগুলোকে ধরব আর টিপে টিপে মারব। আমরা তো এই মিথ্যের বলি হয়েই জীবনটা কাটিয়ে গেলাম। অন্তত, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে….
আমি তাকিয়ে দেখলাম, মানুষটির দু’চোখে জল ছিল না। আগুনের হলকা ছিল। পেট আর পিঠ এক হয়ে গেছে। অন্য সব লোকদেরও শরীরগুলো টিঙটিঙে কিন্তু পেটগুলো ফোলা ফোলা। ঋজুদা বলছিল খিদের জ্বালা সইতে না পেরে ওরা ভাতের সঙ্গে আফিঙের গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায়। শুধু নুন ভাত। তাও জোটে না। জুটলেও এক বেলা। বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। বাঘের জন্যে তাও বন্ধ। আফিঙ চুর্ণ খেয়ে খেয়ে পিলে বড় হয়ে যায়। বুড়োও হয়ে যায় তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সে।
ভটকাই বলল, কলকাতায় বা কেষ্টনগরে আমাদের মধ্যে যারা খারাপও থাকি তারাও কত ভাল আছি এদের চেয়ে, না রে?
হুঁ।
-দুসস। মনই খারাপ হয়ে গেল তোদের সঙ্গে এসে। আগে জানলে আসতাম না।
আমি কিছু বললাম না উত্তরে।
কিছুক্ষণ পরে দূরের জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে জিপের এঞ্জিনের গোঙানি ভেসে আসতে লাগল।
ভটকাই কান খাড়া করে বলল, কী রে! ঋজুদা কি ফিরে আসছে? এত তাড়াতাড়ি দাহ হয়ে গেল?
–দাহ আর কী! একটা তো হাত শুধু। আর রক্তে ভেজা শাড়ি। কতক্ষণ আর লাগবে।
–হুঁ। বলে, ভটকাই যে পথে ঋজুদার জিপ আসবে সেই পথের দিকে চেয়ে রইল।