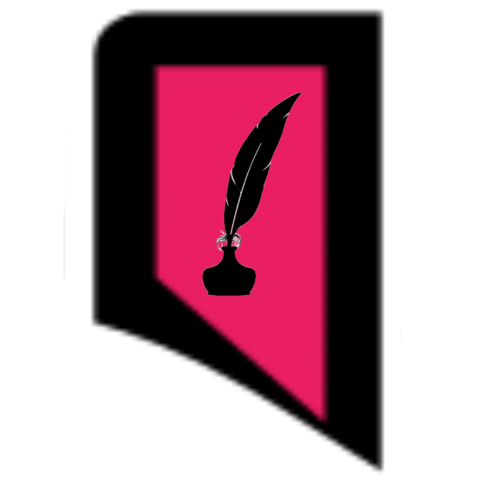মুকুন্দপুরের মনসা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
তেইশ
ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। কেউই কোনও কথা বলতে পারছিলুম না। না আমি, না ভাদুড়িমশাই। নিরুর কথা শুনে আমার আরও খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে, একটা জীবনের এমন কোনও জায়গা আমরা ছুঁয়ে ফেলেছি, যে জায়গাটা বড় বেদনার। কে জানে, কত দিনের কত অসম্মান, অপমান আর গ্লানির জজ্ঞাল সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। সেই জঞ্জালকে এইভাবে বাইরে টেনে আনবার কি সত্যি কোনও অধিকার আছে আমাদের।
ভাদুড়িমশাইয়ের উপরে একটু-একটু রাগও যে আমার- না হচ্ছিল, তা নয়। যে-কাজে তিনি এসেছেন, সেইটে ঠিকমতো করলেই তো গোল মিটে যায়। তা না- করে ঝোপের এদিকে-ওদিকে লাঠি চালিয়ে অনর্থক কেন আবহাওয়াটাকে এইভাবে আরও অস্বস্তিকর করে তুলছেন তিনি? সত্যপ্রকাশের ড্রইংরুমের দেওয়ালে তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর ফটো দেখেই তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে, কাজের লোক বলে নিরুর পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসলে সে ওই ভদ্রমহিলারই ছোট বোন। কিন্তু আন্দাজ করলেই নিরুকে সে-কথা বলতে হবে? বলে এইভাবে তাকে আরও অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিতে হবে? না না, কাজটা ভাদুড়িমশাই মোটেই ভাল করেননি।
নিরুর কথায় আমার চমক ভাঙল।
“যাঁর জন্যে আমার এত ভাবনা, সেই জামাইবাবু মানুষটা কী সাদাসিধে আর সরল দেখুন। দিদির সঙ্গে আমার মুখের এই যে মিল, এটা কি আর মা পিসিমা আর ছেলেপুলেদের চোখে পড়েনি? পড়েছে। কিন্তু তাঁরা ভেবেছেন যে, এমন মিল তো কত লোকের সঙ্গেই কত লোকের থাকে। এর বেশি আর কিছু ভাবেননি তাঁরা। কিন্তু তাঁরা না-ভাবলেও নামজানা একজন গোয়েন্দা যে ঠিকই এটা নিয়ে ভাববেন….শুধু যে ভাববেন, তা নয়, মিলের কারণটাও ধরে ফেলতে পারবেন, এই সহজ কথাটা পর্যন্ত জামাইবাবু বুঝতে পারেননি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “বুঝতে পারলে তিনি কী করতেন? যে ক’দিন আমরা এখানে আছি, অন্তত সেই ক’টা দিনের জন্যে তোমার দিদির ফটোখানাকে তিনি বোধহয় ড্রইং রুম থেকে সরিয়ে রাখতেন। তাই না?”
নিরু বলল, “কী জানি। না-ও সরাতে পারতেন। যে-রকম লোক, হয়তো বলতেন, কী দরকার, বাইরের কেউ যদি বোঝে তো বুঝুক না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা তো হল, কিন্তু অন্য-একটা প্রশ্ন তোমাকে করেছিলুম, তার জবাব এখনও পাইনি।”
“দিদি বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে আমি কখনও আসিনি কেন, এই তো?”
“হ্যাঁ, আসোনি কেন?”
“উপায় ছিল না, তাই আসিনি।”
নিরু আবার মুখ নিচু করল। তাকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল আমার। ভেবেছিলুম, ভাদুড়িমশাই আর এগোবেন না, তাঁর প্রশ্নে এবারে ছেদ টানবেন। ব্যাপারটা শুধুই অস্বস্তিকর নয়, প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নিতান্ত অসহায় আর দুর্বল একটা প্রাণীকে যেন খাঁচার মধ্যে আটকে ফেলেছেন তিনি, আর তারপর খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে চোখা একটা বল্লম দিয়ে ক্রমাগত তাকে খুঁচিয়ে চলেছেন।
কিন্তু না, প্রশ্নে তিনি ছেদ টানলেন না। বললেন, “উপায় ছিল না-ই বা কেন?”
নিরু মুখ তুলল। এবারে তাকে দেখে যেন ধাঁধা লাগল আমার। মনে হল, যতটা দুর্বল তাকে ভাবছিলুম, ঠিক ততটা দুর্বল হয়তো সে নয়। তার চোখে একটু আগে একটা অসহায়তার ছায়া ভাসতে দেখেছিলুম। সেই ছায়াটা হঠাৎ সরে গেছে। ধারালো চোখে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “তার আভাস যে আপনাদের দিইনি, তা নয়। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে যে, ওইভাবে বললে হবে না, স্পষ্ট করে সবিস্তারে সবটাই আপনাকে বলতে হবে। তাই না?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কোনও-কিছু অস্পষ্ট না-রাখাই তো ভাল।”
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিরু বলল, “ঠিক আছে, সবটাই তা হলে বলব। প্রথমেই জেনে রাখুন আমার দিদি আর আমি একই বাবার মেয়ে বটে, তবে একই মায়ের মেয়ে নই।”
আমি বললুম, “তার মানে?”
“মানে অতি সহজ। আলিপুরদুয়ারের জনার্দন বিশ্বাস তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। দিদি তাঁর প্রথম স্ত্রীর মেয়ে, আর আমি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর। দিদি আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়েস এখন চল্লিশ হত। দিদির বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছর বয়েসে। আমার বয়েস তখন সাতের বেশি নয়। কিন্তু তখনই আমাকে দেখে সবাই বলত যে, মেয়েটা একেবারে দিদির মতো হয়েছে।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা তো হয়েছই। নইলে আর আমি সম্পর্কটা আন্দাজ করলুম কী করে?”
নিরু বলল, “না-ও কিন্তু হতে পারতুম। আমরা দুবোন যদি যে-যার মায়ের মতো দেখতে হতুম, কিংবা আমাদের যে-কোনও একজন তার মায়ের মতো, তা হলেই আর মিলটা থাকত না। অথচ মজা কী জানেন, আমরা কেউই আমাদের মায়ের আদল পেলুম না, আমাদের দুজনের মুখেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমাদের বাবার মুখের ছাপ। তফাত শুধু একটাই। দিদি ফর্সা, আমি কালো।”
আমি বললুম, “সে কী, তেমন কালো তো তুমি নও।”
এতক্ষণে হাসি ফুটল নিরুর মুখে। যেন আমার কথাটা শুনে খুব মজা পেয়েছে, এইরকমের হাল্কা গলায় বলল, “ঠিক ঠিক, কাঠকয়লার মতো কালো তো আর নই, ওই যাকে কালো মেয়ের বাবা-মায়েরা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে চালাতে চায়, তা-ই আর কি। তা আমার মাও দেখেছি চিঠিপত্রে কক্ষনো ‘কালো’ লিখতেন না। লিখতেন ‘মেয়ে আমার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা’। ভারী মজার ব্যাপার, তাই না?”
ভাদুড়িমশাই দেখলুম, নির্বিকার। বললেন, “কিসের চিঠি?”
“কীসের আবার,” সেই একইরকমের হাল্কা গলায় নিরু বলল, “বিয়ের সম্বন্ধের। বাবা তো বেশিদিন বাঁচেননি। দিদির বিয়ের বছর তিনেক বাদেই তিনি মারা যান। আমান বয়েস তখন দশ। তার বছর ছ’সাত বাদেই শুরু হল আমার বিয়ের চেষ্টা। বাবা বেঁচে নেই, তাই কাগজে ওই যে সব বিয়ের বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাই দেখে-দেখে মাকেই অগত্যা পাত্রপক্ষের কাছে চিঠি লিখতে হত। চিঠি পেয়ে তাদের কেউ যে আমাকে দেখতে আসত না, তাও নয়। আসত, রসগোল্লা-সন্দেশ খেত, কিন্তু পছন্দ করত না। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। একে তো মেয়ের গায়ের রং কালো, তার উপরে আবার গরিব বিধবার মেয়ে, চট করে কারও পছন্দ হবেই বা কেন?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। নিজেকে তুমি ‘গরিব বিধবার মেয়ে’ বলছ কেন? সত্যপ্রকাশবাবুদের অবস্থা তো যদ্দুর বুঝতে পারছি খুবই ভাল। তাঁর তো নেহাত গরিব-ঘরে বিয়ে হবার কথা নয়। তা হলে?”
নিরু বলল, “এতে এত অবাক হচ্ছেন কেন? রূপকথার রাজপুত্তুররা কি কখনো ঘুঁটেকুডুনির মেয়েকে বিয়ে করে না? তা নইলে তাদের মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে কী করে? তবে হ্যাঁ, আমার মতো পেত্নি হলে চলবে না, কুঁচবরণ কন্যে হওয়া চাই। তা জামাইবাবু যেমন রূপকথার রাজপুত্তুর, আমার দিদিও তেমনি ডাকসাইটে সুন্দরী। যেমন দুধে-আলতা রং, তেমনি টানা-টানা চোখ, তেমনি টিকোলো নাক, আর তেমনি নিখুঁত মুখের গড়ন। তা হবে না-ই বা কেন, বাপ আর মা, দুজনের যা-কিছু ভাল, দিদি সবই পেয়েছিল যে। চোখে তো দেখিনি, তবে সব্বাইকে বলতে শুনেছি যে, আমার বড়মার রং ছিল নাকি মেমসাহেবদের মতো। তার উপরে দিদির আবার গুণও ছিল অনেক।”
“যেমন?”
“যেমন ছিল লেখাপড়ায় ভাল, তেমনি ছিল রান্না আর সেলাই-ফোঁড়াইয়ের হাত, আবার তেমনি ছিল গানের গলা। মনটাও ছিল খুব নরম। ঘটকের মুখে নিশ্চয় জামাইবাবুর বাবা সবই শুনে থাকবেন। আলিপুরদুয়ারেও তো ব্যাবসার কাজে মাঝে-মাঝে যেতেন, তাই সেখানকার লোকেদের কাছেও হয়তা শুনে থাকতে পারেন। নইলে আর আমাদের মতো গরিবমানুষের ঘরে তাঁর পায়ের ধুলো পড়বে কেন। তা মেয়ে দেখে তো তিনি মুগ্ধ। ঠিকুজি মিলে যেতেই আমার বাবাকে বললেন, ‘আপনাকে কিছু দিতে হবে না, বিশ্বাসমশাই, আপনি শুধু পুরুত ডেকে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলুন। খাপত্তর সব আমার। আমিই আমার মা-লক্ষ্মীকে রাজরানির মতো সাজিয়ে আমাদের ঘরে নিয়ে তুলব।’ তা তিনি তুলেওছিলেন।”
একটুক্ষণ চুপ করে রইল নিরু। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, “মুশকিল কী জানেন, আমাদের জীবনটা তো সত্যিই একটা রূপকথা নয়, সবরকমের দয়া দাক্ষিণ্য আর মহত্ত্বের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত তাই একটা ‘কিন্তু’ থেকে যায়।”
“কী রকম?”
“এই যে-রকম হয় আর কি। হাতের মুঠো হয়তো খোলাই থাকে, আর তাই দেখেই আমরা ধন্যি-ধন্যি করতে থাকি, ওদিকে মনের দরজায় যে খিল পড়ে গিয়েছে, সেইটে আমরা বুঝতে পারি না। আমার বাবা অবিশ্যি বুঝেছিলেন। জামাইবাবুর বাবা যেদিন বিয়ের কথা পাকা করে আসেন, আমার বাবা সে-দিন থাকে বলেছিলেন, কাজটা ভাল হল কি না কে জানে। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, হঠাৎ এমন কথা তাঁর মনে হচ্ছে কেন, তখন বাবা বললেন, “সম্পর্কটা সমানে-সমানে হলেই টেকসই হয়, তা নইলে বড়-একটা ধোপে টেকে না। বড়ঘরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মেয়েটা পর হয়ে গেল।” মা অবশ্য বাবার কথায় কান দেননি। সত্মা হলে কী হয়, দিদিকে ভীষণ ভালবাসতেন তো, তাই মা-মরা যে মেয়েটাকে তিনি একদিন কোলে টেনে নিয়েছিলেন, সে যে বড়লোকের বাড়ির বউ হতে চলেছে, মা তখন তাতেই দারুণ খুশি।”
“কিন্তু পরে বুঝলেন যে, বাবার কথায় কান দিলেই ভাল হত, কেমন?”
“কী জানি। তবে বাবা যে ভুল বলেননি, বিয়ের পরেই সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। কী হন। জানেন, খুব ঘটা করে আর দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে গরিবঘরের মেয়েটিকে তো চৌধুরিমশাই তাঁর ছেলে। বউ করে এ-বাড়িতে নিয়ে এলেন, কিন্তু তার পরে আর একদিনের জন্যেও তাকে তার বাপের বাড়িতে যেতে দিলেন না।”
আমি বললুম,”সে কী!”
নিরু বলল, “আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, আমি বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এক বিন্দুও আমি বাড়িয়ে বলছি না। দিদিকেও যেতে দেননি, জামাইবাবুকেও যেতে দেননি। এমন শী অষ্টমঙ্গলাতেও না। সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, অষ্টমঙ্গলার নিয়মই নাকি এঁদের নেই।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তাও কি হয় নাকি?”
নিরু বলল, “হবে না কেন? যেখানে আপনি সম্পর্ক রাখতে চাইছেন না, সেখানে সবই হয়। নিয়ম কি আর নেই। আছে। তা নইলে আর বিয়ের পরে জোড় খুলবার জন্যে সুজাতা তার বরকে নিয়ে কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল কেন। নিয়ম আছে নিশ্চর। যেমন আমাদের আছে, তেমনি এঁদের আছে। কিন্তু আমার বাবা যখন মেয়ে-জামাইকে তাঁর ওখানে নিয়ে যাবার জন্যে মুকুন্দপুরে এলেন, জামাইবাবুর বাবা তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, অমন কোনও নিয়মই এঁদের বাড়িতে নেই।”
“অর্থাৎ তিনি সত্যি-সত্যিই তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাইছিলেন না?” ভাদুড়িমশাইয়ের কথা শুনে হেসে উঠল নিরু। বলল, “সত্যি-সত্যি নয় তো কি মিছিমিছি?” তারপরেই হঠাৎ বিষণ্ণ গলায় বলল, “বাবা বুঝে গেলেন যে, শুধু তাঁর মেয়েটিকে এঁরা চেয়েছিলেন আর-কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাননি। বুঝে গিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর তো কিছু করারও ছিল না। ….কী জানেন, আমার বাবার তো ঠিক মরবার বয়েস হয়নি, তবু যে এরপরে আর খুব বেশিদিন তিনি বাঁচেননি, তারও হয়তো এটাই কারণ। বড়লোকের দরজায় এসে ফিরে যাবার এই অপমানটাই তিনি সহ্য করতে পারলেন না।”
“সত্যপ্রকাশেরও কি তাঁর বাবার কথায় সায় ছিল?”
“ছিল কি না, তখন সেটা আমরা জানতে পারিনি। পরে জেনেছি যে, ছিল না। কিন্তু সায় না থাকলেই বা জামাইবাবু কী করবেন? বলতে গেলে তিনিও তো তখন নেহাতই ছেলেমানুষ, অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা তাঁর তখনও হয়নি। এই বাড়িতে এসে ঢুকবার পরে তাঁরই কাছে শুনেছি যে, ব্যাপারটা নিয়ে কষ্ট যে শুধু দিদির ছিল, তা নয়, কষ্ট ছিল জামাইবাবুরও। কিন্তু বাবার অমতে বউকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারে যাবেন, এমন সাহসই তাঁর ছিল না।”
“সত্যপ্রকাশের বাবা ছেলে-বউকে যেমন তোমাদের বাড়িতে যেতে দেননি, তেমনি তোমাদেরও কখনও বলেননি এখানে এসে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে?”
“কক্ষনো বলেননি। কিন্তু বললেই কি আমরা আসতে পারতুম? বাবা যেভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন এই বাড়ি থেকে, তারপরেও কি আসা সম্ভব?”
আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল নিরু। তারপর বলল, “আপনি তো জানতে চাইছিলেন, দিদি বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে আমি কখনও আসিনি কেন। এখন আপনিই বলুন, এই অবস্থায় কেউ আসতে পারে? আসতে কি আর ইচ্ছে হত না? ‘হত। কিন্তু সাহস হত না। দিদি তো ভীষণ ভালবাসত আমকে। বাসবে না-ই বা কেন, আমাদের তো আর কোনও ভাইবোন নেই, শুধু দিদি আর আমি। তাই দিদিকে ছেড়ে থাকতে আমারও খুব কষ্ট হত। তখন তো কিছু বুঝতে পারতুম না। রোজই বাবাকে বলতুম,দিদির কাছে নিয়ে চলো। বাবা কিছু বলতেন না, চুপ করে থাকতেন।”
নিরু উঠে দাঁড়াল। বলল, “আপনারা কি এখুনি আবার বেরোবেন?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “এখুনি নয়। পরে হয়তো একবার রঙ্গিলাদের ওখান থেকে ঘুরে আসব।”
নিরু বলল, “তা হলে একটু বসুন। মা আর পিসিমাকে দেখে আসি একবার। সেইসঙ্গে আপনাদের চা’ও নিয়ে আসছি। এক্ষুনি যেন আবার বেরিয়ে পড়বেন না।”