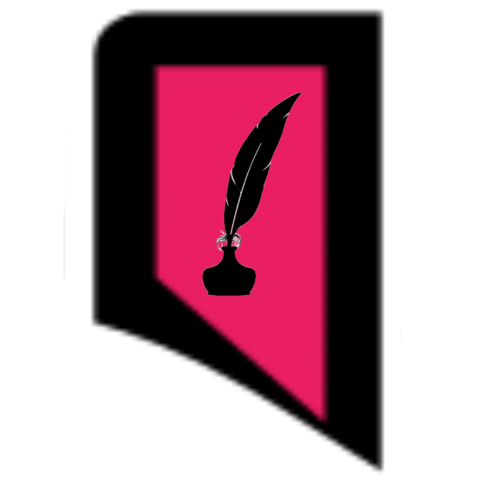দেবযান (উপন্যাস) – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
০১.
কুড়ুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুন্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ী এদেশের লোক কখনো দেখেনি। পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চে নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আসর সাজানো। হয়েছে। খুব জাঁকের বিয়ে।
রাত সাড়ে ন’টা। রায়সাহেবের বাড়ীর বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুড়লে বিনোদপুরের মত অজপাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েচেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামন্ডপ থেকে নানারকম শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।
–ও কি পালমশায়, না-না-মাছের মুছোটা ফেললে চলবে না–
–ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাও-এর বালতি–পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, সুরুচি ও বড়মানুষী চালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না–এঁদের পাত যে একেবারেই খালি–সন্দেশ আর দুটো নিতেই হবে–আজ্ঞে না, তা শুনবো না–বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে–
ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনে উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র–সে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোণ মেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মানুষ আদৌ নেই-ফলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।
ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ী আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়েদেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন–সুতরাং বড় বাড়ীর মধ্যে ওকে নিতান্তই একা। থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।
ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো–আরে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব? ওরে কে আছিস্ এদিকে পাতে লুচি দিয়ে যা–
যতীনের মনটা খুশি হ’ল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না। আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটচে না।
আহারাদি শেষ হয়ে গেল! এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো। হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্যে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েছে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।
হুস্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গায়ে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগলো।
দলের অনেকে চীৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।
দু-চারবার এ রকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।
তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুস্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে চেয়ে দেখচিল একদৃষ্টে ঊর্ধ্বমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত দুরাবস্থায় পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে যেন–সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।
সূতোরগাছির মেঘনাথ চক্কত্তি ওকে দেখে বল্লে–এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ী খেলে নাকি? তোমার নেমন্তন্ন ছিল? তা তোমাদের বলতে সাহস করে–কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামলি, না হয় দুটো টাকাই হয়েছে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন করে খাওয়াবে বাড়ীতে! তোমরা গিয়ে গিয়ে নিজেদের মান। খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে—ছিঃ–
যতীন যখন বাড়ী পৌঁছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।
বাঁশবনের মধ্যে সুড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘরদোর, বাইরের চন্ডীমণ্ডপ, তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্থকষ্টে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকায় গোলাটা বিক্রী করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনির্সিড়ি ক’খানা মাত্র বর্তমান আছে।
আলো জ্বেলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে–তেলের পয়সা জোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে? অন্ধকারে শূন্য বাড়ীতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।
আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত শ্রাবণ-রাত্রিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ীর বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।
মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনের বড় ছেলেটি আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে খাবার তৈরী করলে। বল্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরী করে নিলুম, সস্তাও হবে কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।
পথে দুষ্টুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি যাবার আগেই, আশাকে ঠকাবার জন্যে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বল্লে–কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?
হয়তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ ছ’মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল।–মনে। আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?
–যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো। যে-ইত্যাদি…
আহা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নে রঙীন্ রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালার সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েছে সে সব দিন–তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।।
সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়ীতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও শ্বশুড়বাড়ী যায় না; একবার বছর তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিল যে সে যাচ্চে।
দুপুরের আগে সে গিয়ে পৌঁছুলো। অনেক আগ্রহ করে গিয়েছিল। শাশুড়ীঠাকরুণ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছিলেন, তাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন সুরে বল্লেন–থা থাক্ হয়েছে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?
–এই সব দেখাশুনো করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?
–ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করছে–ডেকে দিচ্ছি।
যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলে না।
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস। করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারা কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বল্লেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকীর বয়েস এক বছর মাত্র।
খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল–ওদের মা কোথায়? দেখচি নে যে?
শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বল্লেন–সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন দশেক হোল গিয়েছে, তার দিদির শ্বশুরবাড়ী বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমা নেই!
যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেছে, আশাকে বলবে–চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে–ঘরের লক্ষ্মী। ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?
তারপর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস্ করলে–কবে আসবে?
–আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পূজোর সময় পর্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাঁধবার লোক নেই, বুড়োমানুষ। এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।
শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেরি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশথ তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বল্লে–দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চল্লেন যে। রইলেন না?
–না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে। নেই, অনেকদিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।
আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে–তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে সুর নিচু করে বল্লে–একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন!
যতীন বল্লে–না, বলছি নে। কি কথা রে আন্না?
–দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী ওর সই-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।
যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে–ঠিক বলছিস্ আন্না!
পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।
যতীন চলে আসছে, আন্না বল্লে–আজ থেকে গেলেন না কেন। দাদাবাবু?
–না, থাকা হবে না আন্না। বাড়ীতে কাজকর্ম ফেলে এসেচি বুঝলি নে?
আন্না আবার বল্লেদিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?
বালিকার সুরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমানুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ীর আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।
যতীন অবিশ্যি রইল না, চলেই এল।
চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা কোনো রকমে বাড়ীতে টেনে এনেছিল মাত্র।
তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েচে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো। সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেচে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্মৃতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।
তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক’বছরের মানসিক যন্ত্রণায় ওর শরীর গিয়েছে, মন গিয়েছে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।
যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ী নেমন্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহূত অনাহূত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না–কিছু ভাল লাগে না।
০২.
যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূৰ্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূৰ্ব্বদিকের আসেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েছে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে।
গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ীর উঠোনে। বাবা…মা… বউদিদি… মেজদিদি… পিসিমা দুই ছোট ভাই… আশা… খোকা-খুকীরা…
কত ভালবাসতো সবাই…সব স্বপ্ন হয়ে গেল…কেউ নেই আজ…
সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তার এক পয়সা উপার্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে। যা-তা বলে।
আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্যে যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো– শাশুড়ী ঠাকরুণের হাতে অনেক টাকা আছে–কোন্ দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েছে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বল্লে–দ্যাখো, এই সময়টা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।
এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাশুড়ীর টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ী সহজে মরবে না।
পিছনে কেউ বলে–এই মোটর গাড়ীর শব্দ ওঠে দ্যাখো না! যতীনের বৌ টাকার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে–এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো–আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলি।
তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে সে সব এখানে ব্যক্ত করবার নয়।
এই সমস্ত ব্যঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়। সয়ে গিয়েছে, আর লাগে না–মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্বরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ দেখায় নাকি মেয়ে কি পুরুষ! সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।
মানুষ হয়ে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চিন্তার বালাই নেই তো!
এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়ীতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনোদিন দেয় না–বলে, বাড়ীতে অসুখ, রাঁধবার লোক নেই–বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই ইত্যাদি।
যতীনের বাড়ীর পেছনে খিড়কির বাইরে ছোট্ট একটু বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, আম কাঁঠালের সময় গাছের আম কাঁঠাল মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে–শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্চে। রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডু কেন তার বাড়ীর কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?
এক সময়ে বড় বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে–কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রী করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এই সব নির্জন রাত্রে বইগুলোর জন্যে সত্যি মনে কষ্ট হয়।
এইরকম নির্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে।
গত পাঁচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মানুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।
বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মানুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত–যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে খেত–যখন না থাকতো শুয়ে চি চি করতো। গায়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো–হয়তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে চিৎ এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো–সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।
অনেকে পরামর্শ দিত–ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আসুন–না এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো, নানারকম ধান্ধাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না? ইত্যাদি।
এ কথার কোনো উত্তর সে দিত না।
০৩.
আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যন্ত্রণা ভোগ করান না। হয় সারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোঁপ। পড়ত বেলায় পাখীর দল কি কি করচে, কেলে-কোঁড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্নিগ্ধ ফুল ফুটেছে, নির্মেঘ আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।
গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায়। রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।
ওর মনে একটা ভয়ানক কষ্ট…বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঠবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা..আশালতা…
না, চিঠি সে দেবে না–দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বুকে বড় বাজবে, পূৰ্ব্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বেচ্ছায় নতুন দুঃখ বরণ করার নির্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক দুঃখ পেয়েচে, আর নয়।
সব মিথ্যে…সব ভুল…প্রেম, ভালবাসা সব দুদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে হাবুডুবু খায়, তখন শত রঙীন কল্পনা তাতে আরোপ ক’রে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপস্রিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুষ্ক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।
এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অনুভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নরনারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা বালিকা প্রেমের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করচে। নিরুপায়। অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য করে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদলের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।
দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে, এই কষ্টই তাকে যন্ত্রণা দিয়েচে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে– সে নতুন মানুষ হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।
যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেছে। পাগল হয়ে যাবে নাকি?
হঠাৎ সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদছে।
একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ-নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখচি। যতীন। কাঠের গুঁড়িটা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েছে আর সে ও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েছে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে–হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।
যতীন বাড়ী ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ী, অন্ধকার দোর। ভাঙা তক্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে ঝাড়েও না, পাতেও না, তোলেও না। অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল–সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!
সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয়তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠাণ্ডা লাগানো দুৰ্ব্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে হইল–কেউ খোঁজ খবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টদের বৌ ওদের উঠোনে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলা পর্যন্ত ঘরের দোর। বন্ধ দেখে বাড়ী গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এদিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।
বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুললে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েছে। কাছাকাছি কারো বাড়ী নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেঁচানোরও শক্তি নেই।
সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ী ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলছে না এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে–যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্চে আজকে!…বেলা দশটা বাজে এখনও সাড়াশব্দ নেই। বেলা বারোটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনও দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না! পাড়ার মধ্যে খবরটা বল্লে।
পাড়ার দু-চারটা ষন্ডাগুণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।
–ও যতীন-দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলন–ও যতীন-দা–
কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোলদোর ভাঙা হোল।
যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেছে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।
তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের সঙ্গে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের আবার অসুখ হয়েছে, এ খবরও কেউ রাখে না।
নবীন বাঁড়য্যে বল্লেন–আহা, ভবতারণ-দা’র ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েছে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বৌটিরই বা কি আক্কেল–ছ’ বছরের মধ্যে একবার চোখের দেখা দেখলে না গা–হ্যাঁ?
সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।
যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সত্ত্বারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।
০৪.
যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচে।…
পুষ্প! এক সময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?
দুজনে–
নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
কত খেলেচি ফুল ভাসায়ে জলে–
সেই পুষ্প।
নৈহাটির ঘাট নয়–সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আড়পারে। সেখানে ছেলেবেলায় তার মাসীমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েচে। এক এক সময় ছ’মাস আটমাস মাসীমার কাছেই সে থাকতো। মাসীমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসীমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন, সাগঞ্জ-কেওটাতে মাসীমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।
বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসীমার বাড়ী আর রাস্তার ও-পাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখুয্যে বাঁশবেড়ে বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে–তার হাসি–সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো। দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে এবং তার বাবার মত সম্রান্ত লোক গঙ্গার ওপারে কোথাও নেই।
ধীরে ধীরে পুষ্পের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, ধীরে ধীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন, ভেসে যেতো। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অশ্বত্থ গাছ যে পুরোনো ঘাটটায় ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেচে, জগদ্ধাত্রী পূজোর ভাসানের দিন পাঁপরভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েচে। কেমন করে যে সেই রূপগৰ্ব্বিতা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পচ্ছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ী না গেলে অনুযোগ করতো–এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়েস তখন ওর হয়নি।
দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর দুবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেছে, কত গল্প করেচে, কত ঝগড়া করেছে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েছে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেছে–সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে। পড়ে।
মাসীমার মৃত্যুর পরে কেওটার পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর–বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অনুরাগের রঙীন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জন্যই চলে যায় এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে–তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়–তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।
পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল–চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন। কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য? আশালতা সে ঘরে ঢোকে নি–আশালতার ঘর আলাদা।
সেই পুষ্প।
যতীন অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েচে তেরো বছর পরে সে বিয়ে করে। আশাকে, বিয়ে করেচেও আজ দশ বছর–এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর। পরে কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে
নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
খেলা করেছিল ফুল ভাসাবে জলে–!
বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েচেঘাটের রানায় শেওলা জমেছে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্যামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েচে রাঙা আলো, কিন্তু সেটা পড়েছে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনও সেই প্রাচীন পাখীর দল ডাকচে বড় অশত্থাগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছে ত্রিবেণীর দিকে..যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারোয়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করচে..তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনও সেই রকমটি দেখতে রয়েচে কেমন করে?
কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল–পুষ্প তো নেই। সে তো বহুঁকাল মরে গিয়েছে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখছে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বল্লে–অবাক হয়ে চেয়ে দেখছো কি? চিনতে পেরেচো? বল তো আমি কে?
যতীন তখনও হাঁ করে চেয়েই আছে। বল্লে–খুব চিনেছি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল–
পুষ্প খিল খিল করে হেসে উঠে বল্লে–মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল–এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।
যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এ সব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জ্বরের ঘোর খুব বেড়েচে, জ্বরের ঘোরে আবোল-তাবল স্বপ্ন দেখচে। তবুও সে এতকাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!
পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে–পুরোনো দিনের মত দুষ্টুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, থাকতে পারচি না–এখন এসো আমার সঙ্গে।
সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারছে। যাবে কোথায় চলে সে? পুস্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েচে, ঐ তো চূণবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলার ভাঙা সিঁড়ি।
পুষ্পকে সে বল্লে–তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেছে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েছে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন। দেখি নি!
পুষ্প বল্লে–কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা! তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর। হওয়ার দিন থেকে? দিন রাতে অনবরতই তো তোমার শিয়রে বসে।
–বলিস কি পুষ্প! আমার শিয়রে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল তো–আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?
–সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের। কি হয়েচে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।
কথা শেষ করে পুষ্প ওর হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ সুস্থ ও হালকা অনুভব করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নিজ্জীর্ব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ–সবই তার মত।
পুস্প বল্লে–দাঁড়িও না যতুদা–এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন। বোধ হয় বিশ্বাস হয়েছে? বুঝলে এখন?
পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কী করে! এখনও রাত আছে। অন্ধকার রয়েছে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বলচে, নবীন বাঁড়য্যের বাড়ীর দিকে একটা কুকুরে ঘেউ ঘেউ করছে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়? কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনও কি সে স্বপ্ন দেখছে?
পুষ্প বল্লে–এখন বিশ্বাস হোল যতুদা? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম দেখলে না?
-–কি করে এলাম?
–ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত। আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো, পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে। উড়ে যাচ্চি
যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। দুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্চে, যতীন কিছুই জানে না।
সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি। স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে? স্বপ্ন যদি না হয়। তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা–hallucination?
–একেই বলে মৃত্যু?
এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে–বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েছে–বেঁচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে–দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে–কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূৰ্য্য দেখা যায় না–অথচ অন্ধকারও নেই–ভারি চমৎকার এক ধরনের। অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।
এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।
একি! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোধূলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হলদে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা মৃদু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালায়, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চূড়োয়। ওকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙীন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বাল্যের শত সুখের, শত আনন্দস্মৃতির রঙ্গস্থল সেই পুরোনো জায়গা–ঐ তো ওপারে শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চৰ্য্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া!
এমন সময়ে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল। তার খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।
যতীন বল্লে–এ কোথায় আলি পুষ্প? বুড়োশিবতলার ঘাট না? এ কি সাগঞ্জ-কেওটা?
পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়যৌবনা, শান্ত আনন্দময়ী মূৰ্ত্তি মানবীর হয় না–কি রূপই তার ফুটেছে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী! যতীন অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।
পুষ্প বল্লে–না যতুদা–এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়!…
তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে–এ আমাদের স্বর্গ তোমার আর আমার স্বর্গ।