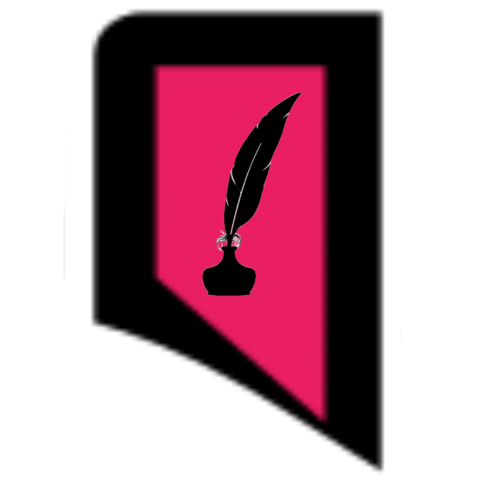মুকুন্দপুরের মনসা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
পচিশ
নিরু চলে যাবার পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম, “রাত তো আটটা বাজতে চলল, এখন তা হলে কী করব?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “নিরু এখন একটু অস্থির হয়ে আছে, ন’টার আগে খাবার ডাক পড়বে বলে মনে হয় না। টর্চটা বার করুন।”
“কেন, এখন আবার বেরুবেন নাকি?”
“বেরুব, তবে দূরে যাব না, বাড়িটার চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে আসব শুধু। আর তা ছাড়া ভট্চাজ-মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।”
“ভট্ট্চাজ-মশাই মানে?”
“এঁদের পুরুতঠাকুর গোবিন্দ ভট্চাজ। ভদ্রলোকের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। অথচ সেদিন শেষরাত্তিরে একমাত্র উনিই নাকি চোর পালাবার শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন। দেখি উনি কী বলেন।”
জাম্পারটা খুলে রেখেছিলুম : পাঞ্জাবির উপরে আবার সেটাকে চড়িয়ে নিয়ে বললুম, “চলুন।”
ভাদুড়িমশাই গলায় একটা মাফলার জড়ালেন। আমাকে বললেন, “আপনি মাফলার এনেছেন তো?”
বললুম, “শুধু মাফলার কেন, একটা আলোয়ানও এনেছি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আলোয়ানের দরকার হবে না, তবে মাফলারটা জড়িয়ে নিন। বাইরে হিম পড়ছে, ঠান্ডা সাধারণত গলাতেই লাগে।”
সুটকেশ খুলে মাফলারটা বার করে বললুন, “আমি রেডি।”
ঘরের পুব দিকের দরজা খুলে আমরা বেরিয়ে এলুম। এ-ঘরের পুব আর পশ্চিম, দু’দিকেই দু’টি টানা বারান্দা। এ-দিকের বারান্দার পরেই বাইরের উঠোন। বাইরের এই উঠোনটা অন্দরের উঠোনের চেয়ে অনেক বড়। এরই উত্তরে মন্দির, পুবে রামদাসের ঘর আর দক্ষিণে কাচারি। কাচারি ঘরটাও রামদাসের ঘরের মতোই ছোট আর বড় দু’টি অংশে ভাগ করা। বড়-অংশটা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বাইরের লোকজনেরা সেইখানেই বসেন। ছোট-অংশটায় থাকেন পুরুতঠাকুর। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, পুরুতঠাকুরের থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবার জন্যেই ঘরটার মধ্যে একটা কাঠের পার্টিশান বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
পার্টিশানের ব্যাপারটা অবশ্য আগে বুঝিনি। পুরুতঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যখন তাঁর ঘরে ঢুকি, তখন বুঝেছিলুম। সে-কথায় একটু বাদেই আসব।
বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে নামলুম আমরা। ঠাহর করে দেখলুম, একমাত্র রামদাসের ঘরের মধ্যেই ক্ষীণ একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আর কোনও দিকেই আলোর কোনও চিহ্ন নেই। চতুর্দিকে একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এতটুকু শব্দ কোথাও শোনা যাচ্ছে না। গাছপালাগুলোও একেবারে ছবির মতো স্থির। গাছপালার পাতা নড়লে তারও একটা শব্দ পাওয়া যায়। তাও পেলুম না। অন্ধকারের মধ্যে নড়াচড়া করতে তারাও সম্ভবত ভয় পাচ্ছে।
আকাশের দিকে তাকিয়ে কিন্তু চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন ঝলমলে আকাশ অনেক কাল দেখিনি। কার্ত্তিক মাস। অথচ এতটুকু কুয়াশা নেই। তারাগুলি একেবারে হিরের কুচির মতো ঝকঝক করছে। দু’দিন বাদেই কালীপুজো। চাঁদ ওঠেনি, জোৎস্নার কণামাত্র নেই কোনওখানে। কিন্তু তারই ফলে আজ নক্ষত্রের বাহার আরও বেশি খুলেছে। নক্ষত্র তো নয়, (খন লক্ষ-লক্ষ শমা-চুমকি। আর সেই শমা-চুমকি বসানো নিকষ কালো রঙের শালখানাকে গায়ে জড়িয়ে আকাশটা যেন খলখল করে হাসছে।
টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে বললুম, “দেখেছেন? কলকাতার আকাশে এর অর্ধেক তারাও আমাদের চোখে পড়ে না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা পড়ে না ঠিকই, তবে কিনা একটা চাঁদে যত কাজ হয়, লক্ষ-লক্ষ তারায় তার সিকির-সিকি কাজও হয় না। একশ্চন্দ্রস্তমোহস্তি, চন্দ্রবিহনে পৃথিবী একেবারে অন্ধকার। টর্চটা জ্বালুন মশাই।”
জ্বালবার আগেই অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন আমার কব্জিতে হাত রেখে চাপা গলায় বলল, “এখন জ্বালবেন না। আমি আগে সরে যাই, তারপর জ্বালবেন।”
চমকে গিয়েছিলুম। তার পরেই অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে, লোকটি জগদীশ। আমাদের বারান্দার ঠিক বাইরে, উঠোনে নামবার সিঁড়ির একধারে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।
ভাদুড়িমশাইও চাপা গলায় বললেন, “সারাক্ষণ নজর রাখতে হবে ওই ঘরটার উপরে, মনে আছে তো?”
“আছে বাবু।”
“কেউ যেন ওর ধারেকাছেও যেতে না পারে।”
জগদীশ বলল, “কেউ পারবে না।” বলেই সে হঠাৎ নিঃশব্দে সরে গেল।
তারও খানিক বাদে টর্চ জ্বাললুম আমি।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “জগদীশ যদি ঠিক কথা বলে থাকে তো এদিকটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চলুন, মন্দিরের পুব দিকের রাস্তাটা ধরে একবার ঘুরে আসা যাক।” তারপর বললেন, “সাবধানে পা ফেলবেন। এখনও তেমন শীত পড়েনি, তার উপরে জংলা জায়গা, পথের উপরে সাপখোপ থাকাটা কিছু বিচিত্র নয়।”
“তাতে ভয়ের কী আছে,” হেসে বললুম, “সত্যপ্রকাশ তো বলেই দিয়েছেন যে, মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে মুকুন্দপুরে কাউকে সাপে কাটেনি।”
“তা বলেছেন ঠিকই, তবে কিনা কোটা কার্যকারণ আর কোন্টা সমাপতন, সেটাও বোঝা চাই। আমার তো মনে হয়, সাপে কাউকে না-কাটার সঙ্গে মনসামূর্তি প্রতিষ্ঠার কোনও সম্পর্কই নেই। এটা নেহাতই সমাপতন…অর্থাৎ ইংরেজিতে ওই যাকে বলে কোইনসিডেন্স, সেই রকমের ব্যাপার আর কি।”
“মানে সাদা-বাংলায় কাকতালীয় ঘটনা, কেমন?”
“ঠিক বলেছেন। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে’ বলে একটা প্রবাদ আছে না, এও একেবারে তা-ই।”
“অর্থাৎ সাবধান থাকাই ভাল। কেমন?”
“বিলক্ষণ।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “সাধুবাবার ব্যাপারটা দেখলেন না? মুখে বলছেন মুকুন্দপুরে সাপই নেই, অথচ সাপের ভয়ে নিজে তো একেবারে কাঁটা হয়ে আছেন।”
“সেটা কী করে বুঝলেন?”
“আরে মশাই, সাপের ভয় যদি ওঁর না-ই থাকবে, তো ঘরের চারপাশে কারবলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে রেখেছেন কেন?”
“তাই তো, এটা তো খেয়াল করে দেখিনি।”
ভাদুড়িমশাই যে হাসছেন, অন্ধকারের মধ্যেও সেটা বুঝতে পারা গেল। হাসতে-হাসতেই বললেন, “শুধু এটা কেন, অনেক কিছুই আপনি খেয়াল করে দেখেন না। কী করেই বা দেখবেন, মাটির দিকে তো আর আপনার চোখ নেই, চোখ পড়ে আছে আকাশের নক্ষত্রের দিকে!”
এবারে আমিও হেসে উঠলুম। বললুম “ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন থেকে তা হলে মাটির দিকেই সারাক্ষণ চোখ রাখব।”
“সারাক্ষণ না-রাখলেও এখন অন্তত রাখুন।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “মুখে আওড়ান আস্তিকস্য মুনের্মাতা’র মন্ত্র, কিন্তু পা ফেলুন মাটির দিকে চোখ রেখে। অর্থাৎ সাবধান থাকুন।”
“তা না হয় থাকলুম, কিন্তু ‘আস্তিকস্য মুনের্মাতা টা কী ব্যাপার?”
আবার হেসে উঠলেন ভাদুড়িমশাই। বললেন, “বামুনের ঘরে জন্মেছেন, অথচ সংস্কৃতটাও জানেন না? এ তো বড় লজ্জার কথা মশাই! ‘আস্তিকস্য মুনেমার্তা’র অর্থ হল আস্তিক মুনির মা।”
“তিনি আবার কে?
“তিনি মনসা। ছেলের নাম আস্তিক হল কেন জানেন?”
“নাস্তিক নামটা যেহেতু সুবিধের নয়, সেইজন্যে?”
“আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! তা হলে শুনুন, এই নামটা নিয়েও একটা গপ্পো রয়েছে। মনসার সঙ্গে যে জরৎকারু মুনির বিয়ে হয়েছিল, সে তো আগেই বলেছি। তা মনসা একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন, আমাকে একটি পুত্রসন্তান দাও। স্ত্রীর প্রার্থনার উত্তরে মুনি বললেন, ‘অস্তি।’ অর্থাৎ কিনা ‘তোমার গর্ভেই রয়েছে আমার ছেলে’। বাস্, ওই ‘অস্তি’ থেকেই ছেলের নাম হয়ে গেল আস্তিক। তাবৎ সাপকে মারবার জন্যে রাজা জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করেছিলেন, সে তো জানেন। এই আস্তিকের জন্যেই সাপেরা সেবারে রক্ষে পেয়ে যায়।”
কথা বলতে-বলতে আমরা মন্দিরের উত্তর দিকের বাগানটাকে পাক দিয়ে আবার উঠোনে চলে এসেছিলুম। শুনেছিলুম, বাইরের উঠোনের দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকেন পুরুতঠাকুর। আমাদের ঘর থেকে যখন উঠোনে এসে দাঁড়াই, এদিকে একমাত্র রামদাসদের ঘর ছাড়া আর-কোথাও তখন আলো জ্বলতে দেখিনি। এখন দেখলুম, রামদাসের ঘরটা অন্ধকার, তবে দক্ষিণের ঘরে আলো জ্বলছে।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ভট্ট্চাজমশাই জেগে আছেন মনে হয়। চলুন, একবার দেখা করা যাক।”
যেমন অন্যান্য ঘরের, তেমনি দক্ষিণের এই ঘরের সামনেও কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা টানা বাবান্দা। বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিতে লন্ঠন হাতে নিয়ে ভিতর থেকে যিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন, বুঝতে পারলুম, তিনিই এ-বাড়ির নিত্যপুজার পুরোহিত গোবিন্দ ভট্টাচার্য। একে পুরোহিত, তায় নাম গোবিন্দ, ভেবেছিলুম যে, মানুষটি নিশ্চয় বৃদ্ধ হবেন। এখন দেখলুম, বৃদ্ধ তো ননই, এমনকী প্রৌঢ়ও নন। নেহাতই ছেলেমানুষ। বয়স মেরেকেটে সাতাশ-আঠাশ। পরনে ধুতি আর মলমলের হলুদ ফতুয়া। ফতুয়ার কাপড় পাতলা বলেই বোঝা গেল, যে, তার আড়ালে মোটা একটা পৈতে ঝুলছে। গোবিন্দ ভট্টাচার্যের গায়ের রং টকটকে ফর্সা, মুখখানিও মিষ্টি।
আমাদের দেখেই বললেন, “আসুন, আসুন।”
ঘরটি ছোট। একদিকে একটা সরু তক্তাপোশ। তার সামনে দুটি মোড়া। অন্যদিকের দেওয়ালে মনসার একখানা পট টাঙানো। তার সামনে মেঝের উপরে পশমের একখানি আসন পাতা। আসনের পাশে ধূপদান, কোষাকুষি, একটি শাঁখ, একটি কাঁসর আর পিতলের একটি পঞ্চপ্রদীপ।
আমরা মোড়ায় বসলুম, গোবিন্দ ভট্টাচার্য বসলেন তক্তাপোশের একধারে। ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনার সঙ্গে এই আমাদের প্রথম দেখা হল।”
ভট্চাজমশাই হেসে বললেন, “আন্দ সকালেই হতে পারত। ভেবেছিলুম চৌধুরিমশাই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু পাঠাননি। আমিও তাই যাইনি। উনি না-ডাকলে আমার নিজের থেকে যেতে বড় সঙ্কোচ হয়।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “সে তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে চৌধুরিমশাই আপনাকে ডেকে না-পাঠালেও আপনার কথা আমাদের বলেছেন।”
গোবিন্দ ভট্চাজ বললেন, “কী বলেছেন? ওঁর নিষেধ সত্ত্বেও যে নিত্য আমি আমার ঘরে বসেই পুজো করে যাচ্ছি, সেটা আবার উনি জেনে ফেলেননি তো?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “না না, ও-কথা কেউ তাঁকে বলেনি। কথা হচ্ছিল মূর্তি-চুরির ব্যাপারটা নিয়ে। চৌধুরিমশাই বললেন, একটা শব্দ আপনার কানে গিয়েছিল। লোকজন ছুটে পালাবার শব্দ। তা ছাড়া একটা গাড়ির শব্দও আপনি নাকি শুনেছিলেন। সত্যি?”
আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, চৌধুরিমশাই নন, আজ সকালে এই কথাটা বলেছিল রামদাস। কিন্তু ভাদুড়িমশাই তবু যখন রামদাসের নাম না-করে সত্যপ্রকাশের নাম করলেন, তখন তার একটা কারণ আছে নিশ্চয়। হয়তো তিনি ভাবছেন যে, চৌধুরিমশাইয়ের নাম করলে কথাটা আরও জোর পাবে। যা-ই হোক, ভুলটা আমি আর শুধরে দিলুম না।
গোবিন্দ ভট্ট্চাজ বললেন, “চৌধুরিমশাই ঠিকই বলেছেন। সত্যিই আমি শব্দটা ওনেছিলুম।”
“শুনে আপনার কী মনে হয়েছিল?”
“মনে হয়েছিল, জনাকয় লোক যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।”
“কোনদিকে পালাচ্ছে?”
“মন্দিরের উত্তর দিকে।”
“তার মানে ফলবাগানের দিকে। তাই না?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, বাগানের মধ্যে দিয়েই যেন হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল তারা।”
“আর ওই গাড়ির শব্দ?”
“হ্যাঁ, সেটাও শুনতে পেয়েছিলুম। লোকজন পালাবার শব্দের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুনেছিলুম।”
“তা হলে তো বুঝতে হয় যে, মুর্তিচোরেরা ওই গাড়িতে করেই পালিয়েছে।”
কথাটা বলে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “আপনি এখানে কতদিন হল পুজো করছেন?”
“তা প্রায় বছর তিনেক হল।”
“আপনার আগে এখানে কে পুজো করতেন?”
“আমার বাবা। দু’বছর হল তিনি গত হয়েছে। তবে গত হবার আগে তা প্রায় এক বছর তিনি পুজো করতে পারেননি। করবার সামর্থ্যই তাঁর ছিল না। তখন থেকে আমিই পুজো করে যাচ্ছি।”
“আপনারা কি এদিকের লোক?”
ভট্চাজমশাই বললেন, “না, আমাদের বাড়ি বর্ধমান জেলায়। বাবাকে এঁরাই সেখান থেকে চিঠি লিখে আনিয়ে নিয়েছিলেন। বাবা আবার বছর তিনেক আগে আমাকে আনিয়ে নেন।”
“বর্ধমানে আপনার কে আছেন?”
“দাদারা আছেন, বৌদিরা আছেন, তাঁদের ছেলেপুলেরা আছে।”
“আপনার মা?”
“আমার বয়স যখন মাস ছয়েক, মা তখনই মারা যান। বাবা তার পরের বছরই মুকুন্দপুরে চলে আসেন। আমি মানুষ হয়েছি আমার এক পিসির কাছে।”
“পিসিমা কোথায়?”
“তিনিও বেঁচে নেই।”
আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “এদিকে কেউ নেই আপনার?”
“এক মামাতো দাদা থাকেন হাসিমারায়। তাঁর সেখানে দোকান আছে একটা। আগে তো আমি সেখান থেকেই রোজ যাতায়াত করতুম। কিন্তু তাতে বড় ধকল হয়। চৌধুরিমশাইকে কথাটা বলতে তিনি তাঁর কাচারিঘরটাকে পার্টিশান করে আমাকে বললেন, তুমি তা হলে এখানে থাকো। সেই থেকে এখানেই আছি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “একটা কথা বুঝতে পারছি। সেটা এই যে, যাঁদের বাড়িতে আছেন, তাঁদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাটা আপনি ভাবেন। তা নইলে নিশ্চয় চৌধুরিমশাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও পুজোটা আপনি চালিয়ে যেতেন না।”
গোবিন্দ ভট্ট্চাজ হেসে বললেন, “তাই বলে আবার কথাটা ওকে জানিয়ে দেনে না যেন।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “পাগল! তাই কখনও বলি!”
ভট্চাজমশাইয়ের ঘর থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে আমরা আমাদের ঘরে এসে ঢুকলুম।