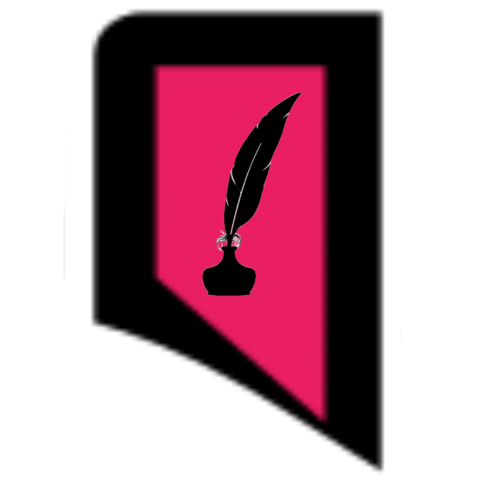মুকুন্দপুরের মনসা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দুই
রবিবারের সকাল। ঘুম থেকে উঠতে-উঠতে বেলা হয়ে গেল। ভাদুড়িমশাই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুতে বলেছিলেন। বাসন্তীই এ-বাড়ির অ্যালার্ম ঘড়ি, তাকে বলেছিলুম, ভোর ছ’টায় যেন আমাকে তুলে দেয়। তা তুলে দেবার চেষ্টা সে নাকি করেছিল, কিন্তু আমিই নাকি উঠিনি। যতবার আমাকে ঠেলাঠেলি করেছে, ততবারই আমি নাকি পাশ ফিরে শুয়ে বলেছি, ঠিক আছে, ঠিক আছে।’ হবেও বা।
এখনও শীত পড়েনি। গরম জলের দরকার হয় না। চটপট দাড়ি কামিয়ে, মাথায় দু মগ জল ঢেলে কাকস্নান সেরে যখন বাথরুম থেকে বার হলুম, রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বাসন্তী তখন জানিয়ে দিল, ‘সাড়ে সাতটা’। এ যখনকার কথা বলছি, ‘সুকুমার সমগ্র’ তখন সদ্য বেরিয়েছে। আর-একজনকে দেব বলে তার প্রথম খন্ড কিনে রেখেছিলুম, কৌশিকের জন্মদিনের উপহার হিসেবে সেটাই একখানা রঙিন কাগজে মুড়ে নিয়ে, গলি থেকে বড়রাস্তায় বেরিয়ে, অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি ধরে যখন যতীন বাগচী রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে কলিং বেল টিপলুম, ঘড়িতে তখন একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আটটা।
মালতীই দরজা খুলে দিল।
চারু ভাদুড়ির ভাই নেই। থাকবার মেধ্যে তিন বোন। তাদের মধ্যে একমাত্র এই ছোটটিকেই আমি চিনতুম। এম. এ. পাশ করে আমাদের কাগজে ট্রেনি হয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু শিক্ষানবিশির পর্ব শেষ করেনি। অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে খবরের কাগজ ছেড়ে দেয়। কাগজে যখন কাজ করত, তখন অবশ্য জানতুম না যে, চারু ভাদুড়ি ওর দাদা। পরে একদিন ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যখন তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ি, আর দোতলার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে মালতী বলে যে, দাদা বাড়িতে নেই, তখন অবাক হয়ে যাই। ভবানীপুরের সেই বাড়িতে থাকতেই মালতীর বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ডাক্তার। শ্বশুরবাড়ি শুনেছিলুম বেহালায়। সে কি আজকের কথা! মালতী অবশ্য তার দাদার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা জানত। কিন্তু কাগজে কাজ করবার সময়ে ঘুণাক্ষরেও তা আমাকে জানায়নি।
দরজা খুলে দিয়ে, একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে মালতী বলল, “আসুন, কিরণদা।”
আমি তো অবাক। মালতী বলল, “কী হল, চিনতে পারছেন না?”
চেনা সত্যিই শক্ত। বেণী-দোলানো ছিপছিপে যে মেয়েটিকে আমি চিনতুম, এ তো সে নয়, রীতিমতো ভারিকে চেহারার এক ভদ্রমহিলা। বললুম, “মা যা হইয়াছেন!”
মালতী বলল, “মা যা হইয়াছেন নয়, মালতী এখন মা হইয়াছেন!” বলে হো হো করে হেসে উঠল। তাতে বুঝলুম, চেহারা পালটেছে বটে, কিন্তু হাসিটা কিছুমাত্র পালটায়নি।
কথা শুনে ভাদুড়িমশাই ইতিমধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, “আরে আসুন, আসুন।” তাঁর সঙ্গেও অনেক বছর বাদে দেখা। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা দেখলুম সেই আগের মতোই রয়েছে। বয়স হয়েছে। অথচ শরীরে কোথাও বাড়তি একটুও মেদ নেই। তেমনি সটান, ঋজু দেহ। তেমনি জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, আর তেমনি তীক্ষ্ণ চাউনি।
ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন ওই চোখ দুটি দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, মানুষটি নেহাত সাধারণ নন, আর পাঁচজন লোকের থেকে একটু আলাদা। সাক্ষাৎটা হয়েছিল বিষাণগড়ে। বি. এ. পাশ করবার পর কিছুদিন স্রেফ বেকার বসে ছিলুম। তারপর বিষাণগড়ের রাজবাড়িতে একটা কাজ পেয়ে যাই। কেয়ার টেকারের কাজ। কাজটা অবশ্য বেশিদিন করিনি। তবে ‘করিনি’ না বলে ‘করা সম্ভব হয়নি’ বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়। সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেন্ট যে পাকা চোর, তা বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আমি বিষাণগড় থেকে পালিয়ে আসি। চুরিটা ধরে ফেলেছিলেন ভাদুড়িমশাই। কিন্তু ধরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এর পরে আর ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় থাকা তাঁর পক্ষে বিশেষ নিরাপদ হবে না। ফলে, চাকরি ছেড়ে তিনিও কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির হয়ে কাজ করতেন। গোটা দুই-তিন রহস্যের কিনারা করে তখন তাঁর খুব নামও হয়েছিল। তবে কলকাতাতেও তিনি বেশিদিন থাকেননি। বড় একটা চাকরির অফার পেয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যান। মাঝেমধ্যে কলকাতায় আসতেন। এলে যোগাযোগও করতেন। তা ছাড়া, বিজয়ার চিঠি লিখতেন নিয়মিত। এবারে তা প্রায় বছর-পাঁচেক বাদে তিনি কলকাতায় এলেন।
ড্রইংরুমে ঢুকে বললুম, “ডাক্তারবাবু কোথায়?”
চারু ভাদুড়ি বললেন, “কে, অরুণ? কল্-এ বেরিয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। …তারপর বলুন খবর কী? সবাই ভাল আছেন তো?”
“বেঁচেবর্তে আছি, এই বাজারে এটাই সবচেয়ে ভাল খবর।”
ট্রে-র উপরে চা আর জলখাবার সাজিয়ে মালতী ইতিমধ্যে ড্রইংরুমে এসে ঢুকেছিল। বলল, “খাবারগুলো ফেলে রাখবেন না। খেতে-খেতে গল্প করুন। একটু বাদে আবার আমি চা দিয়ে যাব।”
গল্প জমে উঠতে দেরি হল না।
কার্তিক মাস। হেমন্তকাল। গরম এখনও কাটেনি, তবে আকাশ ধোঁয়াটে, সকালে আর সন্ধেবেলায় ময়দানে, গঙ্গায় আর লেকের ধারে অল্পস্বল্প কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। বারোয়ারি পুজোর জগঝম্পের ঠেলায় কিছুদিন আগেই সকলের কানের পর্দা ফাটবার জোগাড় হয়েছিল। তারপর লক্ষ্মীপুজোও শেষ হয়েছে। আপাতত কোথাও ঢাকের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে না। পুজোর ছুটির চারটে দিনের সঙ্গে আরও কয়েকটা দিন জুড়ে দিয়ে যাঁরা মারদাঙ্গা করে ট্রেনের টিকিট কেটে বাইরে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার গুটিগুটি এই শহরের খাঁচায় এসে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, আর সেই সঙ্গে ফের শুরু হয়েছে কলকাতাবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ বটে, তবে অফিস-কাছারি বিজয়ার পরেই খুলে গেছে। রাস্তাঘাটে জ্যাম যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়, তবে কিনা পুজোর দিনগুলোর মতো গাড়িগুলো আর ঘন্টার পর ঘন্টা কোথাও নট নড়নচড়ন-নট-কিচ্ছু হয়ে আটকে থাকছে না। অর্থাৎ আবহাওয়া এখন আর সরগরম নয়, মোটামুটি ঠান্ডা।
কালীপুজোর দিন-দুই আগে পর্যন্ত এই ঠান্ডা ভাবটাই বজায় থাকবে বটে, কিন্তু তারপরেই আবার আকাশে হাউই উড়বে, মাথার উপরে আচমকা নেমে আসবে উড়ন-তুবড়ির খোল, ছুঁচোবাজির দাপটে রাস্তাঘাটে সবাইকে একেবারে তটস্থ হয়ে থাকতে হবে, মুহুর্মুহু পটকা, দোদমা আর বোমা ফাটবে, আর শহর জুড়ে চলতে থাকবে শ্যামা-মায়ের চেলাচামুন্ডাদের উদ্দাম নৃত্য।
ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে তাই নিয়ে আক্ষেপ করায় তিনি অবাক হয়ে বললেন, “আরে, এতে এত রেগে যাচ্ছেন কেন?”
“আপনার রাগ হয় না?”
“মোটেই না। আমি তো এই হইচইটা ভীষণ মিস করি কিরণবাবু। ব্যাঙ্গালোরে থাকি, সেখানে সারাটা বছরই যে খুব নিরানন্দে কাটে তা বলব না, আমোদ-আহ্লাদ উৎসব-টুতসবের বিস্তর উপলক্ষ আছে সেখানেও, আলো জ্বলে, মাইক বাজে, সবই হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন মশাই, এই পুজোর সিজনটা এলেই মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। খালি মনে হয়, দুর ছাই, কেন যে দুটো পয়সার লোভে এখানে এলুম, কলকাতায় থাকলেই ভাল হত।”
মালতীর স্বামী অরুণ সান্যাল ইতিমধ্যে রোগী দেখে ফিরেছিলেন। হাসিখুশি মানুষ। বসবার ঘরে ঢুকে স্টেথোস্কোপ আর ব্লাড প্রেশার মাপবার যন্ত্রটাকে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, “তা কলকাতায় থাকলে যে ভাল হয়, সে তো আমরাও বলি। থাকেন না কেন?”
“উপায় নেই রে ভাই,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “যেখানে যার ভাতের থালা, সেখানেই তাকে থাকতে হবে। ভগবান অমার জন্যে ব্যাঙ্গালোরে ভাত বেড়ে রেখেছেন, ফলে সেইখানেই আমাকে থাকতে হয়। তবে কিনা খুব-একটা আনন্দে থাকি না। মনটা বড্ড ছটফট করে।”
বললুম, “এই হুল্লোড়ের জন্যে?”
“সব কিছুর জন্যে। এমন কী, যে ঢাকের বাজনায় এত আপত্তি আপনার, সেই বাজনাটা শুনবার জন্যেও মাঝে-মাঝে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ি, মশাই। আপনি একাই যে অ্যান্টি-ঢাক, তা অবশ্য নয়, দলে হয়তো আপনারাই ভারী, এই তো…মালতীও সেদিন কানে আঙুল দিয়ে বলছিল যে, ঢাকের বাজনা থামলে মিষ্টি, কিন্তু কী জানেন, এই বাজনাটা আমার জীবনে একেবারেই থেমে গেছে তো, তাই এবারে দু’কান ভরে শুনে নিলুম।”
মালতী ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রস্ত চা নিয়ে এসেছিল। ট্রে থেকে তুলে হাতে-হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়ে দিয়ে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “আর হাসিও না, দাদা! এমনভাবে কথা বলছ যে মনে হচ্ছে, ব্যাঙ্গালোর বোধহয় ইউরোপ কি আমেরিকার কোনও শহর। কেন, ব্যাঙ্গালোরে বুঝি ঢাক বাজে না?”
“তা কেন বাজবে না? একশো বার বাজে!” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “কিন্তু তেমন করে বাজে না।”
অরুণবাবু বললেন, “অ্যা, টাকডুম টাকডুম বাজে’ বলে শচীন দেববর্মনের একটা গান আছে না? সেই গানের মধ্যে যেন এই রকমের একটা কথা শুনেছি।”
চারু ভাদুড়ি বললেন, “ঠিকই শুনেছ। তেমন করে বাজে না।”
আমি বললুম, “যার জন্মদিন, তাকে দেখছি না কেন? কৌশিক কোথায়?”
মালতী বলল, “দাদার সঙ্গে জগিং করতে বেরিয়েছিল। এমনিতে তো বাবুর ঘুমই ভাঙতে চায় না। কিন্তু দাদা আসবার পর থেকেই দেখছি ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে উঠে দাদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আজও আমরা মামা-ভাগ্নে ঠিক পাঁচটাতেই উঠেছি। তারপরে মাইল দুয়েক দৌড়েছিও। লেক থেকে ফেরার পথে ও রিক্তাদের বাড়িতে ঢুকল। বলল, রিক্তামাসি ওর জন্যে পায়েস রেঁধে রেখেছে। খেয়ে ফিরবে।
আমি বললুম, “রিক্তা কে মালতী?”
“আমার বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়তুম। ওর ছেলে বুবনু আর কৌশিক তীৰ্থপতিতে একই ক্লাসে পড়ে। দুজনে খুব বন্ধুত্ব। ওদের বাড়িতে গেলে তাই আর আসতেই চায় না। আজ অবশ্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছি।”
বলতে-না-বলতে কৌশিক এসে পড়ল। সুকুমার সমগ্র’ পেয়ে সে দারুণ খুশি। বইয়ের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, “যাই মা, বুবনুকে একবার দেখিয়ে আনি। এক ছুটে যাব আর চলে আসব।”
মালতী বলল, “কিরণদা, আমার মাংস রান্না হয়ে গেছে। একবার এসে একটু টেস্ট করে যান তো আমার কর্তাটি তো কিছুই বোঝেন না, আপনি ঠিক বলতে পারবেন, আর একটা স্টিম লাগবে, নাকি এই ঠিক আছে।”
বলে আমাকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল মালতী। গিয়ে প্রেশার কুকারের ভিতর থেকে হাতায় করে এক টুকরো মাংস তুলে একটা প্লেটে ঢেলে প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “আসলে কিন্তু ঠিক এইজন্যে আপনাকে ডেকে আনিনি, কিরণদা। অন্য একটা কথা আছে।”
অবাক হয়ে বললুম, “কী কথা?”
“অরুণের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাচ্ছে না। মাস খানেক আগে ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলছে, ও নিজেও ডাক্তার, জানে যে, বিশ্রাম নেওয়া দরকার, তবু নেবে না। ভেবেছিলুম, ওকে আর কৌশিককে নিয়ে দাদার সঙ্গে আমিও মাসখানেকের জন্যে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে থাকব। কিন্তু ও রাজি নয়। বলে, ওর রোগীদের মধ্যে দু-তিনজনের অবস্থা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, এই সময়ে ও যদি কলকাতা ছেড়ে বাইরে যায় তো তাদের কী হবে।”
বললুম, “ওর জানাশোনা অন্য কোনও ডাক্তারের হাতে ওদের তুলে দিয়ে গেলেই তো পারে। সেটাই তো রীতি।”
মালতী বলল, “তো সেই কথাটাই ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। দাদা আর আপনি, দু’জনে মিলে যদি বলেন তো আমার মনে হয় আপনাদের কথা ও ফেলতে পারবে না।”
বললুম, “বলব।” তারপর প্লেট থেকে তুলে মাংসের টুকরোটা মুখে ফেলে বললুম, “ঠিক আছে, আর স্টিম দেবার দরকার নেই।”
বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখি, বাংলাদেশের ঢাকের বাজনা থেকে ভাদুড়িমশাই এসে শান্তিপুরী শাড়ির প্রসঙ্গে ঢুকেছেন। শাড়ির থেকে সঙ্গীত। সঙ্গীত থেকে মন্দির-স্থাপত্য। এমনকি, তাতেও নাকি বাঙালির প্রতিভার স্বাক্ষর একেবারে জ্বলজ্বল করছে।
এই শেষ কথাটায় অরুণবাবু আর আমি একটু সংশয় প্রকাশ করেছিলুন। ভাদুড়িমশাই আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, “সত্যিই তা-ই। আরে বাবা, আমি কি কোণার্কের সূর্য-মন্দির দেখিনি? নাকি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ টেম্পল না-দেখেই আমি আমাদের মন্দির-স্থাপত্যের মহিমা কীর্তন করতে বসেছি? শুধু ওই দুটি মন্দির কেন, ভারতবর্ষের হরেক এলাকায় এমন আরও বিস্তর মন্দির রয়েছে, যার উচ্চতা তো বটেই, শিল্পশোভা দেখেও আমাদের তাক লেগে যায়। তা থাক না। আমরা সমতল এলাকার বাসিন্দা, আমাদের এদিকে পাহাড় নেই, তাই পাহাড় কেটে পাথর এনে বড় বড় সব মন্দিরও আমরা বানাতে পারিনি। কিন্তু তাতে হলটা কী? মাটি পুড়িয়ে ইট বানিয়ে তাই দিয়ে যে-সব মন্দির আমরা গড়েছি, তার স্থাপত্যের বাহার কি কারও চেয়ে কিছু কম? আর শিল্প-শৈলীর কথাই যদি তোলেন কিরণবাবু, তো আমি বলব, আমাদের টেরাকোটার মন্দিরের কোনও তুলনাই আমি খুঁজে পাই না। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এবারে যে আমি কলকাতায় এলুম, তাও আসলে একটা মন্দিরের ব্যাপারেই।”
“মন্দিরের ব্যাপারে?” অবাক হয়ে বললুম, “মানত-টানত ছিল নাকি?”
“আরে না, মশাই,” একগাল হেসে চারু ভাদুড়ি বললেন, “মন্দিরের ব্যাপারে মানে তার বিগ্রহের সন্ধানে। তিনশো বছরের পুরনো অষ্টধাতুর বিগ্রহ, হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তিনি উধাও।”
“খোঁজ পেলেন?”
“পেলুম বই কী। কোথায় পেলুম জানেন? স্ট্র্যান্ড রোডের এক গুদামের মধ্যে। সেখান থেকে সেটিকে ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। যদি আর একটা দিনও দেরি হত, তা হলে আর দেখতে হত না, বীরভূমের মন্দিরের বিগ্রহ তা হলে আমস্টার্ডামের মিউজিয়ামের শোভাবর্ধন করত।”
বললুম, “বিগ্রহ চুরির যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে, তাই না?”
“পড়েছেই তো। এই তো, আজকের কাগজটাই দেখুন না। একই দিনে দু’দুটো মন্দির থেকে বিগ্রহ উধাও। একটা খবর আলিপুরদুয়ারের কাছের এক গ্রামের, আর একটা খবর বাঁকুড়ার।”
অরুণবাবু বললেন, “এ তো দেখছি সর্বনেশে কান্ড!”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “সর্বনাশ বলে সর্বনাশ, এককালে এ-দেশ থেকে হিরেমুক্তো যেভাবে লোপাট হয়েছে, এখন সেইভাবে লোপাট হচ্ছে আমাদের প্রত্নদ্রব্য। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, অরুশ, এ-সব মোটেই ছোটখাটো ছিঁচকে চোরের কান্ড নয়, এর পিছনে বড়-বড় সব মাথা রয়েছে। দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে বিদেশে বেচে দিতে তাদের বিবেকে কিছুমাত্র বাধে না। বিদেশিরাও কোটি-কোটি টাকা ঢালছে। তিনশো বছরের পুরনো একটা গণেশমূর্তির জন্যে তারা কত টাকা অফার করেছিল জানেন কিরণবাবু?”
জানা হল না, কেন না তার আগেই কৌশিক এসে বলল, “মামাবাবু, তোমার ফোন, শিলিগুড়ি থেকে কারা যেন কথা বলতে চান। বললেন যে খুব জরুরি।”
ফোনে কথা বলে ড্রইংরুমে ফিরে ভাদুড়িমশাই বেজার গলায় বললেন, “ওই যে একটা কথা আছে না, আমি যাই বঙ্গে তো আমার কপাল যায় সঙ্গে, তা সেই কথাটা একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল। ব্যাঙ্গালোর থেকে বঙ্গে এলুম, কিন্তু কপালের লেখা তো আর খন্ডানো যায় না, একটা তদন্তের কাজ শেষ হতে না হতেই আর-একটা তদন্তের কাজ ঘাড়ে চাপল। ছুটির বারোটা বেজে গেল, মশাই।”
আমি বললুম, “কোথায়? কিসের তদন্ত?”
“ফের সেই বিগ্রহ-চুরির তদন্ত। একটু আগেই আলিপুরদুয়ারের কাছে এক গ্রামের মন্দির থেকে বিগ্রহ উধাও হবার কথা বলছিলুম না? ওই যে মশাই, আজকের কাগজে যার খবর বেরিয়েছে। আসলে ওটা এক ধনী ব্যবসায়ীর পৈতৃক বাড়ির মন্দিরের বিগ্রহ। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে থাকেন না, শিলিগুড়িতে থাকেন। সেখান থেকেই ফোন করেছিলেন। মূর্তিটা উদ্ধার করে দিতে হবে, তা সে যত টাকাই লাগুক।”
“যাবেন?”
‘যেমন কাতর গলায় অনুরোধ জানালেন, তাতে আর ‘না’ বলতে পারলুম না। পরশুর বদলে দিন-সাতেক বাদে মাদ্রাজ গেলে হয় না কিরণবাবু?”
“তা হয়। কিন্তু এ-কথা কেন বলছেন বলুন তো?”
“আপনিও তা হলে আমার সঙ্গে চলুন না। সাত দিন হয়তো লাগবে না, তার অগেই হয়তো ফিরে আসব।”
“কবে যেতে হবে?”
“কালকেই। সকালের ফ্লাইটে।” চারু ভাদুড়ি বললেন, “আপনি রেডি হয়ে থাকবেন, এয়ারপোর্টে যাবার পথে আমি আপনাকে তুলে নেব।”