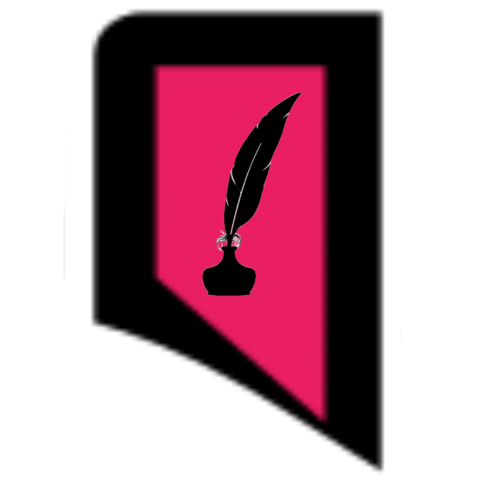নৌকাডুবি (উপন্যাস) – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০৬
বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে এ কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কী মনে হইল?”
বালিকা কহিল, “আমি তো তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নিচু করিয়া ছিলাম।” রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই? বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল–তোমার নাম আমি শুনিই
নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন।
রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখো দেখি।
রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেনসিল দিল। সে বলিল, “তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।”–বলিয়া বড়ো বড়ো অক্ষরে নিজের নাম লিখিল–শ্রীমতী কমলা দেবী।
রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখো।
কমলা লিখিল–শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাও ভুল হইয়াছে?”
রমেশ কহিল, “না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখো দেখি।”
সে লিখিল–ধোবাপুকুর।
এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত আবিষ্কার করিল তাহাতে বড়ো-একটা সুবিধা হইল না।
তাহার পরে রমেশ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি-বা শশুরবাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ। মামার বাড়ি পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়িতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কী গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।
ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানা বর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল।
রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।
কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথম দিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানলায় গিয়া বসিল–সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিসময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, “হাঁগা, হাঁ করিয়া কী দেখিতেছ? বেলা যে অনেক হইল, চান করিবে না?”
ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ি চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল, ‘কমলাকে এখন তো এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না–অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কী করিয়া রাত কাটাইবে?’
.
রাত্রে আহারের পর ঝি চলিয়া গেল। রমেশ কমলাকে তাহার বিছানা দেখাইয়া কহিল, “তুমি শোও, আমার এই বই পড়া হইলে আমি পরে শুইব।”
এই বলিয়া রমেশ একখানা বই খুলিয়া পড়িবার ভান করিল, শ্রান্ত কমলার ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।
সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিল। পররাত্রেও রমেশ কোনো ছলে কমলাকে একলা বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সেদিন বড়ো গরম ছিল। শোবার ঘরের সামনে একটুখানি খোলা ছাদ আছে, সেইখানে একটা শতরঞ্জি পাতিয়া রমেশ শয়ন করিল এবং নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ও হাতপাখার বাতাস খাইতে খাইতে গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।
রাত্রি দুটা-তিনটার সময় আধঘুমে রমেশ অনুভব করিল, সে একলা শুইয়া নয় এবং তাহার পাশে আস্তে আস্তে একটি হাতপাখা চলিতেছে। রমেশ ঘুমের ঘোরে পার্শ্ববর্তিনীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিজড়িতস্বরে কহিল, “সুশীলা, তুমি ঘুমাও, আমাকে পাখা করিতে হইবে না।” অন্ধকারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষপট আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।
ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া উঠিল। দেখিল নিদ্রিত কমলার ডান হাতখানি তাহার কণ্ঠে জড়ানো-সে দিব্য অসংকোচে রমেশের ‘পরে আপন বিশ্বস্ত অধিকার বিস্তার করিয়া তাহার বক্ষে লগ্ন হইয়া আছে। নিদ্রিত বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রমেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এই সংশয়হীন কোমল বাহুপাশ সে কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবে? রাত্রে বালিকা যে কখন এক সময় তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতেছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িল–দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বালিকার বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া রমেশ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।
অনেক চিন্তা করিয়া রমেশ বালিকাবিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে কমলাকে রাখা স্থির করিয়াছে। তাহা হইলে এখনকার মতো অন্তত কিছুকাল সে ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পায়।
রমেশ কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা, তুমি পড়াশুনা করিবে?”
কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।–ভাবটা এই যে, ‘তুমি কী বল?’
রমেশ লেখাপড়ার উপকারিতা ও আনন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কমলা কহিল, “আমাকে পড়াশুনা শেখাও।”
রমেশ কহিল, “তাহা হইলে তোমাকে ইস্কুলে যাইতে হইবে।”
কমলা বিসিমত হইয়া কহিল, “ইস্কুলে? এতবড়ো মেয়ে হইয়া আমি ইস্কুলে যাইব?”
কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তোমার চেয়েও অনেক বড়ো মেয়ে ইস্কুলে যায়।”
কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি-তোহার চেয়ে অনেক বড়ো এবং ছোটো কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, “কোথায় আসিতেছ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।”
কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, “তুমি এখানে থাকিবে না?”
রমেশ। আমি তো এখানে থাকিতে পারি না।
কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চলো।”
রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল, “ছি কমলা!”
এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোটো হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীত মুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।
০৭
এইবার আলিপুরে ওকালতির কাজ শুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিত্ত স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্যারম্ভের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার মতো স্ফূর্তি তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদিঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মনে করিল ‘কিছুদিন পশ্চিমে মিণ করিয়া আসি’, এমন সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।
অন্নদাবাবু লিখিতেছেন, “গেজেটে দেখিলাম, তুমি পাস হইয়াছ–কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোনো সংবাদ পাই নাই। তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে।”
এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির ‘পরে তাঁহার চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনিকন্যার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।
ইতিমধ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্বের ন্যায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্তব্য হইবে কি না, তাহা রমেশ কোনোমতেই স্থির করিতে পারিল না। সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে কথা কাহাকেও বলা সে কর্তব্য বোধ করে না। নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদস্থ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্বের অধিকার লাভ করিবে কী করিয়া?
কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর তো উচিত হয় না। সে লিখিল, “গুরুতর-কারণ-বশত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমাকে মার্জনা করিবেন।” নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।
এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।
একদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় একটি পরিচিত ব্যগ্রকণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল, “বাবা, এই যে রমেশবাবু!”
“গাড়োয়ান, রোখো, রোখো!”
গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়িভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাঁহার কন্যা বাড়ি ফিরিতেছিলেন–এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।
গাড়িতে হেমনলিনীর সেই সিনগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরনের সেই শাড়ি পরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত ভঙ্গি, তাহার হাতের সেই প্লেন বালা এবং তারাকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।
অন্নদাবাবু কহিলেন, “এই-যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল! আজকাল চিঠি লেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি-বা লেখ, তবু ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায়? বিশেষ কোনো কাজ আছে?”
রমেশ কহিল, “না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।”
অন্নদা। তবে চলো, আমাদের ওখানে চা খাইবে চলো।
রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল–সেখানে আর দ্বিধা করিবার স্থান ছিল না।
সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায় সংকোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ভালো আছেন?”
হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কহিল, “আপনি পাস হইয়া আমাদের যে একবার খবর দিলেন না বড়ো?”
রমেশ এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, “আপনিও পাস হইয়াছেন দেখিলাম।”
হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “তবু ভালো, আমাদের খবর রাখেন!”
অন্নদাবাবু কহিলেন, “তুমি এখন বাসা কোথায় করিয়াছ?”
রমেশ কহিল, “দরজিপাড়ায়।”
অন্নদাবাবু কহিলেন, “কেন, কলুটোলায় তোমার সাবেক বাসা তো মন্দ ছিল না।”
উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ কৌতূহলের সহিত রমেশের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল–সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, “হাঁ, সেই বাসাতেই ফিরিব স্থির করিয়াছি।”
তাহার এই বাসা-বদল করার অপরাধ যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ বেশ বুঝিল–সাফাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল। অন্য পক্ষ হইতে আর কোনো প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি কহিয়া উঠিল, “আমার একটি আত্মীয় হেদুয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার জন্য দরজিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।”
.
রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু কথাটা কেমন অসংগত শুনাইল। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলুটোলা হেদুয়া হইতে এতই কি দূর? হেমনলিনীর দুই চক্ষু গাড়ির বাহিরে পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হতভাগ্য রমেশ ইহার পরে কী বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, “যোগেনের খবর কী?” অন্নদাবাবু কহিলেন, “সে আইন-পরীক্ষায় ফেল করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।”
গাড়ি যথাস্থানে পৌঁছিলে পর পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দিল। রমেশের বুকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।
রমেশ কিছু না বলিয়াই চা খাইতে লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এবার তো তুমি অনেকদিন বাড়িতে ছিলে, কাজ ছিল বুঝি?”
রমেশ কহিল, “বাবার মৃত্যু হইয়াছে।”
অন্নদা। অ্যাঁ, বল কী! সে কী কথা! কেমন করিয়া হইল?
রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা করিয়া বাড়ি আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।
একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকসমাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেমনি এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। হেম অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিল, ‘রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম–তিনি পিতৃবিয়োগের শোকে এবং গোলমালে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছিলেন। এখনো হয়তো তাহাই লইয়া উন্মনা হইয়া আছেন। উঁহার সাংসারিক কী সংকট ঘটিয়াছে, উঁহার মনের মধ্যে কী ভার চাপিয়াছে, তাহা কিছুই না জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।’
হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহারে অভিরুচি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল। কহিল, “আপনি বড়ো রোগা হইয়া গেছেন, শরীরের অযত্ন করিবেন না।” অন্নদাবাবুকে কহিল, “বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এইখানেই খাইয়া যান-না।”
অন্নদাবাবু কহিলেন, “বেশ তো।”
এমন সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত। অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছুকাল অক্ষয় একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, “এ কী! এ যে রমেশবাবু! আমি বলি, আমাদের বুঝি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।”
রমেশ কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, “আপনার বাবা আপনাকে যে-রকম তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না–ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছেন তো?”
হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিদ্বারা বিদ্ধ করিল।
অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।”
রমেশ বিবর্ণ মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপর ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের প্রতি মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, “রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নূতন অ্যালবমখানা দেখানো হয় নাই।” বলিয়া অ্যালবম আনিয়া রমেশের টেবিলের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং এক সময়ে আস্তে আস্তে কহিল, “রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নূতন বাসায় একলা থাকেন?”
রমেশ কহিল, “হাঁ।” হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়িতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না। রমেশ কহিল, “না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।” হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি.এ. র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব। রমেশ তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিল।
০৮
রমেশ পূর্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না।
ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসিকৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল।
অনেক কাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্বে হেমনলিনীর চেহারা একপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত–পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয়।
অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা দেখা দিল। তাহার চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমন-কি, অন্যায় মনে করিত। এখন কারো সঙ্গে কোনো তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না।
কর্তব্যবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড়ো কম গভীর ছিল না। বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীর মন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ময় গ্রহতারা চলিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে–রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আয়োজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাকেও আজ এতটা হালকা করিয়া দিল কিসে? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সদুত্তর দিতে না পারিলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুলে এখনো চিরুনি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্বের মতো ময়লা নাই। তাহার দেহে মনে এখনও যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।
০৯
প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে-সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে ভালোবাসার জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহনিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে কত বার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।
রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের সামনে, মুদির দোকানের পাশে, কলুটোলায় ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতেছিল বলিয়া প্রণয়বিকাশ সম্বন্ধে কুঞ্জকুটিরচারীদের চেয়ে তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদাবাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিলটি পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসার মৃগশাবক না হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা চুলকাইয়া দিত–এবং সে যখন ধনুকের মতো পিঠ ফুলাইয়া আলস্যত্যাগপূর্বক গাত্রলেহন দ্বারা প্রসাধনে রত হইত তখন রমেশের মুগ্ধদৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অন্য কোনো চতুষ্পদের চেয়ে ন্যূন বলিয়া প্রতিভাত হইত না।
হেমনলিনী পরীক্ষা পাস করিবার ব্যগ্রতায় সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কিছুদিন হইতে তাহার এক সীবনপটু সখীর কাছে একাগ্রমনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাই-ব্যাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। সাহিত্যে দর্শনে হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দেনাপাওনা চলে–কিন্তু সেলাই-ব্যাপারে রমেশকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, “আজকাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভালো লাগে? যাহাদের সময় কাটাইবার আর কোনো সদুপায় নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভালো।” হেমনলিনী কোনো উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ছুঁচে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষয় তীব্রস্বরে বলে, “যে-সকল কাজ সংসারের কোনো প্রয়োজনে লাগে, রমেশবাবুর বিধানমতে সেসেমস্ত তুচ্ছ। মশায় যত-বড়োই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হোন-না কেন, তুচ্ছকে বাদ দিয়া একদিনও চলে না।” রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসে; হেমনলিনী বাধা দিয়া বলে, “রমেশবাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্য এত ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।” এই বলিয়া সে মাথা নিচু করিয়া ঘর গণিয়া সাবধানে রেশমসূত্র চালাইতে প্রবৃত্ত হয়।
একদিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি ব্লটিং-বহি সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে ‘র’ অক্ষর লেখা আছে, আর-এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই জিনিসটা তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার অন্তরাত্মা বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইল। ব্লটিং-বইটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অক্ষয়ের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই ব্লটিংবেই খুলিয়া তখনি তাহার উপরে একখানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল-
“আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম, কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু লইবার ক্ষমতাও একটা ক্ষমতা। আশাতীত উপহার আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্যামী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না। দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো। ইতি। চিরঋণী।”
.
এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল। তাহার পরে এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর-কোনো কথাই হইল না।
বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে শহুরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে–ওটা আরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী; শহরের বাড়িগুলা তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দা লইয়া বর্ষাকে কেবল নিষেধ করিবার চেষ্টায় ক্লেদাক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। নদী-পর্বত-অরণ্য-প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে। সেইখানেই বর্ষার যথার্থ সমারোহ-সেখানে শ্রাবণে দ্যুলোক-ভূলোকের আনন্দসম্মিলনের মাঝখানে কোনো বিরোধ নাই।
কিন্তু নূতন ভালোবাসায় মানুষকে অরণ্যপর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্তির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুই জনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। বৃষ্টির উপলক্ষে রমেশের আদালতযাত্রার প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। এক-এক দিন সকালে এমনি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, “রমেশবাবু, এ বৃষ্টিতে আপনি বাড়ি যাইবেন কী করিয়া?” রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, “এইটুকু বৈ তো নয়, কোনোরকম করিয়া যাইতে পারিব।” হেমনলিনী বলে, “কেন ভিজিয়া সর্দি করিবেন? এইখানেই খাইয়া যান-না।” সর্দির জন্য উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না, অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোনো লক্ষণও তাহার আত্মীয়বন্ধুরা দেখে নাই; কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত–দুই পা মাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত। কোনোদিন বাদলার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত। বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাট সম্বন্ধে ততটা ছিল না।
এমনি দিন কাটিতে লাগিল। এই আত্মবিসমৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সমাজের আরো পাঁচ জন আলোচনা করিতেছিল। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্তমান মুগ্ধ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরো অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোনো জবাবই পান না।
১০
অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভালো ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত তখন অত্যন্ত কড়া সমজদার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন-কি, আরো গাহিতে অনুরোধ করিত। অন্নদাবাবুর সংগীতে বিশেষ অনুরক্তি ছিল না, কিন্তু সে কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না– তবু তিনি আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, “ঐ তোমাদের দোষ, বেচারা গাহিতে পারে বলিয়াই কি উহার ‘পরে অত্যাচার করিতে হইবে?”
অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত, “না না অন্নদাবাবু, সেজন্য ভাবিবেন না– অত্যাচারটা কাহার ‘পরে হইবে সেইটেই বিচার্য।”
অনুরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, “তবে পরীক্ষা হউক।”
সেদিন অপরাহ্নে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ আসিয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, “অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।”
এই বলিয়া হেমনলিনী হারমোনিয়মে সুর দিল।
অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানি গান ধরিল–
বায়ু বহীঁ পুরবৈঞা, নীদ নহিঁ বিন সৈঞা।
গানের সকল কথার স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় না– কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথায় কথায় বুঝিবার কোনো প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল ঝরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং একজনের জন্য আর-একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।
অক্ষয় সুরের ভাষায় নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল– কিন্তু সে ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর-দুই জনের। দুই জনের হৃদয় সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতেছিল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন মনোরম হইয়া গেল। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মানুষ যত ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত যেন দুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্বচনীয় সুখে দুঃখে আকাঙক্ষায় আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।
সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেমনি হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কেবল অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর-একটা গান, আর-একটা গান।”
উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবাধে উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা সূচিভেদ্য হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল– বেদনাতুর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।
সেদিন অনেক রাত্রে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। হেমনলিনীও চকিতের মতো একবার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।
রমেশ বাড়ি গেল। বৃষ্টি ক্ষণকালমাত্র থামিয়াছিল, আবার ঝুপ্ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিপতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল–
বায়ু বহীঁ পুরবৈঞা, নীদ নহিঁ বিন সৈঞা।
পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, “আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্য অনেক বিদ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।’
কিন্তু কোনো উপায়ে এবং কোনো কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ ভরসা রমেশের ছিল না। সে স্থির করিল, “আমি বাজাইতে শিখিব।” ইতিপূর্বে একদিন নির্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালাখানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল– সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সরস্বতী এমনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালার চর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোটো দেখিয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিল। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া এটুকু বুঝিল যে, আর যাই হোক, এ যন্ত্রের সহিষ্ঞুতা বেহালার চেয়ে বেশি।
পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ি যাইতেই হেমনলিনী রমেশকে কহিল, “আপনার ঘর হইতে কাল যে হারমোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!”
রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে সে একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে ইহাই তাহার ইচ্ছা।
হেমনলিনী কহিল, “ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন। তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন– আমি যতটুকু জানি, সাহায্য করিতে পারিব।”
রমেশ কহিল, “আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে।”
হেমনলিনী কহিল, “আমার যেটুকু বিদ্যা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানোই কোনোমতে চলে।”
ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয় নহে। এমন শিক্ষকের এত অযাচিত সহায়তা সত্ত্বেও সুরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সন্তরণমূঢ় জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্মত্তের মতো হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সংগীতের হাঁটুজলে তেমনিতরো ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্ আঙুল কখন কোথায় গিয়া পড়ে তাহার ঠিকানা নাই– পদে পদে ভুল সুর বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, সুর-বেসুরের মধ্যে সে কোনোপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে রাগরাগিণীকে সর্বত্র লঙ্ঘন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, “ও কী করিতেছেন, ভুল হইল যে–” অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাকৃত করিয়া দেয়। গম্ভীরপ্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তা-তৈরির স্টীমরোলার যেমন মন্থরগমনে চলিতে থাকে, তাহার তলায় কী যে দলিতপিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বরলিপি এবং হারমোনিয়মের চাবিগুলার উপর দিয়া রমেশ সেইরূপ অনিবার্য অন্ধতার সহিত বার বার যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।
রমেশের এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, রমেশও হাসে। রমেশের ভুল করিবার অসাধারণ শক্তিতে হেমনলিনীর অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেসুর হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালোবাসারই আছে। শিশু চলিতে আরম্ভ করিয়া বার বার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতার স্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠে। বাজনা সম্বন্ধে রমেশ যে অদ্ভুত রকমের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, হেমনলিনীর এই এক বড়ো কৌতুক।
রমেশ এক-এক বার বলে, “আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্রথম বাজাইতে শিখিতেছিলেন তখন ভুল করেন নাই?”
হেমনলিনী বলে, “ভুল নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু সত্যি বলিতেছি রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।”
রমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে শুরু করিত। অন্নদাবাবু সংগীতের ভালোমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি এক-এক বার গম্ভীর হইয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন, “তাই তো, রমেশের ক্রমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।”
হেমনলিনী বলিত, “হাত বেসুরায় পাকিতেছে।”
অন্নদা। না না, প্রথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার তো বোধ হয়, রমেশ যদি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গানবাজনায় আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস করা চাই। একবার সারেগামার বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।
এ-সকল কথার উপরে প্রতিবাদ চলে না। সকলকে নিরুত্তর হইয়া শুনিতে হয়।