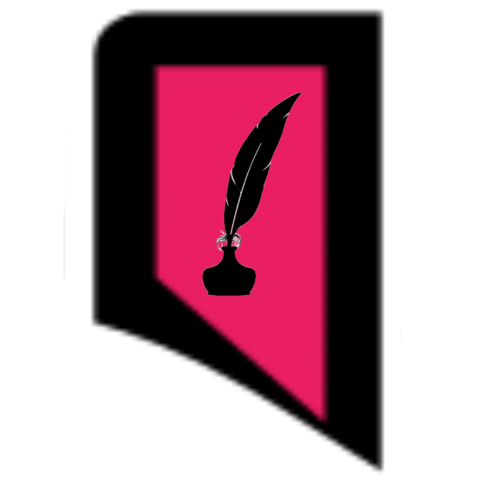মুকুন্দপুরের মনসা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
সাতাশ
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সাড়ে আটটা। জিজ্ঞেস করলুম, “ভাদুড়িমশাই কতক্ষণে শিলিগুড়ি পৌঁছবেন বলে মনে হয়?”
সত্যপ্রকাশ হারলেন। বললেন, “সেটা নির্ভর করছে কী স্পিডে উনি গাড়ি চালাবেন, তার উপরে।”
“আমাদের সেদিন শিলিগুড়ি থেকে মুকুন্দপুরে পৌঁছতে কতক্ষণ লেগেছিল?”
“সেদিন মানে পরশুর কথা বলছেন?”
“হ্যাঁ।”
“তিন ঘন্টা। আমার সাধারণত তিন ঘন্টাই লাগে। অবশ্য এখানে-ওখানে এক-আধবার আমাকে থামতে হয়। সেদিন যেমন ময়নাগুড়িতে থেমেছিলুম।”
“সেদিন আপনি যে-স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, ভাদুড়িমশাই মোটামুটি সেই স্পিডেই চালান। তবে পথের মধ্যে উনি কোথাও থামবেন বলে মনে হয় না।”
“নন-স্টপ চালালে আড়াই ঘন্টার বেশি লাগবার কথা নয়। অর্থাৎ কিনা এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। কেন যাচ্ছেন, কিছু বুঝতে পারলেন?”
“না। যাবার ব্যাপারে যা বললেন, সে তো আপনিও শুনেছেন।”
“হ্যাঁ। কিন্তু তার থেকে তো স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না।” খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন সত্যপ্রকাশ। তারপর বললেন, “উনি বোধহয় সন্দেহ করছেন যে, শিলিগুড়ি দিযে মূর্তিটা পাচার করা হয়েছে। বর্ডারের কথাটা বোধহয় সেইজন্যেই বললেন। তাই না?”
“বর্ডার তো এদিক থেকেও দূরে নয়।” আমি বললুম, “ওদিক থেকে নেপালের বর্ডার কাছে পড়ে, এদিক থেকে ভুটানের বর্ডার। মূর্তি যদি পাচার হয়েই থাকে, তবে যে তা নেপালের বর্ডার দিয়েই হয়েছে, এমন কথা তো জোর করে বলবার উপায় নেই।”
কথাটা সত্যপ্রকাশের পছন্দ হয়েছে বলে মনে হল। সম্ভবত সেই কারণেই বলেন, “তা হলে তো ভূটানের বর্ডারের কথাই ওঁর আগে ভাবা উচিত ছিল।”
তার বদলে ভাদুড়িমশাই কেন শিলিগুড়ির দিকে ছুটলেন, স্পষ্ট করে সেটা না-বুঝলেও একটা কারণ অবশ্য আমি অনুমান করতে পারছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল, আসলে তিনি সম্পৎলালকে সন্দেহ করছেন। লোকটা যে কুখ্যাত স্মাগলার, ভাদুড়িমশাই সেটা জানেন। সুতরাং মুর্তি-চুরির ব্যাপারে সম্পৎলালকে সন্দেহ করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বরং সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।
কিন্তু চুরিটা সে কীভাবে করল? হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিয়ে গেল আমার মনের মধ্যে। গোবিন্দ ভট্চাজ শুধু চোর পালানোর শব্দ নয়, শেষ রাত্তিরে একটা গাড়ির আওয়াজও শুনতে পেয়েছিলেন। তা হলে কি সে-গাড়ি সম্পৎলালেরই? সে নিজে হয়তো আসেনি। কিন্তু যারা এসেছিল, তারা তারই দলের লোক। মুর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে তারা নিশ্চয় সম্পৎলানের হাতে তুলে দিয়েছে। আর তা যদি দিয়ে থাকে, তা হলে শিলিগুড়ি থেকে সে-মূর্তি নেপালে পাচার করা তো তার পক্ষে আদৌ শক্ত হবার কথা নয়।
তার পরেও অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটা আর কিছুই নয়, সম্পৎলাল এই মূর্তির কথা জানল কী করে? সে তো শিলিগুড়িতে লেবার কনট্রাক্টের কাজ করে। থাকে শিলিগুড়িতেই। এখানকার এই প্রাচীন মনসামূর্তির কথা তা হলে সে কার কাছে শুনল? তবে কি সত্যপ্রকাশই…
উত্তেজনায় যেন বুকের মধ্যে টিপ-টিপ করছিল আমার। সম্পৎলালের সঙ্গে সত্যপ্রকাশের যোগাযোগের ব্যাপারটা তা হলে এইজন্যেই ভাদুড়িমশাইয়ের ভাল লাগেনি। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন যে, নিজের হাতে সরাবার সাহস হয়নি বলে সম্পৎলালের সাহায্যে মুর্তিটিকে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করেছেন সত্যপ্রকাশ। সম্পৎলাল তাঁর কাছে প্রচুর টাকা পায়, অথচ ব্যাঙ্ক-লোনের ব্যবস্থা না-হওয়া টাকাটা সত্যপ্রকাশ দিতে পারছেন না। অগত্যা তাঁকে ভাবতে হয়েছে মনসামূর্তি বিক্রি করে টাকা তুলবার কথা। শাঁসালো কোনও বিদেশি খদ্দেরের কাছে যদি বেচতে পারেন তা হলে ওই মূর্তির যে দাম মিলবে, তাতে সম্পৎলালের পাওনা মেটাবার ব্যবস্থা তো হবেই, উদ্বৃত্ত হিসেবে তাঁর নিজের হাতেও নেহাত কম টাকা আসবে না। ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়, তা হলে এই যে মুর্তি-চুরির ব্যাপারটা নিয়ে থানায় ডায়েরি করেছেন সত্যপ্রকাশ, আর তার উপরে আবার ভাদুড়িমশাইকেও কলকাতা থেকে এখানে আনিয়েছেন, এ তো নেহাতই লোক-দেখানো ব্যাপার।
আমার মনে হচ্ছিল, ভাদুড়িমশাই ঠিকই সন্দেহ করেছেন। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি নিশ্চয় ভাবছেন যে, মুর্তিটি হয়তো এখনও নেপালে পাচার হয়নি, হয়তো সম্পৎলালের কাছেই সেটা আছে এখনও। সম্ভবত সেইজন্যেই এমন তাড়াহুড়ো করে তিনি শিলিগুড়ি চলে গেলেন।
কিন্তু গ্রামের সেই চাষিবউটি? তার তা হলে কী ব্যাপার? রঙ্গনাথ যে তাকে বললেন ‘…যেখান থেকে নিয়ে এসেছ, সেইখানেই আবার রেখে এসো’, ও-কথার তাৎপর্য তা হলে কী?
আবার যেন সব জট পাকিয়ে যেতে লাগল। একটু আগেই ভাবছিলুম যে অন্ধকারের মধ্যে যেন এখানে-ওখানে গোটাকয় আলো জ্বলে উঠছে। কিন্তু এখন আবার সব অন্ধকার।
“কী ভাবছেন এত?”
সত্যপ্রকাশের কথায় আমি চমকে উঠলুম। বললুম, “না, তেমন-কিছু না।”
“আর-এক রাউন্ড চায়ের কথা বলি?”
“চা?…ও হ্যাঁ, আর-এক কাপ হলে তো ভালই।”
“তা হলে চলুন ড্রইং রুমে গিয়ে বসা যাক, চা ওখানেই দিয়ে আসবে।”
খাবার ঘর থেকে সত্যপ্রকাশের বসবার ঘরে চলে এলুম আমরা।
আগেই বলেছি, অন্দরের উঠোনের উত্তর-দিকের এই ঘরটা দোতলা। উপরে সত্যপ্রকাশের শোবার ঘর আর নীচে তাঁর বসবার ব্যবস্থা। উপরটা এখনও দেখিনি, নীচতলাটা বেশ সাজানো-গোছানো। ঘরের উত্তর-দিকটায় দেওয়াল-বরাবর বুক-সমান উঁচু করে টানা হয়েছে বই রাখবার জন্যে কাচের পাল্লা-বসানো টানা-র্যাক। পশ্চিম-দিকে, ঘরের ভিতর থেকেই, একটা পালিশ-করা কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। তার উল্টো-দিকে পুরু গালচের চার পশে সাজানো সোফা-সেটি। একপাশে একটা ডিভান। আর এক পাশে একটা ছোট রাইটিং টেবিল আর হালকা একটা চেয়ার। এই রাইটিং টেবিলের দেরাজ থেকেই পরশু রাত্তিরে মনসা-মূর্তির ফোটোগ্রাফ বার করে সত্যপ্রকাশ আমাদের দেখিয়েছিলেন।
যে-সোফাটায় আমি বসে ছিলুম, সেখান থেকে পুব-দিকের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই মন্দিরের চুড়োটা আমার চোখে পড়ল। উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালুম আমি। মন্দির আর এই ঘরের মাঝখানে একটা বড়সড় চত্বর। চত্বরটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। তার মাঝখানে ইঁদারা। এরই জলের গুণের কথা সত্যপ্রকাশ খুব গর্ব করে বলেছিলেন।
চত্বরের উত্তরে ফলের বাগান। বাগান যেখানে শুরু হয়েছে, তার এদিকে পাশাপাশি দুটি উঁচু গাছ যেন থামের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার পত্রপল্লব সারাক্ষণ ছায়া বিস্তার করে রেখেছে চত্বরটির উপরে। দেখে মনে হয়, গাছ দুটি যেন গোটা জায়গাটার উপরে দুটো ছাতা ধরে আছে।
এই ধরনের গাছ এ-গ্রামে আরও অনেক দেখেছি, কিন্তু কীসের গাছ তা জানি না। সত্যপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, “এ হল মুচুকুন্দ চাঁপা। এখানে এ-গাছ বিস্তর দেখবেন। কেন, কলকাতায় এ-গাছ চোখে পড়েনি?”
বললুম, “পড়েছে বলে মনে হয় না।”
সত্যপ্রকাশ হেসে বললেন, “আমার কিন্তু পড়েছে। আমরা তো কলকাতার লোক নই, কাজেকর্মে মাঝেমধ্যে কলকাতায় যেতে হয়, তাও চোখে পড়েছে।”
“কোথায়?”
“টালা পার্কের ওদিকে গেছেন কখনও?”
“মাঝেমধ্যেই তো যাই। কেন, ওদিকে এ-গাছ আছে নাকি?”
“টালা পার্কের উত্তরের দিকটায় বেশ কয়েকটা আছে। অন্তত বছর পাঁচেক আগেও ছিল। সিক্সটি সেভেন… না না, সিক্সটি এইটে একবার কলকাতায় গিয়ে মণীন্দ্র রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে দিন তিনেক ছিলুম। রোজ সকালে তখন টালা পার্কে বেড়াতে যেতুম। মনে আছে, চাঁপার গন্ধে বাতাস যেন ভারী হয়ে থাকত। আর ওই গন্ধ আমাকে মনে পড়িয়ে দিত মুকুন্দপুরের কথা। একটা মজার কথা কী জানেন?”
“কী?”
“আমাদের এই গ্রামের নামও আসলে মুচুকুন্দপুর। সরকারি নাথিপত্রে আর ডাকঘরের ছাপেও দেখবেন মুকুন্দপুরের কোনও উল্লেখই নেই। সর্বত্র মুচুকুন্দ।”
“লোকে তা হলে মুকুন্দপুর বলে কেন?”
“বলে, তার কারণ, মুখে-মুখে অনেক কাল ধরে মুকুন্দপুর নামটাই চালু হয়ে গেছে। মুকুন্দ মানে তো বিষ্ণু, নারায়ণ। তা এখানে কোনও বিষ্ণুমন্দির দেখলেন?”
“কই, দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।”
“থাকলে তো দেখবেন। মুকুন্দর নামে গ্রামের নাম হলে একটা বিষ্ণুমন্দিরও এখানে থাকত। কিন্তু তা তো আর হয়নি। গ্রামের নাম হয়েছে গাছ থেকে। যেমন অনেক জায়গাতেই হয়। কলকাতাতেও তালতলা, বেলতলা, নেবুতলা, এইসব আছে না? সবই গাছের নামে নাম। এও তেমনি। মুচুকুন্দ ফুলের গাছ থেকে মুচুকুন্দপুর। আবার সেই মুচুকুন্দপুর থেকে লোকের মুখে-মুখে মুকুন্দপুর।”
ভাবলুম, ভাদুড়িমশাই ফিরলে এটা তাঁকে বলতে হবে। অনেক-কিছুই তিনি জানে। বটে, কিন্তু এটা নিশ্চয় জানেন না।
গোপালের মা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। সেন্টার টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল, “মাস্টারমশাই এসেছেন, দাদাবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে এখানে নিয়ে আসব?”
সত্যপ্রকাশ বললেন, “বেশ তো, এখানেই নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, পটে ক’কাপ চা দিয়েছ?”
“চার কাপের মতন হবে।”
“ঠিক আছে, তা হলে আর চা দেবার দরকার নেই। শুধু আর-একটা কাপ দিয়ে যাও। এতেই আমাদের তিনজনের হয়ে যাবে।”
গোপালের মা কুণ্ঠিত গলায় বলল, “বলেন তো আর এক পট চi দিয়ে যাচ্ছি।”
সত্যপ্রকাশ বললেন, “দরকার হবে না। যাও, মাস্টারমশাইকে নিয়ে এসো।”
মাস্টারমশাইকে ডাকবার আগে গোপালের মা এসে আর-এক জোড়া কাপ-প্লেট রেখে গেল। তার একটু পরেই মাস্টারমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন।
তাঁর বসবার জন্যে আমার পাশের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে সত্যপ্রকাশ বললেন, “কী খবর মাস্টারমশাই? আর-কোনও গন্ডগোল নেই তো?”
মাস্টারমশাই বললেন, “একেবারে যে নেই, তা নয়। বুড়োরা আমাকে মান্যি করে, হুট করে আমার কথাটা তারা কেউ ফেলবে বলে মনে হয় না। তবে ছোকরাদের রক্ত গরম, তারা বেজায় খেপে আছে। তার উপরে আবার খুড়োমশাইটিও বড্ড অবুঝ। এত করে তাঁকে বললুম যে, এইভাবে মা-মনসার নিন্দেমন্দ করাটা তাঁর ঠিক হচ্ছে না, তবু কাল সন্ধেবেলায় রথতলায় গিয়ে একগাদা লোকের সামনে তিনি জাঁক করে একটা বিচ্ছিরি কথা বলে বসলেন।”
“কী বললেন?”
“বললেন যে, তিনি মন্তর দিয়ে ব্যাংখেকো কানিটাকে ভ্যানিশ করিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যিস আমি সেখানে ছিলুম। নইলে সেখানেই একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হতে যেত।।ন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে সত্য? একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।”
মাস্টারমশাই একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “ব্যবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই ভাল।”
সত্যপ্রকাশ বললেন, “কী যে করব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। উনি আমার কাকা হন। যতই অন্যায় করুন, সম্পর্কে গুরুজন, ওঁকে কোনও কড়া কথা বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”
“বেশ তো, কড়া কথা বলবার দরকার নেই। কিন্তু বুঝিয়ে তো বলতে পারো যে, এখান থেকে এবারে ওঁর চলে যাবার সময় হয়েছে। না-গেলে যে ওঁরই বিপদ ঘটতে পারে, সেটাই বা বুঝিয়ে বলতে বাধা কোথায়?”
সত্যপ্রকাশ বললেন, “ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি।”
ভদ্রলোককে এমন অসহায় দেখাচ্ছিল যে, একটু মায়া বোধ না-করে পারলুম না।
চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন। আমিও বললুম, “আপনি বিশ্রাম করুন মিঃ চৌধুরি। খাওয়ার সময়ে আবার দেখা হবে।”
বলে নিজের ঘরে চলে এসে একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। শুয়েই মনে পড়ল, সত্যপ্রকাশের ঠাকুর্দার ডায়েরিটা তো এই ঘরেই রয়েছে। এই ফাঁকে সেটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে ডায়েরিটা বার করে আনলুম আমি।