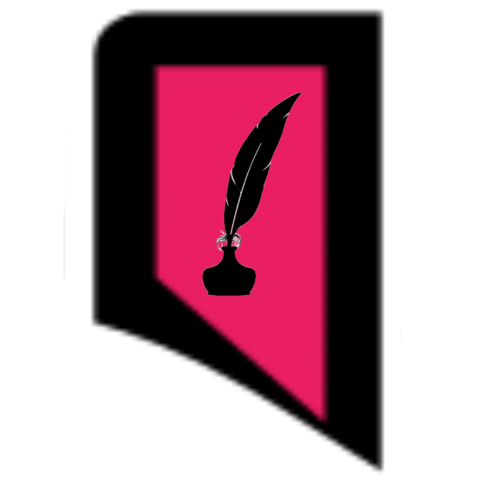মুকুন্দপুরের মনসা (ভাদুড়ি) – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
এগার
কাল রাত্তিরে যখন আমরা শিলিগুড়ি থেকে মুকুন্দপুরে এসে পৌঁছই, অন্ধকারের মধ্যে তখন .কানও কিছু খুব ভাল করে দেখতে পাইনি। অন্ধকার অবশ্য এখনও পুরোপুরি কাটেনি, পুবের আকাশে সদ্য খানিকটা রক্তের ছোপ লেগেছে মাত্র। কিন্তু যে মন্দিরটির সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, তার গঠনশৈলী যে কত সুন্দর, সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তের এই কোমল আলোটুকুই তা যেন আরও স্পষ্ট করে আমাদের বুঝিয়ে দিল।
মনসাদেবীর মূর্তিটি যতই প্রাচীন হোক, তাঁর এই মন্দির যে মোটেই পুরনো নয়, তা আমরা জানি। কতই বা বয়স হবে এর? মহেশ্বর চৌধুরি এখানে এসেইছিলেন তো ১৮৯১ সালে, আর এসেই নিশ্চয়ই এই মন্দির তোলেননি, সত্যপ্রকাশের কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় মন্দির তুলবার মতো অবস্থাই তখন তাঁর ছিল না। যদি ধরে নিই যে, অবস্থা ফিরতে তা অন্তত বছর কুড়ি লেগেছিল, তো বুঝতে হবে ১৯১০ সালের আগে এ-মন্দির তৈরি হয়নি, সম্ভবত তারও পাঁচ-দশ বছর পরে তৈরি হয়ে থাকবে।
চারু ভাদুড়ি বললেন, “এ যে তাক-লাগানো ব্যাপার মশাই!”
আমি বললুম, “যা বলেছেন। মন্দিরটি যে এত সুন্দর তা তো ভাবতেই পারিনি।”
“আমিও না। তবে কী জানেন,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “এমন এক-একটা ব্যাপার দেখছি মাঝে-মাঝেই ঘটে যায়! যেখানে যেটা দেখব বলে কল্পনাও করিনি, সেখানে হঠাৎ—বলা নেই কওয়া নেই—ঠিক সেটাই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গত মাসের গোড়ার দিকে একবার পুনে যেতে হয়েছিল…ওই আর কী, ব্ল্যাকমেলের একটা নোংরা কেস, সেই সূত্রেই যাওয়া…তা সেখানে একটা মস্ত সারপ্রাইজ।”
“কী দেখলেন?”
“সেও একটা মন্দির। শহরতলি এলাকায় ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। শহরতলি বলে যেন আবার ভাববেন না যে খুব খোলামেলা জায়গা; যেমন সব বড়-বড় শহর, তেমনি তাদের আউটস্কার্টগুলোও আজকাল সমান ঘিঞ্জি, ঘ্যাচবক্স-আর্কিটেকচারের দশতলা-বারোতলা সব পেল্লায়-পেল্লায় বাড়ি সেখানেও আকছার আজকাল চোখে পড়বে…তা তারই মধ্যেই হঠাৎ এককালি জমির উপর এই মন্দির দেখে তো আমি তাজ্জব। ছোট্ট মন্দির, কিন্তু কী যে সুন্দর মন্দির, সে আর কী বলব। যেমন চমৎকার তার গড়ন, তেমনি তার দেয়ালের আর পিলারের কাজ। চারদিকের ওইসব মনস্ট্রসিটির মধ্যে যে অমন একটা মন্দির থাকতে পারে, তা আমি কল্পনাও করিনি।”
“কার মন্দির?”
“লক্ষ্মী-ঠাকরুনের।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “বালাজি বিশ্বনাথের কথা মনে আছে তো?”
“পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ?”
“আরে হ্যাঁ মশাই, ওই যিনি শিবাজির নাতি শাহুর মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে তাঁর এক জমিদার-বন্ধু নাকি এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। শিবের ভক্ত হয়ে তিনি হঠাৎ লক্ষ্মীর মন্দির তৈরি করাতে বললেন কেন, তাই নিয়ে একটা গল্প শুনলুম।”
গল্পটা শোনা হল না। ঘুম থেকে উঠবার পরে কেন যে অস্বস্তি বোধ করছিলুম, এতক্ষণে সেটা মনে পড়েছে। বললুম, “শিবের ভক্ত কেন লক্ষ্মীর মন্দির তৈরি করাতে বললেন, সেটা কোনও প্রশ্ন নয়, তার কারণ শিবের যিনি ভক্ত, লক্ষ্মীর ভক্ত হতেও তার কিছুমাত্র বাধা নেই, লক্ষ্মী তো শিবেরই মেয়ে। আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, যাঁরা শিবের ভক্ত, তাঁরা মনসার উপরে খাপ্পা কি না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “সব ভক্তই খাপ্পা কি না, তা আমার জানা নেই, তবে একজন খুবই খাপ্পা ছিলেন। বুঝতেই পারছেন, শিবের সেই ভক্তটি হচ্ছেন চাঁদ সদাগর। তাঁর কাছ থেকে পুজো আদায় করবার জন্যে মনসা কী না করেছেন! তাঁর নৌকো ডুবিয়েছেন, তাঁকে একেবারে পথের ভিখিরি বানিয়ে ছেড়েছেন, এমনকী বাপকে শায়েস্তা করবার জন্যে ছেলের প্রাণ সংহার করতেও ছাড়েননি। কিন্তু চাঁদের তবু ধনুর্ভঙ্গ পণ, কিছুতেই তিনি মনসার পুজো করবেন না। ‘মনসামঙ্গল’ পড়েছেন তো, সেখানে চাঁদ বলছেন, ‘যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর-ভবানী সেই হাতে পুজিব কি চ্যাংমুড়ি কানি?” আরে ছিছি, একটা কানিকে তিনি পুজো করবেন? কভি নেহি!”
“মনসাকে তিনি কানি বলছেন কেন?”
“বলছেন এইজন্য যে, চাঁদের কাছে মনসা তা মোটেই দেবী নন, নেহাতই সাপ!”
“বেশ তো তা-ই না হয় হলেন, কিন্তু সাপকেই বা কানি বলবার মানে কী? সাপেরও তো দু’দুটো চোখ রয়েছে।”
“ও, আপনি জানেন না বুঝি?” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “দু’দুটো চোখ আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা যেমন কোনও কিছু দেখবার সময়ে দু’দুটো চোখকে একইসঙ্গে কাজে লাগাই, সাপ তা পারে না। সাপ যা-কিছু দেখুক, একচোখে দেখে। কখনও বাঁ চোখে দেখে কখনও ডান চোখে। একই সঙ্গে দু’ চোখে দেখে না। চাঁদ সদাগর যে মনসাকে কানি বলে গাল দিয়েছেন, সেটা এই জন্যেই।”
“বুঝলুম। কিন্তু একা চাঁদ সদাগরই যে কেন মনসার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েছিলেন, সেইটে বুঝতে পারছি না। পুরনো আমলের গল্পে কি কবিতায় ঠিক এই রকমের আর-কোনও চরিত্রের কি উল্লেখ আছে?”
“থাকতে পারে, আমি জানি না।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু ও-সব কথা থাক, মন্দিরটি ভাল করে দেখে নিন।”
এ-শড়িতে শুধু এই মন্দিরটিই টাকা। দেওয়াল যেমন ইটের, তেমনি ছা হও ঢালাই। ছাতের উপরে ঢালা;-করা চুড়ো। দেওয়াল জুড়ে পোড়ামাটির কাজ।
সূর্য উঠেছে। মন্দিরের গায়ে এসে পড়েছে তার প্রথম রশ্মি। সবকিছুই এখন পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “দেখুন দেখুন, একটু আগেই তো চাঁদসদাগরের কথা হচ্ছিল, মনসার সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ, তারই কাহিনির নানান ঘটনাকে কী চমৎকারভাবে এখানে এই পোড়ামাটির কাজের মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে।”
মন্দিরটি বড় নয়, ছোট। দেওয়ালগুলোও অপরিসর। পোড়ামাটির স্ল্যাব বসাবার জন্যেও তাই ঢালাও জায়গা ছাড়া যায়নি। অথচ তারই মধ্যে দেখলুম বিস্তর ঘটনাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছদ্মবেশে মনসার পুজো নেওয়া, জাহাজডুবি, লখিন্দরের বিয়ে, লোহার বাসরে সর্পদংশন, সমীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলার স্বর্গযাত্রা, লখিন্দরের আবার বেঁচে ওঠা, আর সর্বশেষে মনসার পূজায় চাঁদের সম্মাত, এই বড়-বড় ঘটনাগুলো তো আছেই, অনেক ছোটখাটো ঘটনাও বাদ পড়েনি।
পোড়ামাটির কাজগুলো কে করেছেন তা জানি না, তবে কিনা যিনিই করে থাকুন, তিনি যে একজন উঁচু ধবের শিল্পী তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য যাঁরা বাঁশবেড়ের প্রাচীন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ দেখেছেন, তাঁরা হয়তো বলবেন, এ আর এমন কী। তা বলুন, কিন্তু আমার তো মনে হল, ইনি নেহাত কম যান না।
ভাদুড়িমশাইকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, “অন্যান্য কাজও পাকা হাতের। যেমন মেঝের পাথরের কাজ, তেমনি পিলারের মোজাইক। চাঁদোয়ায় ঢাকা পড়েছে বলে সিলিংয়ের পঙ্কের কাজ অবশ্য সবটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতেই বুঝতে পারছি যে, এই মন্দিরের জন্যে একেবারে এ-ওয়ান সব লোককে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। পয়সা ঢালবার ব্যাপারে দেখছি মহেশ্বর চৌধুরি কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি।”
মন্দিরের বারান্দার অংশ গি দিয়ে ঘেরা বটে, তবে বন্ধ নয়। জুতো খুলে বারান্দায় উঠে আমরা মেঝে, সিলিং, পিলার, পোড়ামাটির কাজ ইত্যাদির উপরে চোখ বুলিয়ে আবার উঠোনে নেমে এলুম। ভিতরের ঘরটা বন্ধ। দরজায় তা। ঝুলছে। তাই ভিতরে কী আছে, বোঝা গেল না। মূর্তিটি যে নেই, তা অবশ্য আমরা জানি।
এ-বাড়িতে ইতিমধ্যে কাজের লোকজনেরা আসতে শুরু করেছে। রাত্তিরে যে ঘরে ছিলুম, সেই ঘরটাই দু’দিকে ভাগ করে রেখেছে ভিতরের উঠোন আর বাইরের উঠোনকে। ভিতরের উঠোন থেকে সেটা পুবদিকের ঘর, আবার বাইরের উঠোন থেকে পশ্চিম দিকের। বাইরের উঠোনের উত্তরে এই মন্দির। পুবে আর দক্ষিণে দুটি ঘর রয়েছে। পূবের ঘরে থাকে রামদাস আর দক্ষিণের ঘরে পুরোহিত গোবিন্দ ভট্টাচার্য।
পুবের ঘর থেকে রামদাস বেরিয়ে এল। আমরা তার আগেই উঠে পড়েছি দেখে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে এসে বলল, “বাবুরা কি অনেক আগেই উঠেছেন?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “এই তো খানিক আগে উঠলুম, বেশিক্ষণ হয়নি। তা তোমার নাতনির খবর কী?”
“ওই একইরকম বাবু। কাউকে চিনতে পারছে না, কথাও বলছে না।
“ওকে দেখছেন কে?”
“হাসিমারার ডাক্তারবাবু। রোজ বিকেলে এসে দেখে যান। আজও আসবেন। …আপনাদের চা কি ঘরে দেব? বলেন তো এখানেই এনে দিই।”
“এক্ষুনি চা খাব না। চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে আসি। ফিরে এসে চা খাব।”
মন্দিরের উত্তরে ফলের বাগান। ভেবেছিলুম বাগানের ভিতর দিয়ে ওদিকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না।
বাগানটি অবশ্য এমনিতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যাকে আন্ডারগ্রোথ বলে, বড়-বড় গাছের তলায় সেই ঘাস আর আগাছার জঙ্গল একেবারে নেই বললেই হয়। দেখলেই বোঝা যায় যে, বাগানের দেখাশোনা করবার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে, হয় সে নিজেই এর পিছনে বেশ খাটাখাটনি করে, নয়তো নিয়মিতভাবে লোক লাগিয়ে গোটা বাগানটা ফিটফাট করে রাখে। ভিতরে না ঢুকে কোমরসমান উঁচু বেড়ার এদিকে দাঁড়িয়ে বাগানটার উপরে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম আমরা। দেখলুম, নাম জাম সফেদা আর লিচুর সঙ্গে গুটিকয় কমলা আর বাতাবিলেবুর গাছও রয়েছে। একদিকে একটা কলাগাছের ঝাড়ও চোখে পড়ল। নারকেল আর সুপুরির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। গাছগুলো যে উল্টোপাল্টা লাগানো হয়নি, সেটা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। যিনিই করে থাকুন, সবটাই একেবারে প্ল্যান-মাফিক করেছিলেন। জঞ্জাল বলতে নেহাতই কিছু ঝরে যাওয়া পাতা এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তা ছাড়া কোথাও এক-টুকরো ময়লা কাগজ পর্যন্ত নেই। সত্যি বলতে কী, নিজের উঠোনটুকু পর্যন্ত অনেকে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে না।
তবু যে আমরা বাগানে ঢুকলুম না, তার কারণ আর কিছুই নয়, কাদা। বেড়ার এ-পাশ থেকেই বোঝা গেল যে, বাগানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করবার কোনও উপায় নেই। ক’দিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়েছিল নিশ্চয়, বাগানের ভিতরকার পথটা তাই কাদায় পিছল হয়ে আছে। মাটি কোথাও শুকনো কিংবা শক্ত নয়।
“অথচ মজা দেখুন।” ভাদুড়িমশাইকে বললুম, “বাগানের বাইরে এদিককার মাটি একেবারে খটখটে।”
“তা তো হবেই।”
গলাটা ভাদুড়িমশাই নয়, আর কারও। চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি, বুড়োমতন একজন ভদ্রলোক আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মোটা খদ্দরের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। সম্ভবত মন্দিরের পুবদিকের পথটা দিয়ে এসেছেন, তাই আমরা দেখতে পাইনি। ভদ্রলোক বললেন, “বাগানের মধ্যে বিস্তর গাছ-গাছালি রয়েছে তো, তাই খানিকটা আওতামতন হয়ে আছে, মাটি ততটা রোদ্দুর পায় না, তাই শুকোয়নি। এদিকের উঠোন সারাটা দিন রোদ্দুর পায়, তাই এদিকের মাটিও খটখটে। কিন্তু আপনাদের তো চিনলুম না। সত্যপ্রকাশের সঙ্গে এসেছেন বুঝি?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “হ্যাঁ। আমরা কলকাতার লোক। সত্যপ্রকাশবাবু অনেকক্ষন ধরেই আসতে বলেছিলেন, কিন্তু আমাদের আসা হচ্ছিল না। তাই এবারে ভাবলুম, দিন কয়েকের জন্যে ঘুরেই যাই।”
“ভাল সময়ে আসেননি।” ভদ্রলোক বললেন, “এ-বাড়ির মনসামূর্তি চুরি হয়ে গেছে, সক্কলের তাই মন খারাপ। সত্যপ্রকাশ বলেনি আপনাদের?”
“হ্যাঁ, শুনেছি। ওঁকে তো আমরা আগে থাকতে জানিয়ে আসিনি, এখন এসে শুনছি এই ব্যাপার! আপনি বুঝি এখানেই থাকেন?”
“হ্যাঁ, এখানেই এখন থাকি। আসলে আমি মুকুন্দপুরের লোক নই। আমার পৈতৃক ভিটে গয়েরকাটার কাছে একটা গ্রামে। কাঠের ঠিকেদারির কাজ নিয়ে এদিকে এসেছিলুম, তাতে সুবিধে না-হওয়ায় আলিপুরদুয়ারের একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারির কাজে ভর্তি হয়ে যাই। সে কি আজকের কথা? রিটায়ারই তো করেছি তা প্রায় বছর পাঁচেক হল। ভেবেছিলুম এবারে গয়েরকাটায় ফিরে যাব, তা সত্যপ্রকাশই ফিরতে দিল না। বলল, মুকুন্দপুরে তো লেখাপড়া শেখাবার কোনও ব্যবস্থা নেই, আপনি বরং আমাদের পাঠশালাটার দায়িত্ব নিন। ব্যস্, আমিও রয়ে গেলুম। সত্যই পাঁচ কাঠা জমির উপরে দুখানা ঘর তুলে দিয়েছে। ছেলেপুলের ঝামেলা নেই, আমরা বুড়োবুড়ি সেখানে দিব্যি আছি।’
“আপনার পাঠশালা কখন বসবে?”
“পাঠশালা এখন ছুটি। ভাইফোটার পরে খুলবে। চলুন, হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলা যাক। মর্নিং ওয়াক হবে, সেই সঙ্গে গ্রামটাও আপনাদের দেখা হয়ে যাবে।”