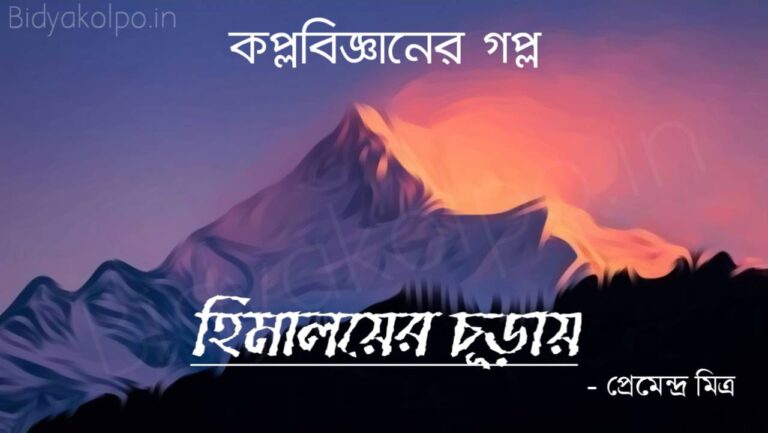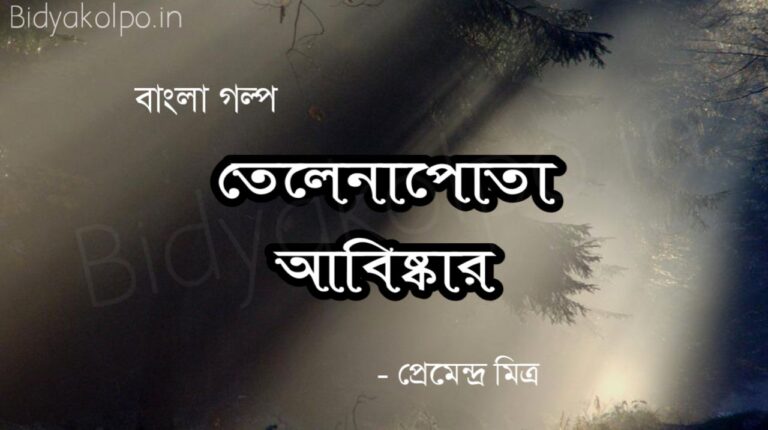পিঁপড়ে পুরাণ কল্পবিজ্ঞান আশ্রিত গল্প লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

সে অনেক কাল আগের কথা।
তখন সবাই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠত ; আর এমন মজা
যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলে৷ থাকত, আর রাত্তিরে
হত অন্ধকার।
পৃথিবীই ছিল তখন কী সুন্দর! মাটিতে নরম সবুজ ঘাস। হরেকরকম গাছে হরেকরকম
রঙের ফুল, আর রাত্তির বেলা আকাশে হাজার হাজার তারা—সে দেখতেই ছিল চমৎকার।
পাখিই ছিল তখন কতরকম! একরকম পাখি ছিল, তার নাম কাক। মিশকালো অন্ধকারের
মতো তার রং। আর তার গলার স্বর? কেউ কেউ বলে তার গলার স্বর নাকি ভালো ছিল না।
আমরা কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। যে কোকিল আজকাল আখছার আমাদের পথেঘাটে ঘুরে
বেড়ায়, তারই যদি স্বর এত ভালো হয়, তবে না জানি কাকের স্বর কী মিষ্টি ছিল! আর এই
কোকিল নাকি সেই কাকেদের বাসাতে গলা সাধতে শিখত। সে কাক এখন আর পাওয়া যায় না,
কেউ কেউ বলে, উত্তর মেরুতে পৃথিবীর যে সবচেয়ে বড়ো চিড়িয়াখানা আছে, সেখানে নাকি
একটি কাক এখনও আছে। তার জোড়টি মরে যাওয়ায় সেটিও নাকি ভারী মনের কষ্টে
আছে—বেশিদিন আর বাঁচবে না। আরেকরকম পাখি ছিল, তার নাম চড়ুই। সে পাখি লোকের
ঘরেদোরে, কড়িকাঠের ফাটলে বাসা বাঁধত। খুদে খুদে পাখিগুলি নাকি মানুষের বসতির কাছে
নইলে থাকত না। মানুষের ফেলা-ছড়ানো খুদ-কুঁড়ো খেয়েই তারা থাকত।
তোমরা ঘোড়া বোধ হয় কেউ কেউ দেখেছ। সে ঘোড়া তখন পথেঘাটে গাড়ি টেনে
লোক বয়ে বেড়াত। কুকুর তো তখন যেখানে-সেখানে এখনকার চিতাবাঘের মতো সস্তা ছিল।
এখন যেমন লোকে চিতাবাঘ পোষে, তখন তেমনি কুকুর পুষত। আরেকরকম জানোয়ার
ছিল—তার নাম বেড়াল। সে বেড়ালের কথা আমরা বেশি কিছু জানি না। সেকালের লোকেরা
বেড়াল সম্বন্ধে বেশি কিছু লিখে যায়নি।
একটি বহু পুরোনো সেকালের পুঁথিতে বেড়ালকে বাঘের মাসি বলা হয়েছে। তাতে মনে
হয়, বেড়াল খুব প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। কিন্তু এত বড়ো জানোয়ার লোকে বাড়িতে কী করে
পুষত, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। সরকারি পশুশালার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেড়াল
সম্বন্ধে গবেষণা করে একটি বই লিখেছেন। সেই বই প্রকাশিত হলে বেড়াল সম্বন্ধে অনেক
আশ্চর্য কথা জানা যাবে। আরও এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল, যা চোখে দেখলেও
তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—–ছাগল, ভেড়া, গোরু ইত্যাদি কত নাম করব!
সবচেয়ে মজার কথা এই যে, তখনকার পিঁপড়ে নাকি খুব বড়ো হলেও মানুষের কড়ে
আঙুলের চেয়ে বড়ো হত না। সে পিঁপড়েও ছিল নানা জাতের। মানুষের ঘরেদোরে, মাঠে-গাছে
নানা রকমের পিঁপড়ে তখন গর্তের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত। তাদের মধ্যে দু-এক জাতের
পিঁপড়ে মানুষকে কামড়ে একটু যন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতিই করতে পারত না। দল
বেঁধে একসঙ্গে তারা তখন থেকেই থাকত বটে, কিন্তু মানুষ তখন মোটেই ভাবতে পারেনি যে,
এই পিঁপড়ের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে তাকে একদিন লড়াই করতে হবে। অনেকে তখন
পিঁপড়ের ওপর দয়া করে তাদের বস্তা বস্তা চিনি খেতে দিত।
আর-বছরে দক্ষিণ আমেরিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা ভয়ানকভাবে হেরে গেছি,
একথা তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই শুনেছ। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, তখন সমস্ত
দক্ষিণ আমেরিকায় নানাজাতের মানুষের বাস ছিল। মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি
করতেই ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কী করছে না করছে তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি। খুব
বেশি পিঁপড়ের উৎপাত হলে পিঁপড়ের গর্তে খানিকটা বিযাক্ত অ্যাসিড ঢেলে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে
যেত। ৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল, জানা গেছে। তারপর থেকেই
আন্দিজ পাহাড়ের জঙ্গল থেকে এই নতুন জাতের ছ-ফুট লম্বা পিঁপড়ে বেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা
থেকে মানুষ তাড়াতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর আগে অনেক পর্যটক সমস্ত দক্ষিণ
আমেরিকার পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কেউই এই পিঁপড়ের কোনো সন্ধান পায়নি।
৬৭৫৭ সালে বিখ্যাত পর্যটক তাশেষ রায় যখন দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল ঘুরে এসে আন্দিজের
পার্বত্য প্রদেশে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেন, তখন কাগজে-কাগজে তাঁকে এমন
উপহাস-বিদ্রূপ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চুপ
করে যেতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর শেষ ডায়েরিতে লিখে যান, ‘আমি শপথ করে
বলে যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি, তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়!’
ওই আন্দিজ় পাহাড়ের কাছেই ৬৭৬৩ সালে একদল জাপানি রুপোর খনি আবিষ্কার করে
তাতে কাজ করতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর পাঁচ বছর ধরে তাদের তন্নতন্ন
করে খুঁজেও কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তোমরা বোধ হয় জান যে, সেসময় এই ব্যাপার
নিয়ে ভয়নাক হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল। অশেষ রায় যখন এই এক হাজার জাপানির অন্তর্ধানের
সঙ্গে এই অদ্ভুত জানোয়ারের কোনো সংস্রব আছে বলেন, তখন লোকে তাঁকে শুধু পাগলা
গারদে পুরতে বাকি রেখেছিল। অশেষ রায় এই অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে যেসব কথা জানান, তা
অত্যন্ত বিস্ময়জনক। সেকালের লোকেরা এই অপরূপ কাহিনিকে আজগুবি বলেছিল বলে তাদের
বেশি দোষও আমরা দিতে পারি না।
অশেষ রায় তাঁর পর্যটন থেকে ফিরে কোনো কাগজে লিখেছিলেন, ‘সেবার দক্ষিণ
আমেরিকা ভ্রমণে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার কাফ্রি বন্ধু, পৃথিবী বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ মন্ডুলা।
আগের দিন আমরা মাসোর নদীর উৎসে পৌছোই। তারপর আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল আলাগাস হ্রদ।
‘সেদিন সন্ধেবেলা আমরা ক্লান্ত হয়ে সারাটার কাছে একটি ছোটো পাহাড়ের ওপর বিশ্রাম
করছিলাম। আমাদের চারপাশে আন্দিজের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তাদের বিপুল দেহ নিয়ে ঘিরে
ছিল। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। আমাদের পশ্চিমে ঠিক আমাদের পাহাড়ের নীচের উপত্যকার
ওপর তখন অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে। উপত্যকাটি আয়তনে খুব ছোটো। চারধারে
পাহাড় যেন বিশাল দেওয়ালের মতো ওইটুকু জমিকে ঘিরে আছে। উপত্যকাটি আগাগোড়া
দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। শুধু এক জায়গায় ছোটো একটি পার্বত্য জলাশয় দেখা যাচ্ছিল।
‘আমি তখন আমাদের ছোট্ট তাঁবুটি রাত্রের জন্যে খাটাবার বন্দোবস্ত করছি। মন্ডুলা তাঁর
সেদিনকার সংগৃহীত নতুন জাতের কীটগুলি বাক্সবন্দি করছিলেন। হঠাৎ চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠে
মণ্ডুলা ডাকলেন, শুনুন !
‘খুঁটি পুঁততে পুঁততে চেয়ে দেখি, তিনি নিবিষ্টভাবে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে আছেন।
তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।
‘জিজ্ঞেস করলাম,—ব্যাপার কী?
‘মডুলা শুধু ইশারায় তাঁর কাছে যেতে বললেন এবং তাঁর কাছে গেলে তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ
করে নীচের পার্বত্য জলাশয়টি দেখিয়ে বললেন,— দেখতে পাচ্ছেন ?
‘জলাশয়ের ধারে কালো রঙের কী একটা জানোয়ারকে অস্পষ্টভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখা
যাচ্ছিল। বললাম, ও আর কী? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার হবে বোধ হয়।
‘মণ্ডুল৷ ঈযৎ হেসে বললেন, কোনো জানোয়ার-টানোয়ার যে হবে তা আমিও বুঝেছি,
কিন্তু কোন জানোয়ার? দক্ষিণ-আমেরিকার অত বড়ো কালো জানোয়ারের একটা নাম করুন তো
দেখি! আপনি দূরবিনটা একবার বের করুন তো!
‘সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেছে। নীচে সমস্ত জলাশয়টির ধারে
একটির পর একটি করে দশটি ওই ধরনের কালো জানোয়ার এসে তখন জড়ো হয়েছে।
‘আমার হাত থেকে দূরবিনটা একরকম কেড়ে নিয়েই মডুলা চোখে লাগালেন। কিন্তু পরের
মুহূর্তেই দূরবিনটা নামিয়ে বললেন, যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল!
‘দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই পাহাড়ে ওঠবার সময়ে কেমন করে না জানি ঠোকা লেগে
দূরবিনের কাঁচ দুটি ভেঙে গেছে।
‘সূর্যের আলো তখন বিরল হয়ে এসেছে। তবু সেই আলোতেই আমাদের খালি চোখে
আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, গভীর অরণ্যের ভেতর থেকে প্রায় দুশো ওই অপরূপ জানোয়ার
জলাশয়ের ধারে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আকৃতি অদ্ভুত—সামনের ও পেছনের দুটি বড়ো-
বড়ো কালো জালা কে যেন এক-একটি খাটো কাঠিতে গেঁথে লম্বা লম্বা পায়ের ওপর সাজিয়ে
দিয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি যত না অদ্ভুত, তাদের আচরণ তার চেয়েও বেশি। দলবদ্ধ হয়ে
অনেক জানোয়ার থাকে বটে, কিন্তু এমন তাপরুপ শৃঙ্খলা কোনো জানোয়ারের ভেতর আছে বলে
শুনিনি। তাদের একসারে চলা-ফেরা দাঁড়ানোর সঙ্গে একমাত্র খুব শিক্ষিত সৈন্যের কুচকাওয়াজের
তুলনা করা যায়।
‘যত তাদের গতিবিধি দেখছিলাম, দূরবিনের কাঁচ ভেঙে যাওয়ায় দুঃখ আমাদের ততই
বাড়ছিল। সন্ধের অন্ধকারে তারা শেষে একেবারে অরণ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে আমরা
বিমর্যভাবে সেদিক থেকে চোখ ফেরালাম। সেদিন রাত্রে তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আমাদের
আসতে চাইছিল না। মডুলা তাঁর বিছানায় অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে বললেন,
আচ্ছা আপনার কী মনে হয় বলুন তো? এমন আশ্চর্য জানোয়ার এতকাল কোনো পর্যটকের
চোখে পড়েনি, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?
‘আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই। হঠাৎ
চমকে জেগে উঠে দেখি, মন্ডুলা উত্তেজিতভাবে আমায় ঝাঁকানি দিচ্ছেন। আমি চোখ খুলতেই
তিনি বললেন, শিগগির বাইরে এসে দেখুন!
‘তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।
‘মণ্ডুলা উত্তেজিতভাবে বললেন, চেয়ে দেখুন, নীচে চেয়ে দেখুন!
‘নীচে চেয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে সেই পার্বত্য জলাশয়ের ধারে
নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে-আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ কিছুই দেখা
যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্টভাবে ওই জানোয়ারদের নড়াচড়া এক-আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা
কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে চেয়ে বসে রইলাম। এত বড়ো বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস
করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।
‘ভোর হওয়ার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিভে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে
পারিনি। ভোরের আলোয় ওই জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।
জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে প্রায় দশ বিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে গেছে। আগের দিন
সন্ধেবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে স্থান অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেঁর চিহ্ন পর্যন্তও নেই।
‘মণ্ডুলার উত্তেজনা তখনও শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন,
আমার কী মনে হয় জানেন? আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী।
‘এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বললাম, কারণ আপনি কীটতত্ত্ববিদ !
‘মন্ডুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর
কোন প্রাণীর চারটের বেশি পা দেখেছেন?
‘কথাটা সত্যি। আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখছি, তাদের পা কতগুলি তা গুনতে না
পারলেও চারের যে বেশি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
‘মন্ডুলা বলে যাচ্ছিলেন, তা ছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন!
‘বললাম, কিন্তু এত বড়ে৷ কীট?
‘মডুলা বললেন, অসম্ভব তো নয়!
‘তারপর পুরো একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে ওই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্যে তাপেক্ষা
করি, কিন্তু তার কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।’
অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। তারপর এক হাজার বৎসর এই প্রাণীর কথা
আর কিছুই শোনা যায়নি। অশেষ রায় ও মন্ডুলার কথায় পৃথিবীর লোক হাসলেও কেউ-কেউ
যে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে সেখানে যায়নি এমন নয়। কিন্তু আর কোনো পর্যটকের
চোখে কিছু পড়েনি। এখন আমরা অবশ্য বুঝতে পারছি যে অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই
দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল।
এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম, তখন আর সময় নেই। ৭৭৫৭ সালে একেবারে
বজ্রাঘাতের মতো আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত করে দেয়। আক্রমণের
আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ একথা কল্পনা করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত
হয়েছিল, তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম ধারে দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর
এক দিনে ধসে পড়ে। কতদিন আগে থেকে যে পিঁপড়েরা এই নগরগুলো ফোঁপরা করে এসেছে,
কেউ তা বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোন শত্রু তার
সর্বনাশের আয়োজন করেছে, একথা সে কেমন করে জানবে? ৭৭৫৭ সালের ১লা ফাল্গুন রাত
একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডরের সমস্ত বড়ো বড়ো শহর যখন হটাৎ
ভীষণ শব্দে ধসে পড়ে, তখন কেউ সন্দেহ করেনি যে, এ কোনো শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প
ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধসে-পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন
প্রভাত হল, তখন যে দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল তা অতি
ভয়ংকর। প্রতি নগরের চারধারে অসংখ্য পিপীলিকা বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।
পিঁপড়েদের সেই প্রথম আক্রমণে যে-সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়, তার একটিমাত্র
অধিবাসীই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবোয়া নগরের ডন পেরিটো। নগর ধ্বংসের সঙ্গে-
সঙ্গেই তাধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে কয়েকজন সকালবেলা পর্যন্ত কোনোরকমে জীবিত
ছিল, পিঁপড়েরা তাদের নির্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্যন্ত
পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না। ডন পেরিটো কোনোরকমে তাঁর এরোপ্লেনে চড়ে একেবারে
মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চড়েও যে তাঁর নিস্তার ছিল তা নয়। এমনি
করে আরও অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা রোমেনে
তাঁদের অনুসরণ করে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ডন পেরিটোর জীবন রক্ষা হয়েছিল শুধু
তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে। অন্য সকলের মতো প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা
না করে তিনি প্রথমে শুধু ঊর্ধ্বে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আট হাজার ফুট পর্যন্ত
তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু তার বেশি তারা আর উঠতে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান।
পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনি পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।
তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে পিঁপড়েরা কীভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও
আর্জেনটাইন রিপাবলিক দখল করে, তার ইতিহাস তোমরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই জান। আশ্চর্যের
কথা এই যে, পিপঁড়েদের প্রথম আক্রমণের পরেও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ তেমনভাবে
সাবধান হয়নি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রথম আক্রমণের পর দু-বৎসর পর্যন্ত তাদের
আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। হঠাৎ দু-বৎসর বাদে একদিন মাঝরাতে ৫২ ডিগ্রি
লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত শহর ধসে পড়ে। এই লঙ্গিচিউড ধরে পিঁপড়েদের আক্রমণ
আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার। এবারেও সেই আগের বারের কাহিনির পুনরাবৃত্তি হয়। শুধু অরিনকো
নদীর ধারে বলিভার নগরের লোকেরা আগে থেকে সন্দেহ করে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্রশস্ত্র ও
যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জড়ো হয়েছিল। তারাই কেবল যুদ্ধ করে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এই
যুদ্ধে প্রথম পিঁপড়েদের অদ্ভুত অস্ত্রের ও তাদের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের
শেযে কয়েকজন মাত্র বলিভার নগরবাসী নদী দিয়ে মোটরলঞ্চে অ্যাটলান্টিক সাগরে পালিয়ে
রক্ষা পেয়েছিলেন।
পিঁপড়েরা যে-অস্ত্র ব্যবহার করে, তাকে খুব ভয়ংকর একরকম বোমা বলা যেতে পারে।
কিন্তু বোমা প্রয়োগ করার রীতিটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। বলিভার নগরবাসীরা বলেন, যখন তীর
থেকে বহু উড়ন্ত পিঁপড়েকে গোল গোল একরকম জিনিস নিয়ে আমাদের দিকে উড়ে আসতে
দেখি, তখনই তাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করি। অনেক পিঁপড়ে সমস্ত গোলাগুলি এড়িয়েও
আমাদের জাহাজ নৌকোতে এসে পড়ে। তাদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভয়ংকর বিস্ফোরক
বোমা ফেটে জাহাজ নৌকো সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক
বোমার সঙ্গে একটি করে পিঁপড়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়। দূর হতে নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট
হওয়ার সম্ভাবনা তারা রাখে না।
পিঁপড়েদের দ্বিতীয় আক্রমণের পর সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে ওঠে। চীনের পিকিন শহরে
পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলে কর্তব্য স্থির করবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ
থেকে অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ, এরোপ্লেন ও সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকার বাকি দেশগুলির অধিবাসীদের
হয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? পিঁপড়েদের আস্তানার কোনো
পাত্তাই কেউ পায় না। মাটির তলায় কোথা দিয়ে তাদের গতিবিধি, সমস্ত আমেরিকা খুঁড়ে না
ফেললে জানবার উপায় নেই। সৈন্যেরা দিনের পর দিন ক্রোশের পর ক্লোশ পার হয়ে তন্নতন্ন
করে সমস্ত খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন হঠাৎ এক জায়গায় গভীর রাত্রে তাদের পায়ের
জলায় মাটি ধসে পড়ে। সকালবেলা তাদের আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। এরোপ্লেনের দল
ঝাকে ঝাকে দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে বিচরণ করে বেড়ায়। পিঁপড়েদের কোনো পাত্তাই
পাওয়া যায়নি। এরোপ্লেনগুলিরও কোনোমতে বিশ হাজার ফুট নীচে নামবার উপায় নেই, কোথা
থেকে একশো এরোপ্লেনের জায়গায় হাজার হাজার উড়ন্ত পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করে।
পিঁপড়েদের সঙ্গে এরোপ্লেন নিয়ে লড়াই করা শক্ত। একটাকে মারতে একশোটা এসে
ছেঁকে ঘরে। সবচেয়ে মুশকিল, তারা এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিনের মধ্যে ঢুকে জড়িয়ে তাকে অচল
করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মরে।
বিশ হাজার ফুট ওপর থেকে পিঁপড়েদের কোনো সন্ধানও মেলে না।
এদিকে মাটির ওপর বাকি সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা তখন প্রাণপণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
হচ্ছে। যেখানে যে শহর ছিল, সমস্ত শহরের লোক শহরের বাইরে নতুন করে ঘর বেঁধে বাস
করতে আরম্ভ করলে। কখন যে কোন শহর ধসে পড়ে, তার ঠিক কী পিঁপড়েরা কবে থেকে
কোন শহরের তলা ফোঁপরা করে রেখেছে, তা কে বলতে পারে?
কিন্তু পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ আক্রমণ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ একদিন
সমস্ত নতুন শহরের ভেতর সকাল থেকে মড়ক শুরু হয়ে গেল। সুস্থ, সবল মানুষেরা হঠাৎ মাথা
ঘুরে পড়ে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাত-পা খিঁচে মারা যায়। কাতারে কাতারে সকাল
থেকে লোক মারা পড়তে থাকে, অথচ ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা রোগের স্বরূপই খুঁজে পান না।
সারা পৃথিবী এ সংবাদ শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। বড়ো বড়ো মাথা ঘেমে উঠল, কিন্তু এই
মড়কের কারণ বোঝা গেল না। এক দিনে এইভাবে অর্ধেক আমেরিকার লোক নিঃশেষ হয়ে
যাওয়ার পর পরের দিন সকালে রোগের কারণ আবিষ্কার করল কিন্তু বাহিয়া শহরের একজন
মুটে। সকালবেলা শহরের সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্তা আর তিনজন বৈজ্ঞানিকের একটি গোপন সভা
বসেছে। শাসনকর্তা নিরুপায় হয়ে শহর ছেড়ে, আমেরিকা ছেড়ে, একেবারে জাহাজে করে এই
ভয়ানক দেশ ছেড়ে যাওয়ারই প্রস্তাব করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও সেনাপতিদের মধ্যে এই কথা নিয়ে
তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে—এমনভাবে পিঁপড়েদের কাছে হার স্বীকার করে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভালো বলে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য শুরু করছেন, এমন সময় হাঁপাতে
হাঁপাতে তাঁদের সভার প্রহরীকে একরকম বগলদাবাতে চেপে ধরে নিয়েই একটা বিশালকায়
লোক ঘরের ভেতরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। সভার সকলে তো স্তম্ভিত! লোকটা যেমন
লম্বা, তেমনি চওড়া—মাংসের একটা পাহাড় বললেই হয়। কিন্তু তার সমস্ত মুখে কে যেন কালি
মাখিয়ে দিয়েছে। সে মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় যে, এই অজানা ভয়ংকর রোগ তাকে
প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে। শেষ হওয়ার তার আর দেরি নেই। সেই বিশাল বিরাট দেহ সেই
ভীষণ রোগের প্রভাবে এর মধ্যেই কাঁপতে শুরু করেছে। তার ভীষণ বাহুর চাপে প্রহরীটিরও
তখন প্রাণান্ত হয়ে এসেছে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সেনাপতি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার বাহুপাশ
থেকে প্রহরীকে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টিত হলেন। প্রহরী তখন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। কিন্তু সে
বিশাল দেহের জোরের সঙ্গে কি পারা যায়। লোকটার তখন হাত-পা খিঁচুনি শুরু হয়েছে। অনেক
কষ্টে প্রহরীকে যখন সবাই মিলে মুক্ত করলেন, তখন দেখা গেল যে তার একটা পাঁজরা
একেবারে ভেঙে গেছে। প্রহরী তো অনেক কষ্টে জানাল যে, এই লোকটাকে সভায় ঢুকতে মানা
করতে গিয়েই তার এই দুর্দশা, এবং লোকটাকে সে চেনে। সে এই শহরের একজন মুটে—তার
নাম গুস্তাভ।
কেন তার সভায় ঢোকবার এত ব্যগ্রতা, সেকথা তখন গুস্তাভকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। মৃত্যুর
পূর্বলক্ষণরূপ প্রবল হাত-পা খিঁচুনি তখন তার শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট বাদেই সব শেষ
হয়ে যাবে। সভার সকলে বিমর্য মুখে তারই অপেক্ষা করতে লাগলেন। দু-এক মিনিটের মধ্যেই
গুস্তাভ মারা গেল, কিন্তু মারা যাওয়ার আগে একটিবার চোখ খুলে সে উন্মত্তের মতো চিৎকার
করে উঠেছিল, ‘জল খেয়ো না!’ তারপর সব শেষ।
‘জল খেয়ো না!’ এই ভয়ংকর দৃশ্যের সামনেও সেনাপতির কৌতুক বোধ হল। শাসনকর্তা
কাতরভাবে মুখ ফেরালেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হঠাৎ একজন তাত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে
উঠলেন। মুখ-চোখ তাঁর অসাধারণভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেনাপতির পিঠ হঠাৎ চাপড়ে দিয়ে
তিনি বললেন, আমরা কী গাধা!
সবাই তো অবাক! শাসনকর্তা বললেন, আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে যান, কাল থেকে
আজ পর্যন্ত একটিবারও তো চোখের পাতা মোড়েননি।
সবাই ভাবছিল—বৈজ্ঞানিকও বোধ হয় পাগল হয়ে গেলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক
সেনাপতিকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, আপনি কাল থেকে এখন পর্যন্ত কী খেয়েছেন?
ম্লান হেসে শাসনকর্তা বললেন, খাওয়ার কি সময় পেয়েছি—শুধু এক পেয়ালা দুধ।
কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরও চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, এবার বুঝেছেন?
এতক্ষণে সকলেই বুঝেছিলেন। নানান কারণে, বিশেষত এই ভয়ংকর মড়ক নিবারণের
উপায়-চিন্তায় তাঁদের কারুরই এই একদিন জল তো দূরের কথা, অন্য কিছু খাওয়ারই সুযোগ হয়নি।
বৈজ্ঞানিক বললেন, যাকে আমরা নতুন রোগ বলে ভেবেছিলাম, তা কেবল বিষের
ক্রিয়ামাত্র। শহরের জল বিযাক্ত হয়ে গেছে এবং কারা যে বিযাক্ত করেছে, তা বোধ হয় আর
বলতে হবে না।
শহরের সব জায়গায় অবশ্য তখনই ঢেঁড়া পিঠে দেওয়া হল এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত
শহরে তার করেও একথা জানিয়ে দেওয়া হল।
সত্যই শহরের জল বিযাক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক শহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কীভাবে কখন
পিঁপড়েরা বিযাক্ত করে দিয়েছিল, তা অবশ্য কেউ জানে না।
কোনোরকমে মানুষ এ যাত্রা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক মানুষ কাবার হবার আগে নয়।
এ ধাক্কা আবার সামলাতে না সামলাতে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে শহরে শহরে সাড়া
পড়ে গেল, পিঁপড়েরা আক্রমণ করতে আসছে! এবার যুদ্ধ মাটির ওপরে — সামনাসামনি! মানুষ
এরই জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছিল। মাটির ওপর যুদ্ধ করতেই সে অভ্যস্ত। এ যুদ্ধের জন্যে
সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
পিঁপড়েদের এই তৃতীয় আক্রমণের কাহিনি রায়ো-ডি-জানেইরো-র বিখ্যাত লেখক সেনর
সাবাটিনির লেখা থেকে আমরা পেয়েছি। তাঁর বিবরণই এখানে তুলে দিলাম ।
সেনর সেবাটিনি লিখেছেন, ‘হঠাৎ গভীর রাত্রে শহরের পশ্চিম ধারের প্রাচীরের প্রহরীরা
সংবাদ দিল যে, দূরে লাখ লাখ পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছে। প্রস্তুত আমরা দিনরাতই থাকতাম,
সুতরাং এ সংবাদে আমাদের বিচলিত হওয়ার কিছুই ছিল না। বরং এতদিন বাদে সামনা-সামনি
যুঝতে পাব বলে আমরাও উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পশ্চিমের প্রাচীরের সমস্ত সার্চলাইট তখন
রাত্রিকে দিন করে তুলেছে। সেনাপতির আদেশে অন্য সমস্ত দিকে কয়েকজন প্রহরী ও সৈন্য
ছাড়া আমরা সকলে পশ্চিমে নগর-প্রাকারের বাইরে এসে জড়ো হলাম।
‘সেখানে যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, তা জীবনে ভোলবার নয়। অন্ধকার রাত্রি আমাদের
অসংখ্য সার্চলাইটের প্রখর আলোয় তিন মাইল পর্যন্ত একেবারে যেন পেছিয়ে গেছে। এই
আলোয় আমাদের শহর থেকে দু-মাইল দূরে অসংখ্য পিঁপড়ের বাহিনী কালো সমুদ্রের বন্যার
মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পিঁপড়ের সারের পর পিঁপড়ে সার— যতদূর আলো
পৌঁছোয়, ততদূর পর্যন্ত শুধু পিঁপড়ের সমুদ্র।
‘সেনাপতির আদেশে আমাদের এক হাজার কামান গর্জন করে উঠল। ঘন পিঁপড়ের সারের
মধ্যে আমাদের কামানের গোলায় যে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা আরম্ভ হল, তা বর্ণনা করা যায় না।
দিকে দিকে আমাদের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়েও কিন্তু পিঁপড়েরা থামল না। মরা পিঁপড়ের
ওপর দিয়ে নতুন পিঁপড়ের দল সমানভাবে অগ্রসর হতে লাগল।
‘পিঁপড়েরা আমাদের গোলার জবাব দেয় না, শুধু নিঃশব্দে অগ্রসর হয়।
সেনাপতির আদেশে এবার আমরা অগ্রসর হলাম। প্রথমে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে এক দল, তার পিছু পিছু
আমাদের আটশো ট্যাঙ্ক। প্রাচীর থেকে সার্চলাইট নামিয়ে বড়ো বড়ো গাড়ির ওপর তুলে
সেগুলিও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।
‘পিঁপড়েদের দিক থেকে তবুও কোনো জবাব নেই। শুধু তারা ধীরে ধীরে এগোয়।
‘সেনাপতি আদেশ দিলেন, বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ো!
‘বিযাক্ত গ্যাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েদের অগ্রসর হওয়া বন্ধ হল। সে গ্যাসে এবং
আমাদের ট্যাঙ্কগুলির মেশিনগানের গুলিতে লাখো লাখো পিঁপড়ে মারা গেল। যেদিকে বিষাক্ত
গ্যাস ছোঁড়া হয়, সেদিকে পিঁপড়ের সার যেন কে মুছে দেয়। শুধু মাটি কালো করে
অসংখ্য পিঁপড়ের মৃতদেহ পড়ে থাকে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলি সেই মরা পিঁপড়ের সার মাড়িয়ে
অগ্রসর হয় ; আর তাদের মেশিনগানের গুলিতে পিঁপড়ের দল ছারখার হয়ে যায়। পিঁপড়েদের
এই দুরবস্থায় তখন তাামরা উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। শহর থেকে ছেলে, মেয়ে, বুড়োরা
পর্যন্ত তখন পিঁপড়েদের ধ্বংস-যজ্ঞ দেখবার জন্যে প্রাচীরের বাইরে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।
‘পিঁপড়েরা হঠাৎ যখন পিছু হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন তাদের অর্ধেকের বেশি মারা
পড়েছে। কিন্তু পেছুলে কী হবে? আমাদের ট্যাঙ্কগুলি এখন একেবারে তাদের ভেতরে গিয়ে
পড়েছে। সেই বিরাট ট্যাঙ্কগুলির চাপেই যে কত পিঁপড়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।
‘আমার তখন মনে হচ্ছিল, এতদিন আমরা মিথ্যাই ভয় পেয়েছি। হয়তো কোনো উপায়ে
তারা কিছু শক্তি অর্জন করেছে; কিন্তু হাজার হলেও তারা কীট— সামান্য কীট মাত্র। মানুষের
শক্তি, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কৌশলের বিরুদ্ধে তারা লড়তে আসে কোন সাহসে? তাদের এই
দুর্দশায় একটু যেন করুণাই আমার হচ্ছিল। সেনাপতির আদেশে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের দল
তাদের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধটা আমার একটা বীভৎস প্রহসনের মতো লাগছিল।
অসহায় পিঁপড়ের দলের পিছু হাঁটবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু
আশ্চর্যের কথা এই যে, ছিন্নভিন্ন হয়ে পিছু হাঁটলেও তারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়নি।
‘এবার সেনাপতির আদেশে পদাতিকদল তাগ্রসর হল। সেনাপতির আদেশ—একটি
পিঁপড়েও যেন আজ না বাঁচে। কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর না হতেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে
পড়লাম। পিঁপড়ে বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ-পাঁচেক সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে।
পিঁপড়েদেরও যে সার্চলাইট থাকতে পারে এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কী প্রয়োজন,
ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চলাইটের
আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সবজে রঙের। সে তীব্র আলোর সরু জিহ্বা
যেন তারা আমাদের আগের সৈন্যদের মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অভুতপূর্ব
দৃশ্য দেখতে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সারের পর সার সৈন্যদের মুখের ওপর
দিয়ে যে আলো বুলিয়ে বুলিয়ে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।
‘জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নিচু হয়ে বসে সেটা
বেঁধে উঠেই আমি দেখি যে, সে আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের
মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
‘আমার পাশের সৈনিকটি আমার হাতটা নাড়া দিয়ে বলল, সার্চলাইটগুলো নিভে গেল কেন
বলো তো?’
‘আমি হেসে উঠলাম, কানা হয়ে গেছ নাকি, সার্চলাইট আবার নিভল কোথায়? দিব্যি
জ্বলছে।
‘সে আবার ভীত কণ্ঠে বললে, কই আমি যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!
আমি তার পিঠ চাপড়ে বললাম, ওই আলোয় চোখটায় একটু ধাঁধা লেগেছে একটু রগড়ে নাও।
‘কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সামনের সার থেকে একজন চিৎকার
করে কেঁদে উঠল, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।
‘আমার পাশের সৈনিক আমার হাতটা কাতরভাবে জড়িয়ে ধরে বললে, তবু যে কিছু
দেখতে পাচ্ছি না ভাই, কী হবে!’
‘বিদ্যুতের মতো চকিতে এ ব্যাপারের আসল অর্থ আমার মনে খেলে গেল। আমাদের
সমস্ত বন্দুক কামান স্তব্ধ হয়ে গেছে, আমাদের ট্যাঙ্কগুলি নিঃশব্দ হয়ে গেছে, শুধু চারিদিক থেকে
অসহায় সৈন্যদের চিৎকার, কলরব, বিলাপ তখন তুমুল হয়ে উঠেছে।
‘আতঙ্কে পেছনে ফিরে চিৎকার করে উঠলাম, চোখ বন্ধ করো, আলোর দিকে চেয়ো না!
কিন্তু চারিদিকের ভীত ভাসহায় সৈন্যদের কলরব ছাপিয়ে সে ক্ষীণ স্বর কতদূর আর পৌঁছোয়।
পিঁপড়েরা তখন আমাদের শহরের প্রাচীরের কাছে সমবেত ছেলেমেয়ে ও বুড়োদের মুখের ওপর
দিয়ে আলো বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
‘তারপর যে ভয়ংকর বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ হল, তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই।
সেই অন্ধ অসহায় সৈন্যদের ওপর অসংখ্য পিঁপড়ে হিংস্র যমদূতের মতো ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল।
‘চিৎকার করে বললাম, পালাও, পালাও!
‘কে পালাবে? কোথায় পালাবে?
‘অন্ধ সৈন্যের দল অসহায়ভাবে পালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই মাথা ঠোকাঠুকি করে
মরতে লাগল এবং পিঁপড়ের দল সেই বিশৃঙ্খল জনতাকে নির্মমভাবে সংহার করতে শুরু করল।
এই হতভাগ্য সৈন্যদের কোনোরকমে বাঁচাবার উপায় না দেখে অবশেষে নিজের প্রাণ রক্ষা
করবার জন্যে ছুটতে হল। কিন্তু ছুটে পালানোও সোজা নয়, পিঁপড়েরা তখন ঘাড়ের ওপর এসে
পড়েছে। একটা বিশাল কালো পিঁপড়ে আমার পিঠের জামাটা কামড়ে ধরেছিল। হাতাহাতি লড়াই
পিঁপড়েদের সঙ্গে এর আগে হয়নি। সেই বিকট কীটকে দেখে শিশুর মতো ভয়ে চিৎকার করে
উঠলাম। কিন্তু চিৎকার করবার সময় সে নয়—পাশ থেকে আর একটা পিঁপড়ে তখন আমার
পায়ে প্রচণ্ড কামড় দিয়ে চলেছে। সেটার মাথায় ছোরা বসিয়ে দিতেই চটচটে একরকম রসে
সমস্ত হাতটা আমার ভিজে গেল এবং পরমুহূর্তেই পেছনের পিঁপড়েটার টানে একেবারে চিত হয়ে
মাটিতে পড়ে গেলাম। সমস্ত পিঠটা আমার ওইরকম রসে ভিজে ওঠাতে বুঝলাম, পেছনের
পিঁপড়েটাকে দেহের চাপে থেঁতলেই ফেলেছি। পিঁপড়েদের দেহগুলো আকারে বড়ো হলেও
ভাত্যন্ত নরম, এই যা রক্ষা। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুট দিলাম,— কোনদিকে, তা মনে নেই।’
এইখানে সেনর সাবাটিনির বর্ণনা শেষ হয়েছে। রায়ো-ডি-জানেইরোর সমস্ত অধিবাসীর
মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনিই রক্ষা পেয়েছিলেন। পিঁপড়েদের হাত কোনোরকমে এড়িয়ে
সমুদ্রে গড়ে ছোটো একটি ভেলার সাহায্যে নিকটের একটি দ্বীপে উঠে তিনি সেবার প্রাণ বাঁচান।
কয়েক বছর বাদে একটি চীনে জাহাজ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।
রায়ো-ডি-জানেইরোর সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েরা সেদিন দক্ষিণ আমেরিকার বাকি সমস্ত শহরও
আক্রমণ করে। সে আক্রমণে কোনো শহরই রক্ষা পায়নি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সেদিনই
মানুষের পাট ওঠে। তারপর আর মানুষ সেখানে পা দিতে পারেনি। গত বৎসর সে চেষ্টা করতে
গিয়ে আমরা কী ভীষণভাবে হেরে গেছি, সে খবর তো তোমরা সবাই জান।
এই হল গিয়ে পিঁপড়েদের দক্ষিণ আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস। মানুষ অবশ্য
হয়ে বসে নেই। সামান্য কীটের হাতে এই লাঞ্ছনার শোধ নেওয়ার জন্যে পৃথিবীর বড়ো বড়ো
বৈজ্ঞানিক এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু শিগগির যে আমরা দক্ষিণ আমেরিকা ফিরে পাব, তারও
বড়ো আশা নেই ; কারণ যে অদ্ভুত আলোয় তারা অমন করে মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তার
রহস্য এখনও আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেননি।
পিঁপড়েদের আমেরিকা অধিকারের ইতিহাস পাঁচ বছর আগে সংক্ষিপ্তভাবে কাগজে বের
হয়। তারপর সেই বিবরণ পড়ে অনেকে কৌতূহলী হয়ে আরও অনেক কথা জানতে চেয়েছেন।
কিন্তু তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার কোনো সুবিধে হয়নি, কারণ এতদিন পিঁপড়েদের সম্বন্ধে
ওর বেশি কিছু জানা ছিল না। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে বিশদভাবে সন্ধান করা তো দূরের কথা, মানুষ
সেবার পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পালাবারই পথ পায়নি। পিঁপড়েরা কেমন
করে এই বিপুল শক্তি অর্জন করেছে, তাদের রাষ্ট্রসমাজের গঠন কেমন, তারা দক্ষিণ
আমেরিকাকে কীভাবে এখন গড়ে তুলেছে, তার কোনো বিবরণই মানুষের জানবার কোনো
সুযোগ হত না—যদি না…
..যদি ভারতীয় জাহাজ ‘যমুনা’র সমস্ত নাবিক আর যাত্রী একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের
দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে না উঠত। একটি ছেলের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের
বিবরণ-সংগ্রহের সম্বন্ধ কোথায়, তা প্রথমে বোঝা একটু কঠিন বটে। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার
করেই বলি। ভারতীয় নৌবহরের ‘যমুনা’ জাহাজটি সেবার ফিলিপাইনের পূর্ব-উপকূল হয়ে
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোটো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার
কাছাকাছি ও পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের প্রধান ঘাঁটি। মাঝ রাস্তায় ঝড় হয়ে আগের
দিন জাহাজ নির্দিষ্ট পথ থেকে একটু দূরে এসে পড়েছিল, এখন আবার নির্দিষ্ট পথ খুঁজে নেওয়ার
চেষ্টা হচ্ছিল ; কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল শুধু একটি ছেলের দৌরাত্ম্যে। ছেলেটি ‘যমুনা’র
ক্যাপ্টেনের, বয়স তার মাত্র বারো; কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি ও সাহসে সে পঁচিশ বছরের যুবককেও হার
মানায়। ঝড়ের রাত্রে সবাই যখন জাহাজ ও নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময় দেখা গেল,
ছেলেটি জাহাজের দুটিমাত্র লাইফবোটের একটি খুলে ঝড়ের সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে।
ঝড় থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ ছেলেটির খোঁজ পাওয়া যায় না। তানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা
গেল যে, সবচেয়ে বড়ো মাস্তুলের আগায় উঠে সে বসে আছে। নামিয়ে এনে ধমক দেওয়ায় সে
বলল, আমি নতুন দেশ আবিষ্কার করছিলাম।
ঝড়ের পরের দিন রাত্রে হঠাৎ মাঝ সমুদ্রে বারবার জাহাজ থেকে সার্চলাইট জ্বলতে দেখে
দু-একজন যাত্রী এসে ক্যাপ্টেনকে কারণ জিজ্ঞেস করল। ক্যাপ্টেন তো তাবাক। মাঝ
সমুদ্রে—যেখানে অন্য কোনো জাহাজের নামগন্ধ নেই, সেখানে সার্চলাইট জ্বালবার মানে কী?
কোন নাবিক এরকম করছে, তার সন্ধান নিয়ে তাকে শাসন করবার জন্যে সার্চলাইট-টাওয়ারে
গিয়ে ক্যাপ্টেন দেখেন যে তাঁর ছেলেটি পরমানন্দে সার্চলাইট জ্বালিয়ে সমুদ্রের এধার থেকে
ওধার ঘুরিয়ে ফেলছে। তিনি কান ধরে তাকে শাসন করতে যাবেন, এমন সময় চকিত
সার্চলাইটের আলোকে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ায় তিনি ছেলেকে শাসন করার কথা ভুলে
নিজেই সার্চলাইট ধরে বসলেন।
সে আলোয় যা দেখা গেল, তাতে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। দেখা গেল যে, জাহাজ
থেকে শ-দুয়েক গজ দূরে একটি ছোট্ট ভেলা সমুদ্রের ওপর দুলছে। তার ওপর আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা
একটি ভার্ধ-উলঙ্গ মানুষের দেহ। মানুষটি বেঁচে আছে কি না, বোঝা যায় না।
তৎক্ষণাৎ তিনি নৌকো নামিয়ে ভেলাটি ধরে আনবার আদেশ দিলেন। আর তার ফলেই
সেই ভেলাতে বাঁধা লোকটির ডার্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটিমাত্র
লোকের জানা ছিল, তাঁর উদ্ধার হল।
তিনি সুখময় সরকার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষ পালিয়ে আসার পর পাঁচ বছর তিনি
সে দেশে কাটিয়েছেন পিঁপড়েদের সঙ্গে। আর মানুষের ভেতর একা তিনিই তাদের সমস্ত ব্যাপার
জেনে জীবিত অবস্থায় মানুষের দেশে আবার ফিরতে পেরেছেন। পিঁপড়েদের সঙ্গে তাঁর বাসের
কাহিনি তিনি নিজ মুখে যা বলেছেন, তা-ই আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। রায়ো-ডি-
জানেইরোর পতনের দিন তিনি নগরের ভেতর একটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় অত্যন্ত ব্যস্ত
ছিলেন। এমন সময় অযুত মানুষের আর্তনাদ তাঁর কানে এসে পৌঁছোয়। এখান থেকেই তাঁর
বর্ণনা হয়েছে
‘প্রথমে মনে হল, আমাদের সৈন্যেরা বুঝি যুদ্ধজয় করেছে, তাই এই জয়ধ্বনি, কিন্তু
পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—না, এ তো আনন্দধ্বনি নয়, এ যেন সহস্র কণ্ঠের আর্তনাদের মতো
শোনাচ্ছে। এ শব্দ শুনলে গায়ের ভেতর যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।
‘তাড়াতাড়ি কী ব্যাপার দেখবার জন্যে নগর-প্রাচীরের কাছে গেলাম ; কিন্তু ওপরে আর
উঠতে হল না। দূরে তোরণের ভেতর দিয়ে দেখি——অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে
কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছে; তাদের চলবার ভঙ্গি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম
কিন্তু বিস্ময়ের সময় বেশি ছিল না। তাদের পেছন পেছনই দেখি—অগুনতি কালো পিঁপড়ের দল
তাদের তাড়া করে আসছে। অসহায় সৈন্যদের পিঁপড়েদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার কোনো
ক্ষমতাই নেই। তারা এলোপাথাড়িভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে, কিন্তু পিঁপড়েরা অনায়াসে তাদের আঘাত
এড়িয়ে একেবারে তাদের মর্মস্থলে ঘা দিচ্ছে।
‘নগর-তোরণ পার হয়ে যে কয়জন এসেছিল, তাদের কেউই শেষ পর্যন্তরক্ষা পেল না,
একজন মাত্র সৈন্য প্রাণপণ বেগে ছুটে পিঁপড়েদের পেছনে ফেলে আমার কাছ পর্যন্ত এসে
পড়েছিল। পিঁপড়েরা তখন আমাদের ধরে ধরে। পিঁপড়েদের হাতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কোনো
গতি নেই, বুঝতে পারছিলাম।
‘সেইজন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মনে হল, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু এভাবে হওয়া উচিত নয়!
মরতে যদি হয় তো নিজের পরীক্ষাগারের ভেতর নিজের গবেষণা করতে করতেই মরব। তা ছাড়া যে পরীক্ষাটি অসমাপ্ত রেখে এসেছি, পরীক্ষাগারের সকল দরজা-জানলা বন্ধ করে
পিঁপড়েদের গতিরোধ করলে তা সমাপ্ত করবার সময়ও হয়তো পেতে পারি।
‘তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এই সৈন্য বেচারিকেও তো আমার
সঙ্গে নিতে পারি! পেছন ফিরে বললাম, আমার পিছু পিছু এসো। খানিকটা নিরাপদ হতে পারবে।
কিন্তু সে আমার গলার আওয়াজ শুনে ভড়কে যেভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল, তাতে মনে
হল, আমি যেন অদৃশ্য কোনো একটা পদার্থ। বললাম, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? এসো আমার সঙ্গে।
‘কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
‘এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না; কিন্তু তখন সে কথা আলোচনা করবার সময়
নেই। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে যখন পরীক্ষাগারে এসে পড়লাম, তখন দুটো
পিঁপড়ে আমাদের পিছু পিছু এসে প্রায় ধরে ফেলেছে। সৈন্যটিকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে
নিজে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারই ভেতরে কিন্তু একটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে
আধখানা শরীর ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। দরজার চাপে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আমার ঘরের মধ্যে
পড়ল।
‘দরজাটা দিয়ে আমার মনে হল, যাই হোক—এখন কিছুক্ষণের জন্যে নিরাপদ হওয়া
যাবে। পরীক্ষাগারের সমস্ত জানলা আগে থেকেই বন্ধ ছিল। পিঁপড়েরা ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত
নিশ্চিন্তভাবে কাজ করা যাবে।
‘এইবার আমার সঙ্গে যে সৈন্যটি এসেছিল তার দিকে ফিরে বললাম, — মাটির
তাতেও পিঁপড়েদের কাছে পারা গেল না—কী তাদের এমন ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র?
‘লোকটা মেঝের ওপর মাথা নিচু করে বসে ছিল। আমার দিকে চোখ
আলোয় তার চোখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম—চোখের তারার জায়গায় তার রগরগে একটা ক্ষত!
‘তারপর তিন দিন পরীক্ষাগারের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। সৈন্যটির কাছে যুদ্ধে আমাদের
বাহিনীর যে দুর্দশার কাহিনি শুনলাম তারপর আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়নি। শুধু
শান্তভাবে মানুষের নতুন বিজেতাদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। এখনও কেন পিঁপড়েরা
আমাদের ধরবার চেষ্টা করেনি, তা বুঝতে পারছি না। আমাদের দরজায় তো সারাক্ষণই প্রহরীর
মতো একটি পিঁপড়ে মোতায়েন আছে, দেখতে পাচ্ছি চাবির ফুটোর ভেতর দিয়ে। জানলাগুলো
দিয়েও সারাক্ষণই একটা না একটা পিঁপড়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনও অক্ষত দেহে
বেঁচে আছি। যারা অজ্ঞাত আলো দিয়ে মানুষকে অন্ধ করবার বিদ্যে আয়ত্ত করেছে, তারা একটা
সামান্য দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে না, এমন কথা অবশ্য মনেও স্থান দিইনি। তবুও এদের মতলব
কী, বুঝে উঠতে পারছি না।
‘চতুর্থ দিন কিন্তু সব দুর্ভাবনার শেষ হল। পরীক্ষাগারের ভেতর যা সামান্য খাবারদাবার
ছিল, তা একদিনে আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। সকাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে,
পিঁপড়েরা না মারলেও উপবাসেই কয়েক দিনের ভেতর আমাদের মরতে হবে। পিঁপড়েদেরও
সেই মতলব আছে কি না, বলতে পারি না। এমন করে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করাও
অসহ্য। ভাবলাম, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু তার যন্ত্র হাতে নিয়েই হোক। যে সাধনা আজীবন করে
এসেছি, মরবার সময়ে যেন তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারি। এই ভেবে যন্ত্রপাতি নিয়ে
নিজের গবেষণায় মন দিয়েছি, এমন সময় দেখি—বন্ধ দরজার কঠিন লোহার মতো কাঠ কী
অস্ত্রে জানি না একেবারে মাখনের মতো কেটে যাচ্ছে। চারিধার কাটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা
সশব্দে ভেতরে পড়ে গেল। অন্ধ সৈনিকটি সে শব্দে চমকে ভীত হয়ে একধারে সংকুচিত হয়ে
গিয়ে লুকোল। আমিও ভয়ংকর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।
‘এক-এক করে ছটি বৃহদাকার পিঁপড়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের এত কাছ থেকে নজর
করবার কোনো সুবিধে এতদিন হয়নি। লক্ষ করলাম—একজনের ছাড়া তাদের বাকি সকলের
আকৃতি এক। একজনের মাথার আকারটা একটু বৃহত্তর এবং মুখের শুঁড়গুলির রংও একটু
আলাদা। কোনোপ্রকার শব্দ বা সংকেত দেখতে বা শুনতে না পেলেও বুঝতে পারলাম যে, তারই
আদেশে সব কাজ হচ্ছে। পিঁপড়েদের সর্দার ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ
পেছনের পায়ে ভর দিয়ে টেবিলের ধারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার পরীক্ষার যন্ত্রপাতির ওপর
ঝুঁকে পড়ে কী দেখল ও কী বুঝল, সেই-ই জানে। আমার পাশেই সেই কদাকার লোমশদেহ
কীটটাকে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এরাই মানুষের মতো প্রকৃতির রহস্য
উদ্ঘাটন করে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক চাপড়ে এই ঘৃণ্য
কীটটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই। সে ইচ্ছে দমন করেই অবশ্য রেখেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত
আর থাকতে পারলাম না। এই অতিকায় পিঁপড়েদের গা থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বের
হয় যে, সে দুর্গন্ধ সহ্য করা কঠিন। পিঁপড়েরা আমার অতি নিকটে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, দুর্গন্ধ সহ্য
করতে না পেরে তাকে ঠেলে দিলাম। ঠেলা যে বিশেষ জোরে হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেই
সামান্য ঠেলাতেই সে চারপাক খেয়ে ঘুরে একেবারে বহু দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মনে হল,
এবার আর নয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এদের আর বিলম্ব হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য!
তাদের দলপতির এই অপমানে কোনো পিঁপড়েকেই একটুও বিচলিত হতে দেখলাম না।
ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। তারা যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। দলপতিও
খানিক বাদে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। দেখলাম, তার সামনের একটা ঊই সামান্য পড়াতেই
ভেঙে গিয়েছে।
‘দলপতি খাড়া হয়ে উঠেও কোনোপ্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করল না দেখে তাত্যন্ত
বিস্মিত হয়ে গেলাম। তাহলে এরা কী করতে চায়? কী এদের মতলব? কিন্তু সেকথা ভাববার
অবসর বেশি পেলাম না।
‘হঠাৎ মনে হল, আমার পা দুটো ধীরে ধীরে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সেই অবশতা পা
থেকে ক্রমশ আমার দেহের ওপর দিকে উঠতে জারম্ভ করল। সে অবশতার কোনো কষ্ট অনুভব
করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল শরীরটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে এসেছে—এখন যেন একটু কোথাও
গড়াতে পারলেই বেঁচে যাই। কিন্তু মিনিট-খানেকের ভেতর যখন হঠাৎ মনে হল যে আমার দৃষ্টি,
শ্রবণ, স্পর্শ—সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়ে আসছে, তখন ভয়ংকর ভীত হয়ে উঠলাম — এ কী
ব্যাপার! এই কি মৃত্যু নাকি? ধীরে ধীরে জ্ঞান লোপ পাচ্ছিল। এই আচ্ছন্ন ভাবের বিরুদ্ধে সমস্ত
মনের জোর দিয়ে যুদ্ধ করেও সজ্ঞান থাকতে পারছিলাম না। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে জ্ঞান
হারিয়ে নেতিয়ে পড়বার আগে এই আকস্মিক অবশতার কারণ বুঝতে পারলাম। স্পষ্টভাবে
দেখলাম, প্রহরী পিঁপড়েদের একজনের দুটি সামনের পায়ে একটি রেডিয়ো সেটের মতো ছোটো
যন্ত্র রয়েছে। তার সামনের দিক থেকে একটা পিচকারির মতো নল উঁচিয়ে আছে ; আর সেই নল
দিয়ে একরকম বাষ্প এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ পড়েনি, তার
কারণও ছিল—সে বিষবাষ্প বাতাসের মতোই বর্ণগন্ধহীন।
‘জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি যেন কোন অতলে নেমে চলেছি। চারিদিকে
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। প্রথমে মনে হল, এই কি মৃত্যুর পরের অবস্থা! পরের মুহূর্তেই একটি
উৎকট দুর্গন্ধ নাকে যাওয়ায় সে ভয় দূর হয়ে গেল। উৎকট দুর্গন্ধও যে মানুষের মনে আনন্দ
দিতে পারে, আগে তা কখনো ভাবিনি। এখন এই দুর্গন্ধ থেকে বুঝলাম যে আমি বেঁচেই
আছি—যদিও পিঁপড়েদের বন্দি। হাত বাড়িয়ে একটি পিঁপড়ের ঠান্ডা গা স্পর্শ পর্যন্ত করলাম।
অনেক দূর এই অন্ধকার দিয়ে নেমে গিয়ে হঠাৎ আলো চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের
ইলেকট্রিক আলোর মতো; কিন্তু সেই অলোগুলির চারধারে কোনো কাচের আবরণ নেই,
বৈদ্যুতিক শক্তিতেও তা জ্বলে না। পাথরের মতো এক-একটি নুড়ি নানা জায়গায় ছড়ানো, তা
থেকেই এই আলো বের হয়। পরে জেনেছি, এই আলো-বিজ্ঞানে পিঁপড়েরা মানুষকে অনেক
দূরে ছাড়িয়ে গেছে। তাপহীন যে আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনও অক্ষম,
পিঁপড়েরা তাই বের করেছে। সেই আলোয় ওপর দিকে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল, তার
মাঝখান দিয়ে তামার একটি রড বসানো। সে রড বেয়েই আমাদের লিফ্ টের মতো ঘরটি নেমে
এসেছে। বুঝলাম, পৃথিবীর ওপরের স্তর থেকে নেমে একরকম পিঁপড়েদের পাতালেই নেমে
এসেছি। বড়ো বড়ো খনিতে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি–চারধারে অনেক সুড়ঙ্গ চলে
গেছে। সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অসংখ্য পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। সমস্ত সুড়ঙ্গপথটি
আলোকিত। সে আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়।
‘আমার জ্ঞান হলেও হাত-পাত তখনও অবশ। আমাকে ঠেলাগাড়ির মতো একটা গাড়িতে
পিঁপড়েরা চাপিয়ে দিল। ভাবলাম তারা বুঝি ঠেলেই কোথাও নিয়ে যাবে; কিন্তু ছেড়ে
দেওয়ামাত্র গাড়িটি আপনা থেকেই চলতে আরম্ভ করল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গাড়িটাতে না
আছে বাষ্পের ইঞ্জিন, না জাছে মোটর। প্রথমে এই গাড়ি পিঁপড়েদের বিজ্ঞানের আর এক কীর্তি
বলে মনে হয়েছিল কিন্তু পরে এ গাড়ির রহস্য জানতে পেরে না হেসে থাকতে পারিনি। গাড়িটি
আমাদের ঘোড়ার গাড়ির জাতভাই, শুধু ঘোড়ার বদলে এ গাড়ি যারা টানে তাদের নাম শুনলে
বিস্মিত হবে। এ গাড়ির বাহন গণেশের বাহনের মতো বড়ো বড়ো মেঠো ইঁদুর।
পিঁপড়েরা এই একটিমাত্র জানোয়ারকে বশ করেছে ও কাজে লাগিয়েছে। মাটির তলায় আর
কোন জানোয়ারই বা তাদের কাজে লাগাতে পারে। এই ইঁদুরগুলিকে আশ্চর্যরকম শিক্ষিত
তারা করছে, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। মানুষ অনেক জানোয়ার বশ করেছে, কিন্তু
পিঁপড়েদের ইঁদুর-বাহনেরা যেভাবে — যেরকম বুদ্ধি খাটিয়ে মনিবদের কাজ করে, মানুষের বশ
করা কোনো জানোয়ারকে তো সেরূপ করতে দেখিনি। এই ইঁদুর দিয়েই পিঁপড়েরা তাদের
ছোটোখাটো সমস্ত কাজ করায়। পিঁপড়েদের গাড়ির তলায় প্রায় গুটি-বিশেক ইঁদুর জোতা থাকে।
ওপর থেকে তাদের দেখা যায় না। আদেশ পাওয়ামাত্রই তারা শিক্ষিত ঘোড়ার মতো গাড়িটি
টেনে নিয়ে যায়। আর গাড়ির বেগও বড়ো কম হয় না। মজার কথা এই যে এই মূষিকদের
কোনো চালকের প্রয়োজন হয় না, তারা নিজেরাই যেন জানে যে কোথায় থামতে হবে। অন্তত
আমার বেলা তো তাই হল। এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সেখানে পিঁপড়েরা আমায়
যেভাবে নামিয়ে নিয়ে গেল, তাতে বুঝলাম — তারা আমার আসার কথা আগে থেকেই জেনে
প্রস্তুত হয়েছিল। আমাকে তারা যেখানে নিয়ে গেল, সেটি একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গা।
সুড়ঙ্গটি এখানে চওড়া হয়ে এই আকার নিয়েছে। পিঁপড়েদের নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই। তারা
অনেকে মিলে এমনি এক-একটি হলঘরে দরকার হলে এসে বিশ্রাম ও আহারাদি করে। আমাকে
হলঘরের একটি কোণে এনে তারা শুইয়ে দিল। তখন আমার ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে শরীরের
এমন অবস্থা যে, একটু গড়াতে পারলেই বাঁচি। আমি সেখানে কাত হয়ে পড়লাম। কদিন ধরে
অজ্ঞান ছিলাম, জানি না। অত্যন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেয়েছিল, কিন্তু সেকথা জানাবই বা কাকে এবং
জানালেই বা কী হবে! আমার বন্দি জীবন সেইদিন থেকেই আরম্ভ হল।
‘কিন্তু আমি না জানালেও পিঁপড়েরা মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভোলেনি দেখা গেল।
পিঁপড়েদের ইঁদুর-ভৃত্যের কথা তখনও জানি না। হঠাৎ বড়ো বড়ো গুটি চার-পাঁচ ইঁদুরকে আমার
দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। ইঁদুরগুলি কিন্তু কোনোরকম বিচলিত না
হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে জিনিস। সেগুলি নামিয়ে
রেখে তারা আবার চলে গেল। সে জিনিসগুলি যে আহার্য, প্রথমে তা বুঝতে পারিনি,
কৌতূহলভরে সেগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে একটি জিনিস যেন মুলোর মতো মনে হল।
তখন আর ভাববার অবসর ছিল না। অন্য জিনিসগুলি বাদ দিয়ে সেই মুলোর মতো জিনিসটিতে
এক কামড় দিলাম। জিনিসটা কোনো গাছের মূলই বটে, কিন্তু স্বাদ তার মুলোর মতো নয়। স্বাদ
যে বিশেষ ভালো, তাও বলতে পারি না; কিন্তু সেদিন তাই-ই অমৃতের মতো লেগেছিল।
জিনিসটি রসালো, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই-ই তার দ্বারা কতকটা নিবৃত্ত হল। খাওয়ার পর ক্লান্তিতে কখন
যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারি না।
‘তারপর পিঁপড়েদের সঙ্গে যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর
নয়। অবশ্য একথা জানি যে, বিশদভাবে জানালেও সেই দীর্ঘ বিবরণ একঘেয়ে লাগবে না। কারণ
প্রত্যেক দিনই ওই অদ্ভুত জাতের যেসব নতুন নতুন ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি, মানুষের
জ্ঞানের দিক থেকে তাঁর প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ। আপাতত সংক্ষেপে পিঁপড়েদের সমাজ-গঠন
প্রভৃতি জানাবার চেষ্টা করব। কেমন করে পিঁপড়েরা ধীরে ধীরে আমায় একটু একটু স্বাধীনতা
দিতে শুরু করলে, কেমন করে পিঁপড়েদের নানা ব্যাপার জানবার সুযোগ আমার হল, কেমন করে
শেষ পর্যন্ত আমার সেখানে একরকম প্রভাব প্রতিপত্তি পর্যন্ত হল, তার বিশদ বর্ণনা আমি করব
না, শুধু পিঁপড়েদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন — অর্থাৎ তাদের ভাষা
শিক্ষা—কেমন করে তা আমার হল, তাই একটু জানাব।
‘পিঁপড়েরা আমায় তখন স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি যেখানে-সেখানে বেড়াই,
সময়মতো আহার পাই ও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই। চোখ দিয়ে যেটুকু বোঝবার তার বেশি কিন্তু
কিছুই বুঝতে পারি না। পিঁপড়েদের কোনোদিন শব্দ করতে শুনিনি।
তারা কী করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে, কী করে কাজ চালায় এই ভেবে আমার বিস্ময় লাগে। এমন সময় একদিন
কয়েকটি পিঁপড়ে আমার ঘুম ভাঙার পর আমার বিশ্রাম-স্থানে এসে হাজির হল। তাদের ভেতর
একটি পিঁপড়ের মাথাটি অত্যন্ত বৃহৎ, দেখে বুঝলাম যে, সে সর্দার-টর্দার হবে। বিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ-
ঘরের নানা জায়গায় তখন অন্যান্য পিঁপড়েদের কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ সবে জেগে উঠেছে। বড়ো
মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী দেখল, সেই জানে।
দেখলাম তার মুখটা নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ সেখান থেকে শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ
এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে কী আদেশ করলে জানি না, কিন্তু একটি পিঁপড়ে একটি
গ্রামোফোনের সাউন্ড-বক্সের মতো যন্ত্র নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। সামনের দু-পা দিয়ে সেই
যন্ত্রটি সে হঠাৎ আমার কানে লাগিয়ে দিল ; আমি প্রথমত প্রতিবাদ করে যন্ত্রটি ফেলে দিতে
যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরে, অনিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এতদিন বাদে তারা নিশ্চয়ই আসেনি জেনে চুপ
করে সব সহ্য করলাম। যন্ত্রটা পরাবার সময় প্রথমটা কানে একটু লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে
হল, যেন চারিধারে অদ্ভুত কোনো শব্দ শুনছি। প্রথমটা বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরক্ষণেই
সামনের দিকে বড়ো-মাথাওয়ালা পিঁপড়েকে মুখ নাড়তে দেখে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।
এতক্ষণে হঠাৎ তার মুখ থেকে শব্দ শুনতে পেলাম। তার মানে অবশ্য বুঝতে পারলাম না বটে
কিন্তু এতদিনে পিঁপড়েদের কথা শুনতে পাওয়ার আনন্দেই তখন আমি বিভোর। মনের আনন্দে
নিজেই— সাবাস ভাই বলে ফেলেছিলাম। দেখলাম, আমি কথা বলামাত্র পিঁপড়েটা অমনি
একপ্রকার যন্ত্র তার নিজের কানে লাগান। বুঝলাম, আমাদের শব্দও সে এইভাবে শোনবার চেষ্টা
করছে। পিঁপড়েটা তারপর বহুক্ষণ কথা কইল, কিন্তু তার শব্দ শুনতে পেলেও অর্থ বুঝতে না
পেরে মনে হচ্ছিল, এমনভাবে শব্দ শুনতে পেয়েই বা লাভ কী? কিছুক্ষণ বাদে পিঁপড়েটা নিজে
থেকেই তাদের ভাষা আমায় শিক্ষা দেওয়ার উপায় করে নিল। রাত্রের আহার্যের কিছু কিছু
তখনও আমার শয্যাপার্শ্বে পড়ে ছিল, সেইদিকে একটা পা বাড়িয়ে সে একটা শব্দ করল, আমিও
সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খাবার। পিঁপড়েটা পূর্বের মতো শব্দ আরও কয়েকবার করে আমায় বুঝিয়ে
দিল যে, খাবারের প্রতিশব্দ পিঁপড়েদের ভাষায় কী হয়।
‘এরপর পিঁপড়েদের ভাষা শেখা আমার খুব তাড়াতাড়িই হতে লাগল। সকাল থেকে রাত
পর্যন্ত সেই বড়ো-মাথাওয়ালা পিঁপড়েটা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমায় কয়েক মাসের মধ্যেই
এমন তামিল করে তুলল যে তাদের ভাষা শুধু বোঝা নয়, কতকটা বলতে পর্যন্ত আমি পারলাম।
এখন থেকে পিঁপড়েদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ আমার পক্ষে সম্ভবপর হল।
‘কানের যে যন্ত্রের দ্বারা পিঁপড়েদের ভাষা আমি বুঝলাম, সেইটির এবং কেন পিঁপড়েদের
শব্দ মানুষ শুনতে পায় না সে-বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। তোমরা জান কি না জানি
না যে, মানুষের কান দিয়ে যে শব্দ শুনতে পাই, তা ছাড়া আরও অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে।
সে শব্দ এত বেশি তীব্র যে, আমাদের কান তা ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর শব্দও
আমরা স্বাভাবিক কান দিয়ে ধরতে পারি না। আমরা যে শব্দ শুনি, তা মাঝামাঝি আওয়াজ ; কিন্তু
অতিকায় পিঁপড়েদের আর কিছু না থাক, গলার আওয়াজ এমন প্রচণ্ড যে, মানুষের কান তা
ধরতেই পারে না। তাই পিঁপড়েদের আমাদের বোবা বলেই মনে হত। আমাদের শব্দ করার শক্তি
পিঁপড়েদের মতো প্রচণ্ড নয় বলে আমাদের শব্দও পিঁপড়েদের কানে যেত না। যে যন্ত্র পিঁপড়েরা
আমার কানে পরিয়ে দিয়েছিল, সেটিকে শব্দশোধন যন্ত্র বলা যেতে পারে। তার ভেতর দিয়ে
পিঁপড়েদের চড়া শব্দ নরম হয়ে আমাদের কানের উপযোগী হয়ে যায় বলেই আমি তাদের কথা
শুনতে পেয়েছিলাম। আবার আমার মৃদু শব্দও তাদের কানের মতো চড়া করে নেওয়ার
পিঁপড়েরা নিজেদের কানে অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। সেদিন থেকে সেই যন্ত্রের সাহায্যেই
আমাদের কথাবার্তা চলতে শুরু হয়। আমাদের কানের এই রহস্য বুঝে যে জ্ঞানিক পিঁপড়ে এই
যন্ত্র আবিষ্কার করে—শত্রু হলেও তাকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।
‘পিঁপড়েদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। সাধারণ ছোটো পিঁপড়েরা
কীভাবে বাস করে, তা বোধ হয় তোমরা জান। তাদের ভেতর একজন থাকে রানি। সে-ই ডিম
পাড়ে ও তার ডিম থেকেই সমস্ত পিঁপড়ের জন্ম হয়। দু-একটি পুরুষ-পিঁপড়ে ছাড়া আর বাকি
সমস্তই পিঁপড়ের রাজ্যে শ্রমিক, তারা রানির জন্যে খেটে মরে মাত্র। অতিকায় পিঁপড়েদের
সমাজব্যবস্থা প্রায় একরকমই, শুধু তাদের ভেতর কোনো রানি নেই। তাদেরও অধিকাংশ পিঁপড়ে
শুধু দাসবৃত্তি করে জীবন কাটায়—তাদের না আছে ঘর না আছে স্ত্রী-পুত্র। কিন্তু তাদের উপরে
একদল পিঁপড়ে থাকে, পালন-শাসন প্রভৃতি সমস্ত কাজ তারাই করে। তারা পিঁপড়েদের
রাজবংশ। তারা কতকটা মানুষের মতো স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে ঘর বেঁধে থাকে। যা কিছু বৈজ্ঞানিক
গবেষণা, রাজ্য-পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব—তাঁদের দ্বারাই হয় এবং তাদেরই ছেলেপুলেদের ভেতর
যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম, তাদের ছেলেবেলা থেকেই দাস করে দেওয়া হয়। দাস
পিঁপড়েরা বিয়েও করে না, তাদের ছেলেপুলে সংসারও হয় না; তাই বলে তারা অসন্তুষ্ট
নয়— আর তারা উৎপীড়িতও হয় না। পিঁপড়েদের রাজবংশের এক-একটি দম্পতির ছেলেপুলে
হয় অসংখ্য। ডিম ফুটে বেরোবার পরই বৈজ্ঞানিকেরা এসে তাদের পরীক্ষা করে যায়। প্রাচীন
স্পার্টার্নদের মতো তাদের ভেতর একেবারে যারা অকর্মণ্য তাদের মেরে ফেলে, অপেক্ষাকৃত
নির্বোধদের দাস করে দিয়ে বাকি সব শিশুদের ভেতর কার মাথা কোন দিকে খেলবে, আগে
থেকে বুঝে সেইদিকে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। শিশু অবস্থাতেই প্রত্যেকের
শক্তি-বিচারের বিদ্যায় পিঁপড়েরা যে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, মানুষ তা ভাবতেই পারে না।
পিঁপড়েদের ভেতর রাজা নেই। অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মতো। তাদের রাজবংশের মেয়ে-
পুরুষ সবাই মিলে এক সভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করে। সেখানে বিশেষ মতভেদ বা
গোলমাল কখনো হয় না, কারণ যার মাথা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ খোলে, সে কখনো রাজনীতিতে মাথা
ঘামাতে আসে না।
‘পিঁপড়েদের ভেতর বড়োলোক কেউ নেই, গরিবও নেই। যার যা দরকার, রাজভাণ্ডার
থেকে সবাই তাই পায়। একদল পিঁপড়ে শুধু এই কাজেই আছে। পিঁপড়েরা কেউ কিছু সঞ্চয়
করে না, সুতরাং অর্থ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি সেখানে নেই। যে যার নিজের কাজ করতে
পেলেই তারা সন্তুষ্ট।
‘কিন্তু জ্ঞানে, বিদ্যায়, সমাজগঠনে তারা বিশেষ অগ্রসর হলেও কলাবিদ্যা তাদের নেই
বললেই হয়। রাজবংশের পিঁপড়েদের মাঝেমাঝে কাজের অবসরে একত্র হয়ে নাচের মতো
একরকম মজলিশ করতে দেখেছি, এ ছাড়া গান-বাজনা, ছবি আঁকা বা চৌষট্টি কলার
কোনোটিরই তাদের চর্চা নেই।
‘স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি বৃত্তিরও তাদের একান্ত অভাব। তারা শুধু ন্যায় বিচারই জানে।
কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞানও তাদের অদ্ভুত।
‘এখন কী করে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম, সংক্ষেপে তা বলে এ কাহিনি শেষ করব।
‘পিঁপড়েদের ভেতর পাঁচ বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে তাদের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ
করা সত্ত্বেও মানুষের সংসর্গের জন্যে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। শুধু পালানো অসম্ভব
জেনেই চুপ করে থাকতাম। একদিন কিন্তু অভাবনীয়রূপে সে সুযোগ এসে গেল। রায়ো-ডি-
জানেইরোর কাছে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। একদিন হঠাৎ সে ভূমিকম্প একটু ভীষণভাবে
দিল। ভূমিকম্প হওয়ামাত্র পিঁপড়েদের নিয়ম—নীচের গর্ত থেকে ওপরে, মাটির
যাওয়া। আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমেছিলাম, সেরকম সুড়ঙ্গ সেখানে আরও প্রায় পঞ্চাশটি আছে।
ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার বেঁধে পিঁপড়েরা দলে দলে বেরিয়ে পড়তে লাগল।
পিঁপড়েদের দলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। পিঁপড়েরা ব্যাস্ত হতে জানে না—শুধু এই
ভূমিকম্পেই তাদের যা বিচলিত হতে দেখেছি। এক-এক দল করে লিফ্টের খাঁচায় ঢুকে আমরা
ওপরে উঠে এলাম। অন্যান্য অনেকবার দেখেছি, ওপরে উঠতে না উঠতেই ভূমিকম্প থেমে
যায় ; কিন্তু এবারে ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ হয়ে উঠল। আমাদের দল ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই
সুড়ঙ্গ পথটি ধসে নীচে পড়ে গেল। চারিদিকে তখন ভীষণ বিশৃঙ্খলা ; প্রতিমুহূর্তে পায়ের তলার
মাটি ধসে পড়তে পারে জেনে পিঁপড়েরা ব্যাকুলভাবে এদিকে-সেদিকে ছুটতে শুরু করেছে।
আমিও প্রাণভয়ে একদিকে ছুট দিলাম। ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে তখন ভয়ানক ঝড়ও
উঠেছে। সেইসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। খানিকদূর ছোটবার পর দেখলাম—চারিধারে কোথাও কোনো
পিঁপড়ের দেখা নেই। এতদিন পিঁপড়েদের সঙ্গে বাস করে তাদেরই সঙ্গী ও সহায় বলে ভাববার
অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা সত্যিই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম। ভূমিকম্পে তখন নানা
জায়গায় মাটি ফেটে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে আরম্ভ করেছে। পিঁপড়েদের ভাষায় চিৎকার করে
ডাকলাম। এই মানুষশূন্য আমেরিকায় একমাত্র পরিচিত পিঁপড়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে আমি
কোথায় যাব! কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় আমার কণ্ঠের ডাক আপনি থেমে
গেল। এই তো মুক্তির সুযোগ! পিঁপড়েরা হাজার ভালো ব্যবহার করলেও চিরদিন আমায়
নজরবন্দি করে রাখবে, কোনোদিন মানুষের মাঝে ফিরতে দেবে না। আমি যে তাদের তানেক
কথা জানি! হয় মৃত্যু, নয় কোনোরকমে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়াই হল আমার
উদ্দেশ্য, প্রাণপণে তাই ছুটতে লাগলাম।
‘ভূমিকম্প যখন থামল, পিঁপড়েদের ঘাঁটি থেকে তখন আমি অনেক দূর এসে পড়েছি।
এইবার আমার খোঁজ পড়বে জেনে ক্লান্ত পদেও আরও এগিয়ে চলতে লাগলাম। আমার একমাত্র
মুক্তির উপায় সমুদ্রতীরে পৌঁছে কোনোরকমে ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে ভাসা। সে সমুদ্রে যদি
মৃত্যুও হয় তবুও ভালো, তবুও তো আকাশের তলায় ফাঁকা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে মরতে পারব!
ইঁদুরের মতো মাটির নীচে মরতে হবে না!
‘কেমন করে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ভেলা তৈরি করে ভেসে পড়েছিলাম ও কেমন করে
আমার উদ্ধার হয়, তার কথা সব সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে ; সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি করে
কাহিনি বাড়াব না।
‘পরিশেষে বলতে চাই যে, মানুষ আবার দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন
করছে—কিন্তু আমার সে আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই। দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করা
তো দূরের কথা, মানুষের বর্তমান অধিকারগুলি এই দুর্ধর্য কীটদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই
একদিন আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার বিশ্বাস। পিঁপড়েদের আমি যেরকম করে
জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমরা সহজেই জন্মেছে।’